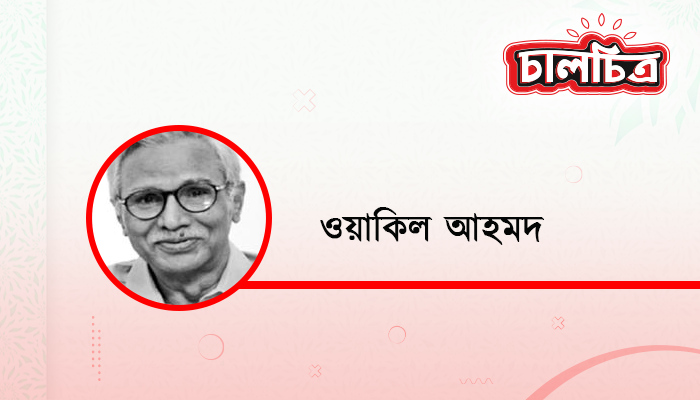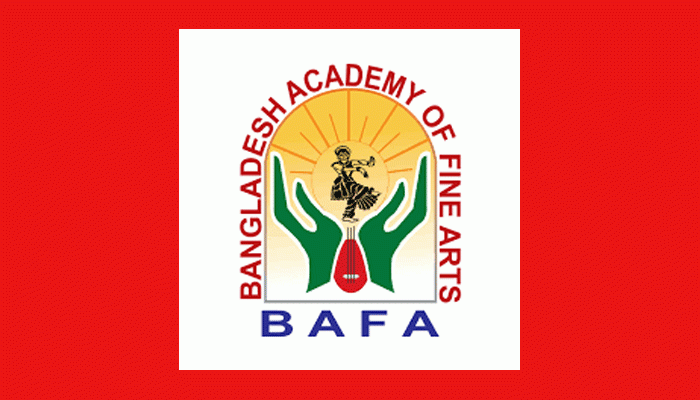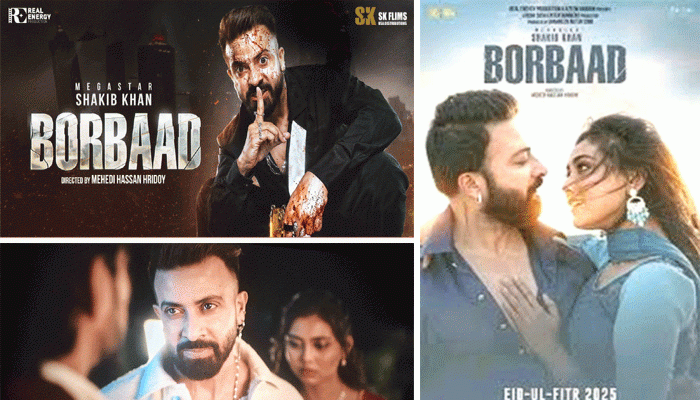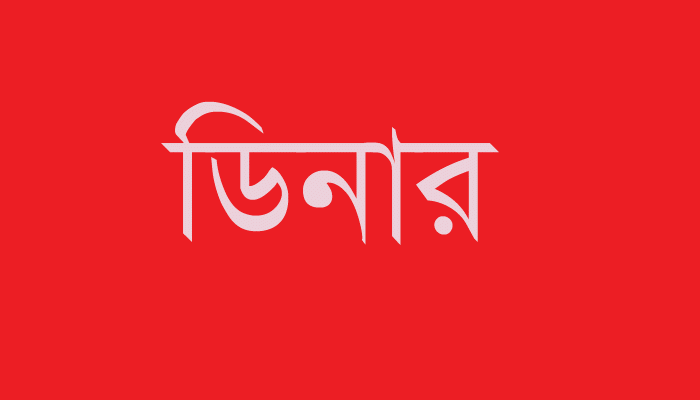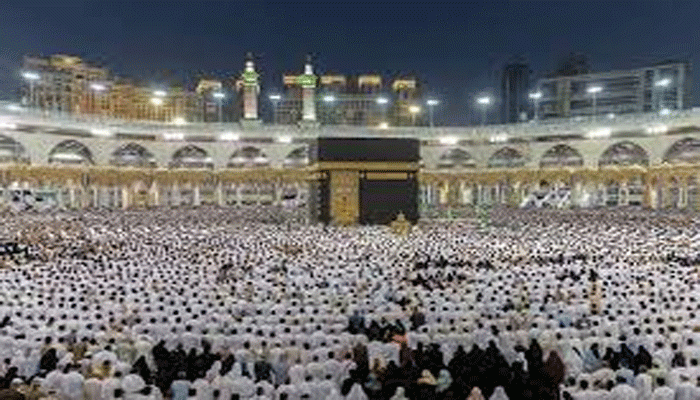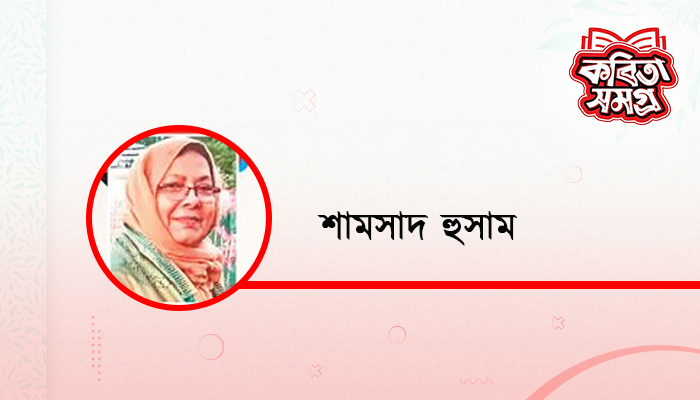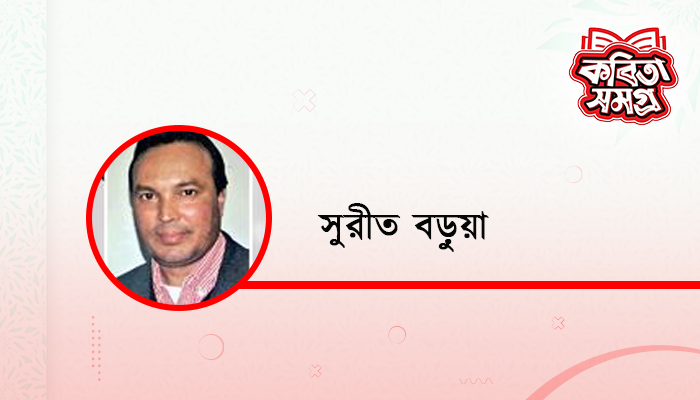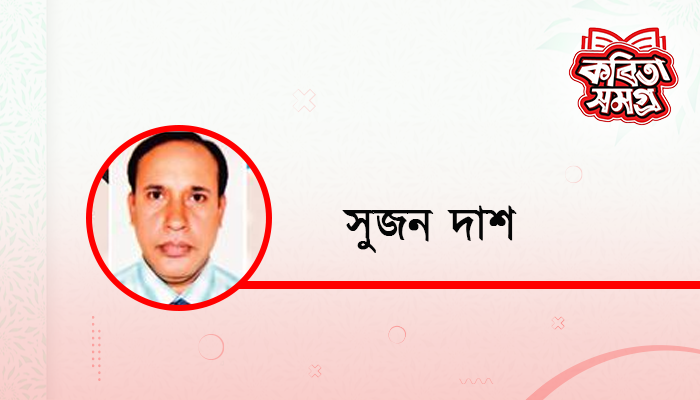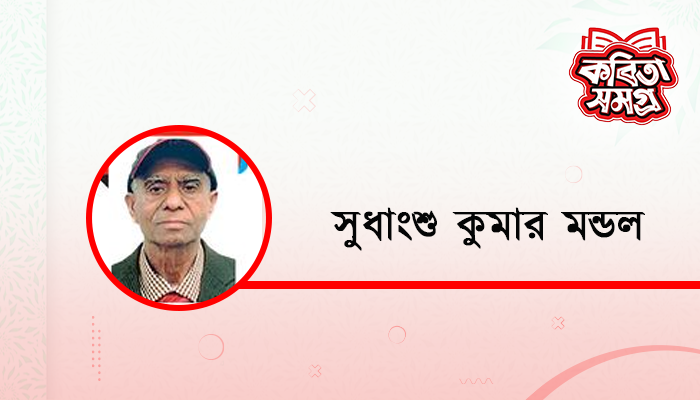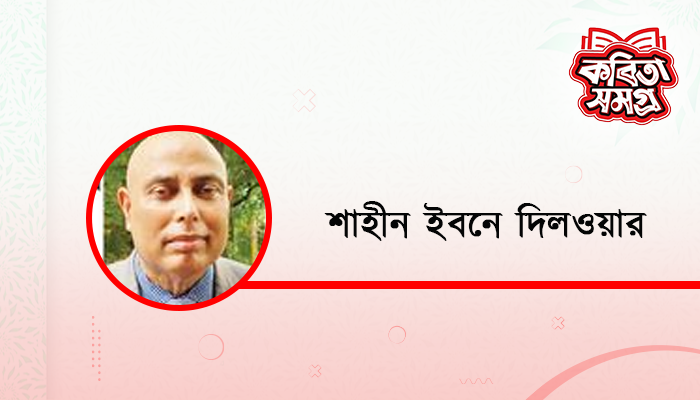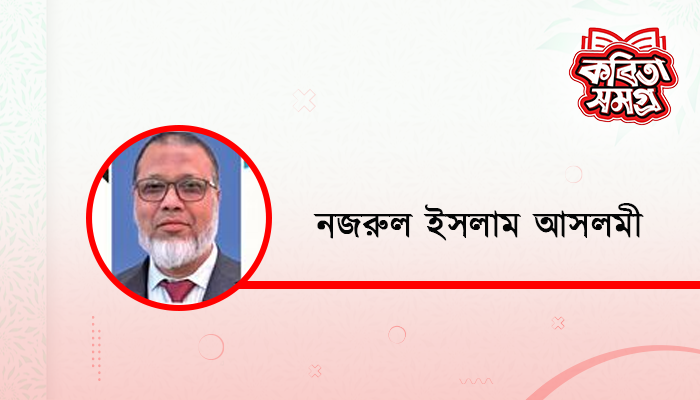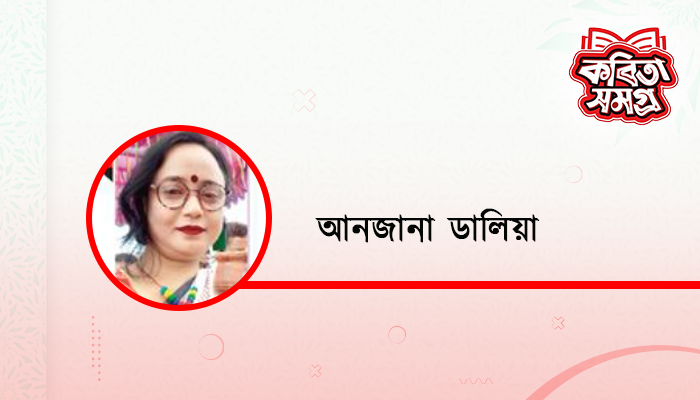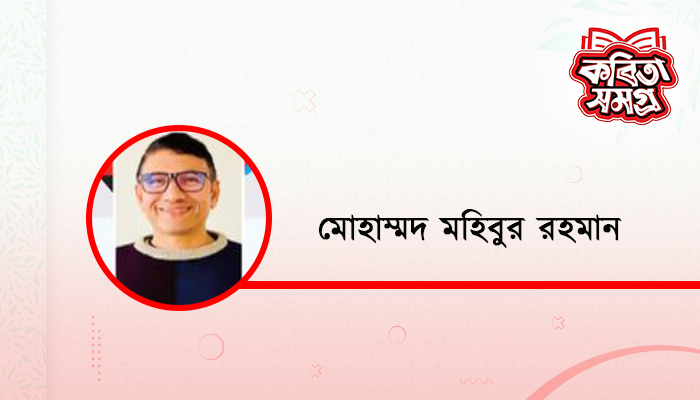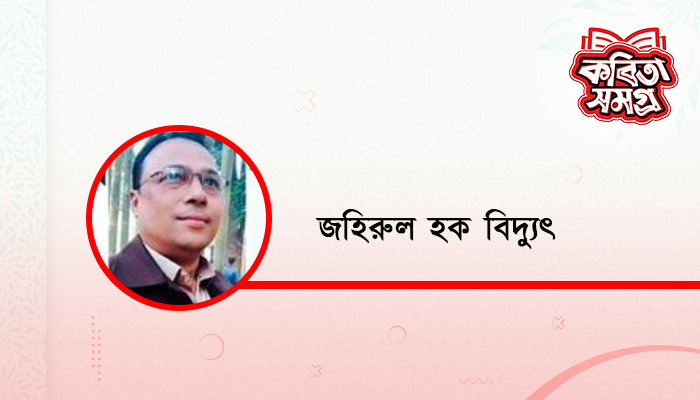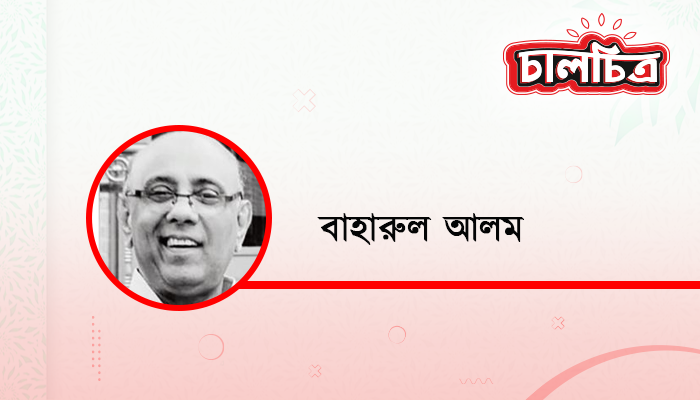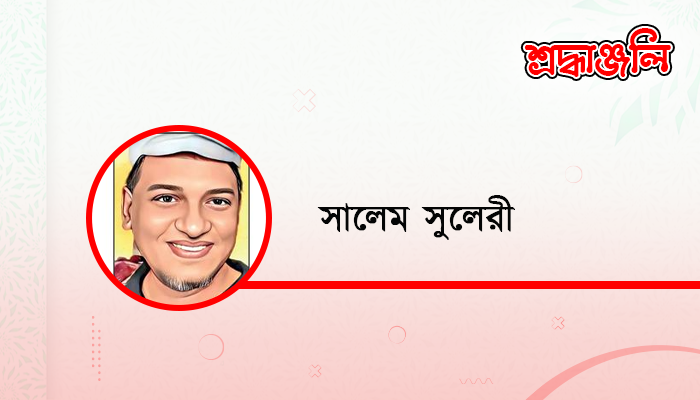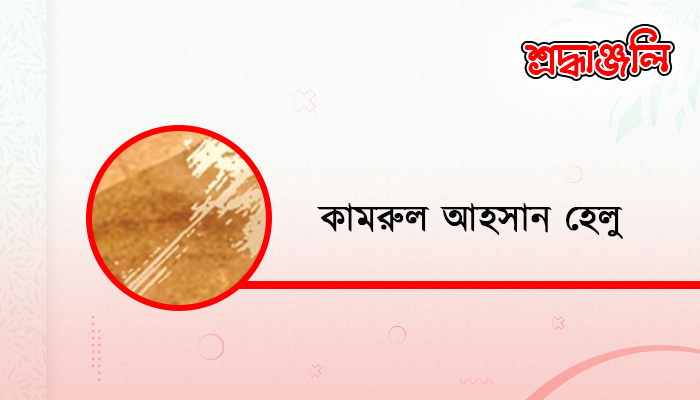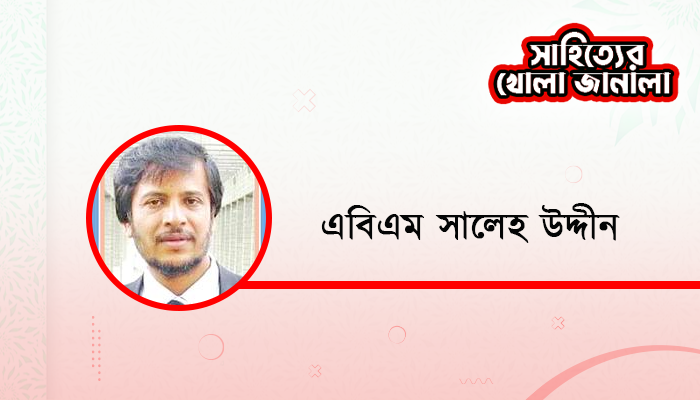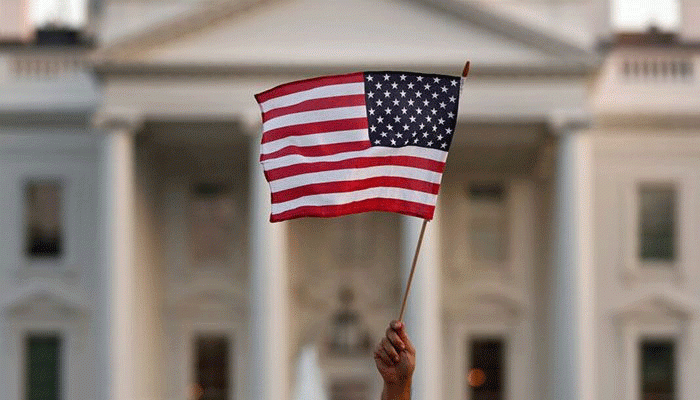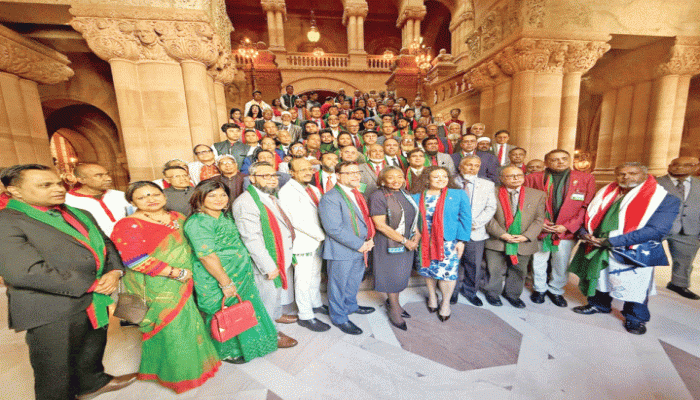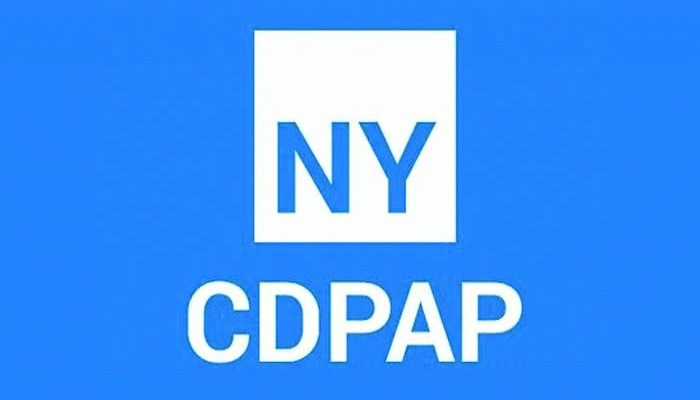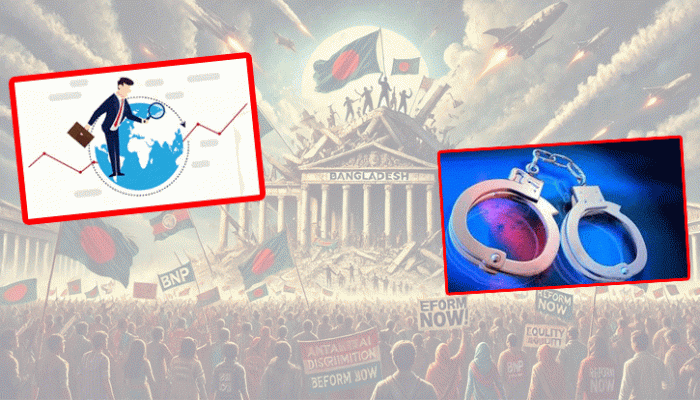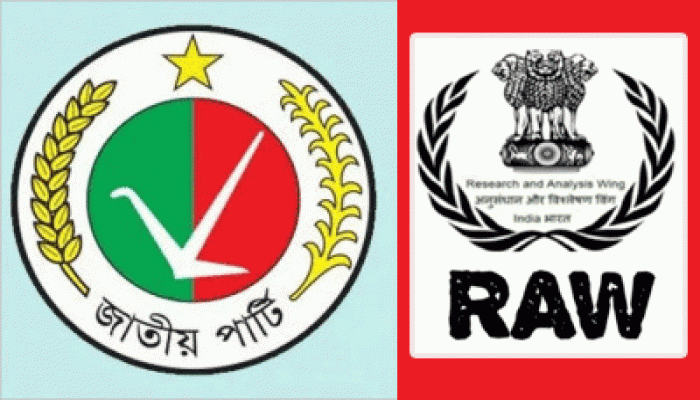গত বছরের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে একটি বড় মাপের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়, যার ফলে স্বৈরাচার ও কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের পতন হয়। বিশ্বনন্দিত নোবেল লরিয়েট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে জনগণ-সমর্থিত একটি ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার’ দায়িত্বভার গ্রহণ করে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে। একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।
ওই ঐতিহাসিক ঘটনার পর প্রায় ৯ মাস অতিবাহিত হলো। একটি বিশাল ঘটনার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিতর্ক চলছে। এর কটি বিষয় হলো-এটি কি নিছক কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, না বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থান, না চব্বিশের জুলাই বিপ্লব? আরও নানা নাম পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়। কোটা সংস্কার ছাত্র আন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ৩৬ জুলাই আন্দোলন, জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি। অনেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনুসরণে চব্বিশের ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থান বলতে চান। পরে যুক্ত হয়েছে ‘জুলাই বিপ্লবে’র ধারণা। অতিসম্প্রতি চব্বিশের ‘গণ-বিদ্রোহ’ নামও শোনা যায়। মহিউদ্দিন আহমদের মতো লেখক-গবেষক একই রচনায় ‘২০২৪ সালে গণ-বিদ্রোহ’, ‘চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ নামদ্বয় ব্যবহার করেন। (প্রথম আলো, ২৫-৪-২৫)। প্রকৃত নামকরণ কী হবে, তা এখনই পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। অবশ্য নামটি সহজপাচ্য ও সহজোচ্চার্য হওয়া উচিত। ‘জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান’, না ‘চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’, না ‘জুলাই বিপ্লব’, না ‘চব্বিশের গণ-বিদ্রোহ’-কোনটি?
আমরা যদি ঘটনাক্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহলে শুরুতে দেখা যায়-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটাপদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রাজু ভাস্কর্যে’র সামনে জড়ো হয়ে স্লোগানসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এর নাম ছিল ‘কোটাবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন’। দু-এক দিনের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হন চাকরিপ্রত্যাশীরা এবং ঢাকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা। আরও পরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যুক্ত হলে এর নাম হয় ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন’। শেষে ঢাকার নগরবাসী ও দেশের জনগণ যুক্ত হলে আন্দোলনের কলেবর ও পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে এক দফা দাবিতে স্বৈরাচারবিরোধী একটি সফল ‘ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থানে’ পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়; শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। আমরা ‘গণ-বিদ্রোহ’ নাম সরাসরি নাকচ করতে পারি, যদিও আন্দোলনের এক স্তরে ‘দ্রোহযাত্রা’ কর্মসূচি ছিল। ছাত্ররা রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে এরূপ কর্মসূচি প্রদান করেন। ছাত্র-জনতা পদযাত্রাসহকারে গণভবনে যান এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। কোনোরূপ বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। একে গণ-বিদ্রোহ বলা নিরর্থক। মূল বিতর্ক হলো আন্দোলন ও বিপ্লব নিয়ে। তাত্ত্বিক বিচারে আন্দোলন হলো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কিছু নিয়ে ন্যায়সংগত দাবিতে অথবা কোনোরূপ বঞ্চনা-নির্যাতন-অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী একদল লোকের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Movement. আন্দোলনের বিষয় এবং আন্দোলনকারীর শ্রেণিগত পরিচয় অনুসারে তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয় হতে পারে। এরূপ আন্দোলনে ব্যক্তির নেতৃত্ব ও একটি সংঘবদ্ধ দল থাকতে হয়। ইতিহাস থেকে কতক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। কলকাতার ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে ‘ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন’ (১৮২৬), রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ‘সতীদাহ প্রথা আন্দোলন’ (১৮২৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে ‘কুলীনপ্রথা রোধ’ ও ‘বিধবাবিবাহ প্রচলন’ আন্দোলন (১৮৫৬), ঢাকার আবুল হুসেনের নেতৃত্বে ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ (১৯২৬) ইত্যাদি। প্রথম ও শেষেরটি গুণগত বিচারে সামাজিক-বৌদ্ধিক এবং বাকি সব সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন ছিল। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আমরা ‘বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন’ (১৯৫২) করি, যা ছিল রাজনৈতিক।
বিপ্লবের বিবিধ সংজ্ঞা আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় দীর্ঘদিনের পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রশক্তিকে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে উৎখাত করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Revolution. এর যেমন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে, তেমনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব থাকে, থাকে শক্তিশালী সংগঠন ও প্রচারমাধ্যম। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের মতাদর্শ বা মূলমন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী (Libarty, Equality and Fraternity)। তারা সফল হয় এবং শাসক ষোড়শ লুইয়ের ‘রাজতন্ত্রে’র ও ক্যাথলিক চার্চের একচেটিয়া কর্তৃত্ব উৎখাত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। রাশিয়ার ‘জারতন্ত্রে’র বিরুদ্ধে অনুরূপ ‘রুশ বিপ্লব’ (১৯১৭) সংঘটিত হয়। উভয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ‘আমূল পরিবর্তন’ ঘটে। রাজনীতির আনুষঙ্গিক অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। কার্ল মার্ক্স অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু মূল্যায়ন করে থাকেন। রাজা-প্রজার, মালিক-শ্রমিকের শ্রেণিস্বার্থ থেকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণিসংঘাত ও শ্রেণিসংগ্রাম ঘটে থাকে। তার মতে, সমাজবিকাশের ধারায় একপর্যায়ে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিপ্লবের সূচনা হয়, যার প্রভাব সমাজ-সংস্কৃতির ওপর পড়ে রূপান্তর ঘটায়।
আমরা দেখেছি, প্রথমার্ধে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল অরাজনৈতিক ও অহিংস। পরে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে প্রথমে ছাত্র এবং পরে সাধারণ মানুষ নিহত হলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে এবং রাজনীতির দিকে মোড় নেয়। একসময় তা ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যায়। ছাত্র-জনতার দাবি কোটা সংস্কার বা বৈষম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পরিণত হয়। ফলে গণতন্ত্রের মুখোশধারী একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়। ফ্যাসিস্ট শাসকের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে, সংগ্রাম আছে, প্রাণনাশ-সম্পদহানি আছে, যা বিপ্লবী লড়াইয়ের মধ্যেও ঘটে থাকে। এমনকি জনসমর্থন লাভ করে আন্দোলনকারীদের পছন্দসই ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার’ও গঠিত হয়, ছাত্ররাও যার অংশীদার। যারা দেশ চালাচ্ছেন, তাদের শ্রেণিগত চরিত্র কী? তারা কী করছেন? ৯ মাস পূর্ণ হলো, তারা সংস্কার নিয়ে মেতে আছেন। কী কী সংস্কার? মূলত রাষ্ট্র সংস্কার তাদের লক্ষ্য। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য কোথায় গেল? এটাই কি বিপ্লবোত্তর আমূল পরিবর্তন? মুখে যা-ই বলুক, আসলে পুরো বিষয়টি বিপ্লব নয়। ছাত্ররাও বিপ্লব বলে দাবি করেননি। তাদের স্লোগানে ‘বিপ্লব’ শব্দটি নেই। লেখক-গবেষক-তত্ত্ববিদ বদরুদ্দীন উমর একটি ‘বিশেষ সাক্ষাৎকারে’ বলেছেন, ‘এই যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে, এটা তো কোনো সামাজিক বিপ্লব নয়, যদিও এর মধ্য দিয়ে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। একটা নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট সরকার অক্টোপাসের মতো দেশকে আঁকড়ে ধরেছিল, সেটা উৎখাত হয়েছে। ... কিন্তু এই সংগ্রামের তো কোনো শ্রেণি-পরিচয় নেই, এটা কোনো শ্রেণি-সংগ্রাম ছিল না। একটা রিগ্রেসিভ (নিপীড়নমূলক) সরকারকে ফেলে দিয়েছে এই অভ্যুত্থান। যারা ফেলে দিয়েছে, তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না। যারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই ছাত্রদের মধ্যে তত্ত্বগত বোঝাপড়া খুব একটা আছে, সেটাও দেখা যাচ্ছে না।’ (প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল। ২০২৫)। আসলে আন্দোলনটি অসমাপ্ত থেকে গেছে, তার বড় প্রমাণ শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পলাতক হলেও তার নিয়োগপ্রাপ্ত ও বশংবদ রাষ্ট্রপতি স্বপদে বহাল আছেন। অতি উচ্চপদে আরও অনেকে আছেন, নাম না-ইবা বললাম। আমলারা তো অগুনতি। অর্থাৎ স্বৈরাচার শাসক গেছেন, কিন্তু শাসকের শ্রেণিচরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। এখন যারা দেশ চালাচ্ছেন, তাদের শ্রেণিচরিত্রই-বা কী? এর চেয়ে বেশি কথা বলা ঠিক হবে না, তাতে তিক্ততা বাড়ে।
সুতরাং ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে ‘বিপ্লব’ বানানো কিংবা তাদের ‘বিপ্লবী’ বলে আখ্যাত করা চলে না। একে ‘ছাত্র-জনতা আন্দোলন’ অথবা ‘গণ-অভ্যুত্থান’ বলাই সংগত। এর আগে মাস বোঝাতে ‘জুলাই’ অথবা সাল বোঝাতে ‘চব্বিশ’ যোগ করে জুলাইয়ের বা চব্বিশের ছাত্র-জনতা আন্দোলন’ অথবা জুলাইয়ের বা চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান’ নামে চিহ্নিত করা যায়। আমি ‘জুলাই ’২৪-এর গণঅভ্যুত্থান’ নামের পক্ষপাতী।