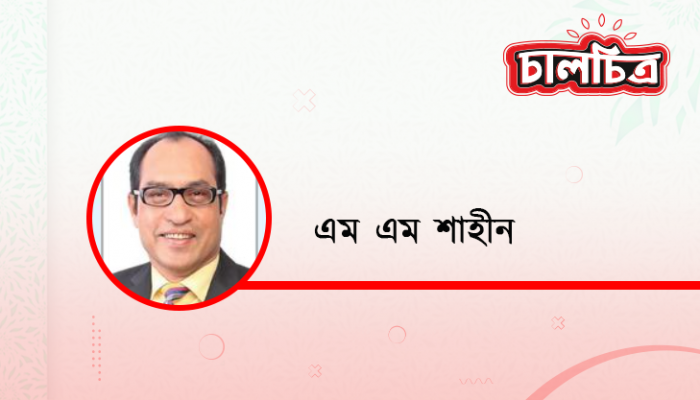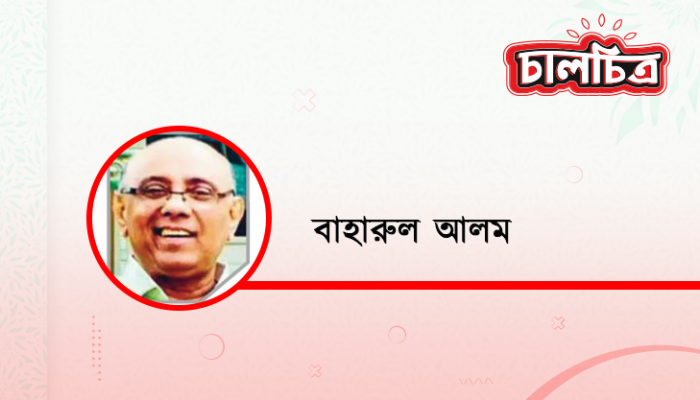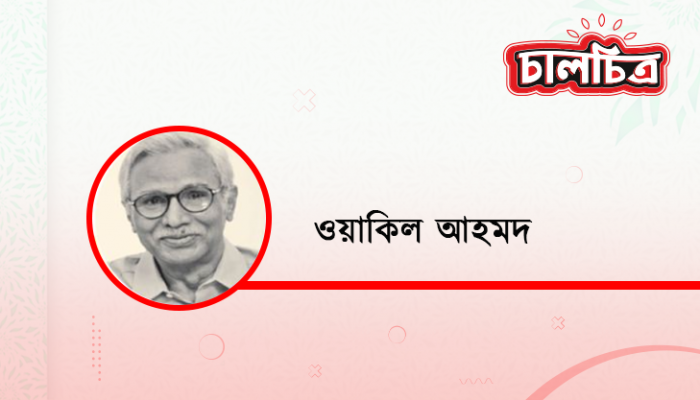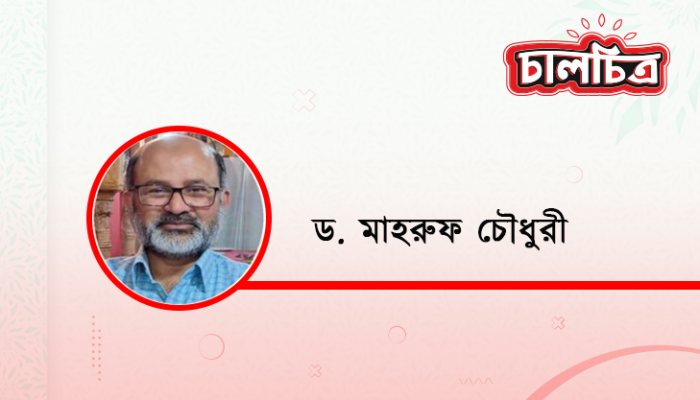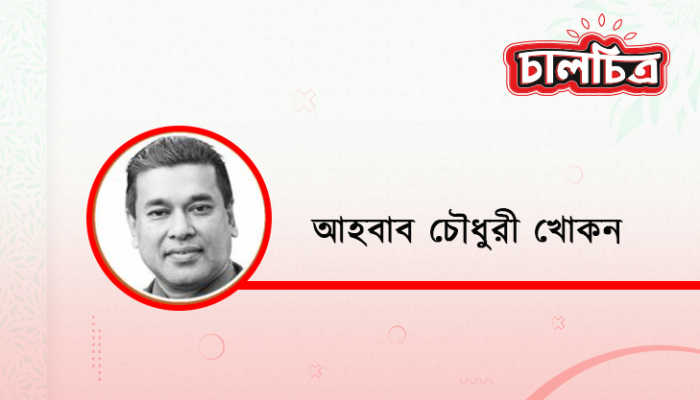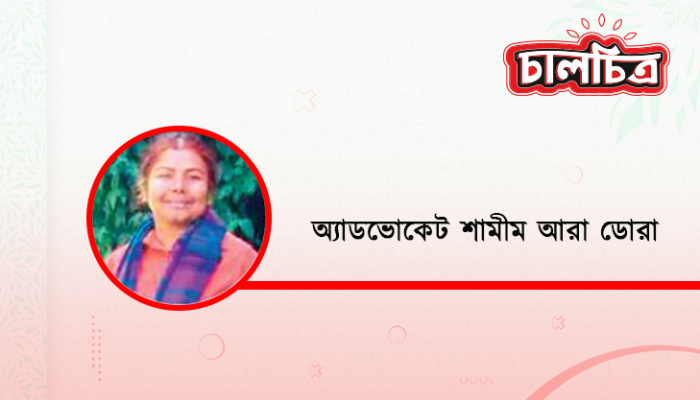বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন। তিনি একাধারে লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশে খ্যাতিমান।
চট্টগ্রামের হাসিমপুরের গাছবাড়িয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ বাড়িতে ক্রমে ক্রমে বেড়ে আহমদ ছফার মাঝে শিশুকালেই মেধা ও প্রতিভার দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রাইমারিতে পড়ার সময় রামচন্দ্রকে নিয়ে একটি পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে তিনি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুত্রের এই কৃতিত্বে বাবা হেদায়েত আলীর (ধন মিয়া) নির্দেশে জুমার নামাজের পর মসজিদের মুসল্লিদের সামনে তা পাঠ করতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য, গুরুজনের দোয়া ও শুভাশিষ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভেতর মেধা ও মননচিন্তার বিস্ময়কর প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়।
হাইস্কুলে পড়ার সময় তিনি বাম রাজনীতির ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তার অন্যতম কারণ ছিল সমাজের নানা রকম অন্যায়, অনাচার ও অসংগতি দেখতে দেখতে স্কুলজীবন থেকেই আহমদ ছফার চিন্তা ও দর্শনে এই পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারলেন যেকোনো কাজ সফল করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল কোনো প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে হলে এককভাবে করা যায় না। এ জন্য সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ শক্তির ভূমিকার প্রয়োজন। সে জন্য তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সংগঠনে যুক্ত থেকে মানুষকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যাশা ছিল, সামাজিকভাবে অবহেলিত মানুষকে শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা। মানুষের মুক্তি ও অধিকারের সমব্যবহার নিশ্চিত করা। তিনি সামাজিক অবক্ষয় ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করতেন। রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশে অরাজকতা ও গণমানুষের দুর্ভোগে খুব কষ্ট পেতেন। ফলে ওইসব কষ্টবোধ ও সংক্ষুব্ধতার ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মে একধরনের প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।
আমাদের সমাজের মানবতা-বিবর্জিত কুসংস্কার আর অনাচারবৃত্তির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালনের জবাব মেলে আহমদ ছফার লেখনীতে। অসাধারণ মেধা ও মননের ছাপ তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ ও গল্প-উপন্যাসের পরতে পরতে। তাঁর লেখা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক উপাদানে ভরপুর। তাঁর কয়েকটি কবিতার বইও আছে, যার অনেক কবিতা কালজয়ী। এ ছাড়া বেশ কিছু চিরন্তন গানও আছে তাঁর। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস এবং উপলক্ষ্যের লেখাগুলো পাঠককে নাড়া দেয়, শিহরিত করে। পাঠককে আলোড়িত করে এবং ভাবতে শেখায়। আমাদের চলমান সমাজ ও রাষ্ট্রপুঞ্জকে নাড়া দিয়ে যায়।
বাংলা সাহিত্যাকাশে আহমদ ছফার আবির্ভাব অনেকটা ধ্রুবতারার মতো। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর আশ্চর্যজনক বিচরণ ছিল। তাঁর মনন-ক্ষমতা এতই প্রখর ও ঈর্ষণীয় ছিল যে, অনেকটা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জীবনধারার সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যায়। নজরুলের অপ্রতিরুদ্ধ সাহসী চেতনার মতো আহমদ ছফা সব সময় রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সমাজে চেপে থাকা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। যেকোনো বৈষম্য ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। অসংগতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, লিখেছেন এবং মাঠপর্যায়ে কাজ করেছেন। জাতীয় চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তিনি বলেন :
‘একটি ভাববিপ্লবের মশালচি হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব।’ নজরুলের মননশীলতা, সৃজনক্ষমতা ও সৃষ্টিচেতনায় ঊর্ধ্বমুখী শিহরণের কথা তিনি সব সময় জোরের সঙ্গে বলতেন। নজরুলের সৃষ্ট বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে তিনি বলেন, “বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ জলস্তম্ভের মতো চেতনার ঊর্ধ্বে উড্ডীন অবস্থার প্রকাশ; তা যেমন চিত্তবিহারী, তেমনি বলিষ্ঠ। এই চিত্তবিহারী বলিষ্ঠতাই নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।” তিনি উচ্ছ্বাস ও আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের সাহিত্যের এ পর্যন্ত সর্বশেষ আদর্শ নির্মাতা এবং শেষতম শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের পুনর্মূল্যায়ন এখনো হয়নি।’
বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের নিয়ে এমন অসংখ্য মন্তব্য নির্বিশঙ্কভাবে আহমদ ছফা প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্য দর্শনেও তাঁর ভেতরকার সৃজন ও মননের শক্তিময়তার বহু নজির আছে। কখনো কোনো একপেশে মতবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি সমাজের সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীকেও পরোয়া করে চলেননি। যাকে মনে ধরেছে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন। সাহিত্যাদর্শে যেকোনো অসংলগ্নতা প্রশ্নে নিজের ভাবনাচিন্তা ও লেখায় রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকেও ছাড় দেননি। ব্যক্তিগতভাবে কবিগুরুর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সর্বব্যাপী সব মানুষের কথা বলতে ও লিখতে কিংবা সব মানুষ সম্পর্কে মূল্যায়নে ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ায় কতিপয় মৌলিক প্রশ্নে আহমদ ছফা তাঁর সংক্ষুব্ধতা ও আক্ষেপ প্রকাশ করেন।
এ প্রসঙ্গে ‘জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথকেই জিজ্ঞেস করতাম’ শিরোনামে একটি কালজয়ী প্রবন্ধে স্পষ্টত তাঁর প্রতিবাদী চেতনা, সংক্ষুব্ধতা ও সাহসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখেন, “গোত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার জীবনের মহত্তম মানুষ। জীবনের সমস্ত রকম সমস্যা সংকটে আমি তার রচনা থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেছি। আমার বোধবুদ্ধি যখন একটু সেয়ানা হয়ে উঠল, একটা প্রশ্ন নিজের মধ্যেই জন্ম নিল। আমি মুসলমান চাষা সম্প্রদায় থেকে আগত একজন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কিছু লিখেননি কেন? এ প্রশ্নটা মনের মাঝে জাগলেও প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস করিনি। আমাদের গোঁড়া মুসলমানরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে সকল অপপ্রচার করে থাকে, আমার প্রশ্নটিকে তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে আমাকে রবীন্দ্র-বিরোধীদের সঙ্গে এককাতারে দাঁড় করার ভয়ে অনেক দিন চুপচাপ ছিলাম। এখন আমার একটি উপলব্ধি এসেছে, যে যেভাবে ইচ্ছে গ্রহণ করুক, আমার মন যেভাবে বলছে আমি প্রশ্নটা সেভাবে উচ্চারণ করব। এখানকার রবীন্দ্রভক্তরা হয়তো রুষ্ট হবেন। তবে আমি নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথের রুহ মোবারক আমার প্রশ্নে কষ্ট পাবে না। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি ফুলের গন্ধ, পাখির গান, এমনকি গোধূলির আলোর কাছেও নিজেকে ঋণী ভাবতেন। সম্প্রতি ‘ফায়ার অব বেঙ্গল’ শীর্ষক এক হাঙ্গেরিয়ান মহিলার একটি চমৎকার উপন্যাস আমি পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। ঐ উপন্যাসের চরিত্রের একটি উক্তি ‘রবীন্দ্রনাথ যখন ধ্যানে বসতেন, ঘাসের অঙ্কুর গজানোর শব্দও তিনি শুনতে পেতেন।’ আমার প্রশ্নে আসি। অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রশ্ন। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুসলমান প্রজাদের নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প কিংবা উপন্যাস কেন লিখলেন না? এই মুসলমান প্রজারাই তো রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বের ঠাকুর জমিদারদের অন্ন সংস্থান করত। এই মুসলমান প্রজাদের জীবনের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যত বেশি জানতেন, গোটা ভারতবর্ষে সে রকম আর একজন মানুষও ছিলেন কি না সন্দেহ।”
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপর আহমদ ছফার শ্রদ্ধাবোধ ও ভক্তির অপার নিদর্শন ছিল। যাঁর প্রতি ছিল আকাশ পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু কবিগুরুর রচনার মধ্যে কোনো অসংগতি দেখা দিলে তো স্বাভাবিকভাবে তাঁকে কাঁদাবে, পীড়িত করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধার কমতি ছিল না। কবিগুরুর বিষয়ে তাঁর উক্তি হচ্ছে, ‘বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় আমার মন বসে না।’
আসলে আদর্শ ছায়ায় নিজের মননসত্তা পোক্ত হওয়া মানুষই পারেন অধিকারের আপন মহিমায় এমন শক্ত ও কঠিন সত্যের পক্ষে অবস্থান করতে। তাঁর মধ্যে একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব ও আবিষ্কারের নেশা ছিল। যিনি আমাদের সমাজের চিত্র ও চারপাশ দেখতেন। সমাজের প্রকৃত চিত্র তাঁর লেখার মধ্যে এঁকে নিতেন।
১৯৬৭ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর আহমদ ছফা একটি প্রবন্ধ সংকলন বের করেছিলেন। যার সম্পাদকীয় লিখেছেন ড. আনিসুজ্জামান। বাংলাবাজারের স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে সেটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ ছিল আকাশ সমান। তবু সাহিত্যের অসংগতির ব্যাপারে তিনি তাঁর আক্ষেপ, দুঃখবোধ ও কষ্টের কথা কেন এমনভাবে প্রকাশ করলেন, তা নিয়ে অনেকের মাঝে দ্বিধার সৃষ্টি হয়।
অন্যদিকে ‘শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তক লিখেও বঙ্কিমের উপন্যাসে মুসলমান-বিদ্বেষী লেখার কঠোর সমালোচনা করেছেন আহমদ ছফা। যা নিয়ে বঙ্কিমপন্থীরা ঢাকা ও কলকাতায় আহমদ ছফাকে কুপোকাত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর যুক্তির কাছে টিকতে পারেননি। কেননা, সাহিত্য সংস্কৃতি কোনো নাচের পুতুল নয়। কোনো মতলববাজ রাজনীতি কিংবা ধর্মান্ধতা নয় যে, কট্টর থেকে বিবেক-বোধহীন জড় পদার্থও নয় সেটি। আহমদ ছফার সাহিত্যদর্শন হচ্ছে সর্বজনীন। সব মানুষের জন্য নিবেদিত।
পৃথিবী ও প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আহমদ ছফা ‘উত্থানপর্ব’ নামে একটি সুসমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য ও রাষ্ট্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার কলাম চালিয়েছেন। স্বাধীনতার পর অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আহমদ ছফা স্বাধীন দেশের আলো ও বাতাসের স্নিগ্ধ পরশের দোলায় দুলতে দুলতে মুক্তহাতে লেখালেখি শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় মানবতাহীন বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। একশ্রেণির উগ্র বখাটে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দ্বারা ঢাকা শহরসহ অন্য শহরগুলোতে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ধন-সম্পদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তিগুলো সরকারি দলের লোকের দখলে চলে যেতে শুরু করল। আহমদ ছফা কঠোর প্রতিবাদ করলেন। তিনি কলাম লিখতে শুরু করলেন। এ ছাড়া ব্যাপক লুটতরাজ, রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কলাম লিখলেন। এই সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলে থাকতেন। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কল্যাণে লিখতে শুরু করলেন। শুধু তা-ই নয়, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাকশাল প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কখনো সমালোচনা করেননি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিও ছিল তাঁর আকাশ পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ। তিনি কখনো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো কটূক্তি করেছেন বলে আমার জানা নেই। এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কারও কারও সমালোচনা ও বক্রোক্তিকে তিনি কখনো আমলে নেননি।
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ যেন সরকারের ফাঁদে পা না দেন এবং বাকশালের খাতায় স্বাক্ষর না করেন, সে জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ করেন। আমাদের দেশের পরান্নজীবী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তিনি তার কষ্টবোধ ও সংক্ষুব্ধতা নিয়ে অনেক সাহসী কথা লিখেছেন। ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’ (১৯৭২) গ্রন্থে তিনি লেখেন, ‘বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রেণি। এরা চিরদিন হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। প্রবৃত্তিগত কারণে তারা ফ্যাসিস্ট সরকারকেই কামনা করে। কেননা একমাত্র ফ্যাসিস্ট সরকারই কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে সম্মান শিরোপা দিয়ে পুষে থাকে। অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোককে দিয়ে নিজেদের প্রচার-প্রোপাগান্ডা করিয়ে দেশের জনসমাজের স্বাধীন চিন্তা এবং প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ করেই ফ্যাসিবাদ সমাজে শক্ত হয়ে বসে। চিন্তাশূন্যতা এবং কল্পনাশূন্য আস্ফালনই হলো ফ্যাসিবাদের চারিত্র্য লক্ষণ।’
তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার কর্তৃক বাকশাল গঠনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন। বাকশালের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে বাকশালে যোগদানে নিষেধ করেন। একপর্যায়ে তখনকার সরকারদলীয় ক্যাডারদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। এই সময় অধ্যাপক কবির চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জমান, ড. আহমদ শরীফসহ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর কথায় আহমদ ছফা ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লায় চলে যান। সেখানে তিনি কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ডে যোগদান করেন। এখানে নিরিবিলি পরিবেশে জার্মান কবি গ্যাটে রচিত ‘ফাউস্ট’ অধ্যয়ন ও অনুবাদ শুরু করেন। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর মনোনিবেশের উজ্জ্বল গভীরতার প্রকাশ পেয়েছে।
তেমনি কবিতায়ও আহমদ ছফার সদর্প বিচরণ ছিল। কবিতার মানদণ্ডে সেগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাঁর রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বেশ কিছু গান ও গীতিনাট্য আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, আহমদ ছফা ১৯৭০ সালে জার্মান সাহিত্যিক গ্যেটের ফাউস্ট অনুবাদ শুরু করেন। সৃজনশীল প্রকাশনার পথিকৃৎ চিত্তরঞ্জন সাহা কর্তৃক তাঁর প্রকাশনা সংস্থা মুক্তধারা থেকে বিখ্যাত ‘ফাউস্ট’ অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
১৯৭৬ সালে ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের হাজার বছরের বিবর্তন বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক বাঙালি মুসলমানের পশ্চাদগামিতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জমান এবং বুদ্ধিজীবী সলিমুল্লাহ খানসহ আরও অনেকে আহমদ ছফার ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ (১৯৮১) প্রবন্ধসংকলনটিকে বাংলা ভাষায় রচিত শতাব্দীর ‘সেরা দশ চিন্তার বইয়ের’ একটি বলে মনে করেন।
আহমদ ছফার রচিত প্রতিটি উপন্যাসই সৌকর্যময়। সৃজনে বিষয়বস্তু এবং শিল্পশৈলীতে অনন্য। বাংলার মানুষের শিল্প-সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক অনুষঙ্গে প্রতিটি উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির যথার্থ পারঙ্গমতাও অসাধারণ। আহমদ ছফার ‘ওঙ্কার’ (১৯৭৫) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রমের সর্বোত্তম সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ।
শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ‘গাভী বৃত্তান্ত’ (১৯৯৫) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া ‘পুষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ’ (১৯৯৬) উপন্যাস আহমদ ছফার ঢাকা শহরের পার্কের বৃক্ষরাজির পুষ্পোদ্যান, ফুল, পাখি, বৃক্ষ-লতার রূপসুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিজস্ব স্বকীয়তার বর্ণনার বহিঃপ্রকাশ।
এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কতিপয় বিদগ্ধ কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীকে নিয়েও আহমদ ছফার রচনা রয়েছে। শিল্পী এস এম সুলতানের জীবনাচার নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে যে অনুপম বর্ণনা করেছেন, তা প্রশংসনীয়। সুলতানের শিল্পবোধ ও বিশাল শিল্পকর্ম সম্পর্কে আহমদ ছফা যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন; তেমনটি কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি সুলতানকে মনে করতেন একজন সত্যিকার পূর্ণায়ত মানুষ হিসেবে। যাঁর শিল্পকর্মে মানুষ ও প্রকৃতির বিষয় সুউজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে। একসময় তিনি চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন। চরিত্রগত অবয়ব ও জীবনাচারে দুজনই ছিলেন অবিবাহিত, বোহেমিয়ান ও ভবঘুরের মতো। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বৈষয়িক মোহ-বিবর্জিত নির্লোভ মানুষ ছিলেন তিনি।
আহমদ ছফা অকপটে বলতেন, ‘শিল্পী এস এম সুলতান ছিলেন মানবতা ও প্রকৃতিপ্রেমী দার্শনিক। বাংলার মাটির প্রতীক ও বাংলার খাঁটি মানুষ। আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা খুঁটিনাটি সমস্যাগুলোই ছিল তার শিল্পের উপাত্ত। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে তাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি।’ আহমদ ছফা মনে করতেন, এই বাংলায় সুলতানকে আরও বেশি দরকার। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানরাও বড় শিল্পী, ভদ্রলোক। তবে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে শিল্পের জায়গা করে দিতে হলে সুলতানদের কোনো বিকল্প নেই বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা নিজেই বলেছেন :
‘আমি মনে করি, আমার স্বীকৃতি নিয়ে পশ্চিম বাংলা কী বলতে চায়, সেটা আমার লুক আউট নয়। আমি পৃথিবীর গন্ধ এবং স্বাদ বুঝি। তুমি দেখবা আমি যখন আমেরিকায় যাব, তখন ওখানেও ঝড় তুলব। তখন ওখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখবে আমি কীভাবে মিশে গেছি। সুলতানের বিশালত্ব চিন্তা করো, ৭৬-এর আগে এই জায়ান্ট কোথায় ছিল? কেউ তাকে আবিষ্কার করল না কেন? এই আমি যাকে প্রেজেন্ট করেছি, আরেকজন লোক আসুক তো এমন।’
বাংলাদেশের সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট পণ্ডিত জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক প্রসঙ্গে রচিত স্মৃতিচারণ গ্রন্থ ‘যদ্যপি আমার গুরু’ স্মৃতিধর্মী গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধ বিচরণ ছাড়াও তিনি পত্রিকা সম্পাদনা ও দেশের স্বার্থে অসংখ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং উপলক্ষের লেখা লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে আহমদ ছফার রচনাবলি এক অমূল্য সম্পদ। নিজের সাহিত্যকর্ম ও চিন্তাদর্শন নিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ‘বাংলা সাহিত্যে আহমদ ছফার মেধা ও মননের তীক্ষèতার কারণেই বোধ হয় এমএ পাস করার পূর্বেই অধ্যাপক কবির চৌধুরীর (বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক) মাধ্যমে নিয়ম ও প্রটোকলের বাইরে আহমদ ছফা বাংলা একাডেমিতে তিন বছরের জন্য (পিএইচডি) ফেলোশিপ প্রোগ্রামের জন্য মনোনীত হন। কারণ হলো, সৃজনে, মননে এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে আহমদ ছফার ঈর্ষণীয় যোগ্যতা। আর যোগ্যতার সুষম ব্যবহার হলেই সাফল্যের পথ মসৃণ হয়।’
ছফা ভাই তাঁর প্রতি কবির চৌধুরী স্যারের অসামান্য অবদানের কথা একদিন আমাদের এক ঘরোয়া আসরে গল্পের ছলে বলে ফেলেছিলেন। আশির দশকে আমার তরুণতম ছাত্রজীবনে ছফা ভাইয়ের অসাধারণ জীবনচরিত সময়ের স্মৃতিগুলো যেন একেকটি সাহিত্য উপাখ্যান। তারপর নিউইয়র্কে একই ছাদের নিচে টানা তিন মাস।
স্মৃতিকে সঙ্গে করেই মানুষের বসবাস। ছফা ভাইয়ের সঙ্গে স্মৃতিসমূহ আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে। সেই স্মৃতি সাহিত্যে, মননে, সৃজনে এবং আমাদের যাপিত জীবনের পরতে পরতে। আহমদ ছফার সাহিত্যরচনা পাঠ করলে কখনো মনে হতো যেন স্রোতের বিরুদ্ধে বিবেকী সন্তরণ; যা পাঠ করলে মানুষকে ঘোরমুক্ত করে তোলে। অবক্ষয়ী সমাজ আলোর পথ দেখতে পারে। মানুষের মাঝে মানবিক আদর্শ ও বিবেকবোধ জাগ্রত করতে পারে।
ব্যক্তিগতভাবে সাদাসিধে সরল জীবনযাপনকারী আহমদ ছফা ছিলেন নিরন্ন মানুষের প্রতিভূ। সাহিত্যের আবেগ ও আদর্শে তাঁকে দুঃখী মানুষের বন্ধু এবং সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষিত যুবসমাজের আগামী দিনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে তিনি অনেকের কাছে তারুণ্যের প্রতীক।
স্বাধীনতার পর আহমদ ছফার কিছু লেখা নিয়ে ঢাকা ও কলকাতার সাহিত্যাঙ্গনে তুমুল আলোড়ন ও হইচই শুরু হয়ে যায়। কেননা, সাহিত্যে তিনি কোনো গোঁজামিল পছন্দ করতেন না। তিনি যা ভাবতেন, অকুণ্ঠচিত্তে লিখতেন এবং সেই অনুপাতে নিজের জীবনেও প্রতিফলিত করার জন্য দৃঢ় থাকতেন।
আহমদ ছফার ওপর আঠারো শতকের ইয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠাতা ক্ষণজন্মা কবি ও বুদ্ধিজীবী হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রভাব ছিল। যিনি তৎকালীন সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজে চেপে থাকা মানববিদ্বেষী কুসংস্কার, যেমন সতীদাহসহ এ ধরনের ভয়ংকর প্রথার মূলোৎপাটনের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডিরোজিওর মানবতাবাদী আন্দোলন ভারতবর্ষে ক্ষিপ্রতর ও জোরদার হয়েছিল। আহমদ ছফার মাঝেও সে রকম একটা উজ্জ্বল চেতনার নিদর্শন দেখা যায়। চিন্তা ও দর্শনে সামাজিক অবক্ষয় দূষিত রাজনীতিমুক্ত সুশীল সমাজ বিনির্মাণের পথে তিনি ছিলেন সক্রিয়। তাঁর মাঝে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতা ছিল না।
কবি হিসেবেও আহমদ ছফা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিতাগুলো যত বেশি পড়া যাবে, তাঁর ভেতরকার সাহিত্যমনস্ক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানার পথ সহজতর হবে। ‘কবি ও সম্রাট’ তাঁর সৃষ্টিশীলতার অনন্য দীর্ঘ সংলাপকাব্য। সেটিকে একটি সুদীর্ঘ কাব্যনাটক হিসেবেও বিচার করা যায়। কবিতার ফরম্যাটে নাট্যচরিত্রের ঢঙে কবিতাটির মূল্যমানকে উচ্চকিত করেছে। তেমনি ‘বস্তি উজাড়’, ‘লেলিন ঘুমোবে এবার’সহ বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ‘শুধু একটি শব্দের জন্য’ শিরোনামে কবিতার কটি লাইন এমন :
‘আমি গগনে মেঘ দেখামাত্র মেঘের অংশ
হয়ে গেলাম। বৃক্ষ দেখে বৃক্ষের আকার
ধারণ করলাম। যখন নদীর সান্নিধ্যে এলাম
ছলছল ধ্বনিতে বয়ে যাওয়ার আবেগ আমার
বুকের ভেতর তরঙ্গ সৃষ্টি করল। তারপরে
যখন আকাশের অভিমুখে দৃকপাত করলাম,
দেখলাম ঘুঙুর পরা নক্ষত্ররা একে একে
আমার প্রাণে এসে প্রাণের চেরাগ জ্বালিয়ে তুলছে।’
তেমনি ‘কবি ও সম্রাট’ গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র ‘মির’ তকির মতো তিনি বলেন :
‘মির :
জাঁহাপনা, খাকসার নালায়েক নাচিজ বান্দা
জন্মগুনাহগার, সবিনয়ে শ্রীচরণে নিবেদন রাখিÑ
আমার সহজ বাক্যে না নিন গোস্তাকি।
সম্রাট :
মির তকি মির, শশকের মতো শুধু ডানেবামে হেলো
নিজস্ব বয়ানটুকু মুকতসর বলো।’
‘বেতারে খবর ঝরে’ নামক কবিতায় তিনি জানান দেন :
‘সেই ঘৃণ্য দানবের নগ্ন বর্বরতা
ভিয়েতনাম সইবে না, সইবে না দুনিয়ার সংগ্রামী সেনানী।
আফ্রো’শিয়ার গহীন গহন বন, ফেনিল সমুদ্রতীরে।
মরুভর বুক কুঁড়ে অযুত নিযুত কণ্ঠ
বাতাসের হৃৎপিণ্ড চিরে চিরে কয়,
-আদিম বর্বর তেজ বলদীপ্ত অহিংস হৃদয়
হিংসায় হিংসায় আজ নব পরিচয়।
তাই ধমনীর শেষে লালে, লিখে যাবো
সংগ্রামের রক্তাক্ত আখর।’
আহমদ ছফার মননশীল কাব্যসম্ভারের পূর্ণতা এমনই উজ্জ্বল। জল্লাদ সময় (১৯৭৫) কবিতাটি প্রকাশিত পঁচাত্তরের কঠিনতম সময়ে। তিনি লেখেন :
‘আমাদের এ সময় সুসময় নয়
জোয়ারে হিন্দোল দোলা, ভাটার মন্থর
চেনাজানা ভদ্র নদী ভেবে
যেজন ভালোভাবে ডিঙ্গা পৈতৃক বিশ্বাসে
জেনে রাখো সর্বনাশ সম্মুখে তোমার।’
রাষ্ট্র ও সমাজে ব্যক্তিগত চাহিদা কিংবা কোনো লোভনীয় চাতুর্যের ফাঁদে পা দিতে অনেক বিদ্যজনকেও দেখা যায়। কিন্তু আহমদ ছফা ছিলেন তার সম্পূর্ণ উল্টো। কোনো লোভ ও স্পর্শকাতর স্বার্থপরতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সাধারণত মানুষের স্বভাব যেমন থাকে; সেসব উতরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্য রকম চরিত্রের একজন মনুষ্যত্ববোধের পূর্ণায়ত মানুষ। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে অনেকটা নজরুল, নিটসে, ডিরোজিও এবং ইয়েটসের প্রভাব পরিলক্ষিত। চিন্তা-চেতনায় প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের প্রতি গভীর অনুরাগ ও গুরুত্বশীল এবং সর্বোপরি মানবীয় গুণাবলীর একজন রোমান্টিক মানুষ। তিনি ছিলেন স্বার্থবিরোধী বিত্তবৈভবের প্রতি উদাসীন একজন সাদামাটা মানুষ। মানুষের কল্যাণ চিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম আদর্শ। চিন্তা-চেতনায় আপাদমস্তক একজন খাঁটি বাঙালি।
তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গপুরাণ, ‘গাভী বৃত্তান্ত’, ‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী’, ‘আলাতচক্র’, ‘সূর্য তুমি সাথী’, ‘অঙ্কার’, ‘একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন’ এবং ‘মরণবিলাস’। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘জল্লাদ সময়’, ‘লেনিন ঘুমোবে এবার’, ‘বস্তি উজাড়’, ‘দুঃখের দিনের দোহা’, ‘একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা’ ও ‘আহমদ ছফার কবিতা’ (কাব্য সমগ্র) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ ছাড়া অনুবাদগ্রন্থ ‘ফাউস্ট’, ভ্রমণকাহিনি ‘চৎড়ংঢ়বপঃরাব এবৎসধহু’, গল্পগ্রন্থ ‘নিহত নক্ষত্র’, ‘দোলা আমার কনকচাঁপা’ (ছোটদের), প্রবন্ধের বইয়ের মধ্যে ‘জাগ্রত বাংলাদেশ’, ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’, বাংলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে’, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা’, ‘বাঙালি মুসলমানের মন’, ‘শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ’, ‘আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধ’, ‘রাজনীতির লেখা’, ‘আনুপূর্বিক তসলিমা ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ’, ‘নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ’, ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’, ‘শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ’, ‘আহমদ ছফার প্রবন্ধ’, ‘রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ’, ‘বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র’, ‘আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’, ‘উপলক্ষ্যের লেখা’ এবং ‘সংকটের নানান চেহারা’। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে স্মৃতিধর্মী বই ‘যদ্যপি আমার গুরু’। এ ছাড়া ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ গ্রন্থ এবং আহমদ ছফার বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি বড় সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের জনজীবনের দুর্ভোগ, রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা ও রাষ্ট্রীয় অনাচারবৃত্তির প্রতিবাদে সংবাদপত্রে তাঁর সমকালীন লেখাগুলো ছিল একেকটা তীরের মতো। স্বাধীনতার পর ‘দৈনিক গণকণ্ঠে’র প্রধান সম্পাদক থাকাকালীন বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস নামে ধারাবাহিক কলাম লেখার মধ্য দিয়ে আহমদ ছফার মেধা, মনন ও সৃজনে তীক্ষè বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বলতর দিকটি প্রকাশ পায়।
লেখক-সাহিত্যিকদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তাদের স্বার্থে তিনি সর্বদা ছিলেন উদার। বিশেষ করে, নবীন ও তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের ভালো লেখা প্রকাশ করার জন্য তিনি সব সময় প্রেরণা দিতেন। তিনি নিজের অর্থে অনেক তরুণ মেধাবী লেখকদের বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস প্রথম বই ‘নন্দিত নরকে’ আহমদ ছফার উদ্যোগে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শুধু তা-ই নয়, হুমায়ূন আহমেদের পুরো পরিবার শহীদ মুক্তিযুদ্ধ পরিবার হিসেবে তাদের প্রতি আহমদ ছফার বিরাট ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ এবং মুহাম্মদ জাফর ইকবালের লেখায় উল্লেখ আছে। ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের একটি প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল আহমদ ছফা। তিনি (জাফর ইকবাল) অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও আবেগময় লেখাটিতে তাদের প্রতি ছফা ভাইয়ের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন।
আহমদ ছফার জীবনবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে তিনি সময়ের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারতেন। তাঁর ভেতরকার মানবিক গুণাবলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ অনির্বাণ হয়ে আছে। তাঁর রচনাবলির সবকিছুই সব সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগাঁথা সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাঁর রচনাসমূহ সকল সময়ের জন্য উপযোগী এবং তিনি তার ওপর সারা জীবন কাজ করেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় তরুণ কবি আবুল হাসানের পুনর্ভর্তি হওয়া দরকার ছিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য। কিন্তু আবুল হাসানের হাতে তখন কোনো টাকাপয়সা ছিল না। আহমদ ছফা বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার পর নিজের বইয়ের ‘রয়্যালিটির’ সম্পূর্ণ টাকা আবুল হাসানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাকে পুনর্বার ভর্তির জন্য। ছফা ভাইয়ের জীবনে এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে।
স্বাধীনতার পর আধুনিক ও রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কবি খুব অসুস্থ ছিলেন। আহমদ ছফা বিষয়টি জানতে পেরে প্রশাসনের ওপর খেপে যান। বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম কবি অসুস্থ, অথচ কোনো এক অজানা অজুহাতে সরকারের তরফ থেকে টাকা প্রদান বন্ধ থাকবেÑএটা আহমদ ছফা মেনে নিতে পারেননি। তিনি সহজে তা মেনে নেওয়ার মানুষ ছিলেন না। তিনি বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু করে দিলেন। প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন। অবশেষে সরকারের তরফ থেকে কবি ফররুখ আহমেদের জন্য টাকা প্রদানের পুনর্ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে তখনকার তরুণ কবি নির্মলেন্দু গুণকে অজ্ঞাত কারণে আর্মি গ্রেপ্তার করে রমনা থানাহাজতে নিয়ে গিয়েছিল। আহমদ ছফা সেই খবরটি পাওয়া মাত্র নির্মলেন্দু গুণকে ছাড়িয়ে আনার জন্য থানায় ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি গুণকে ছেড়ে দিতে থানার ওসির সঙ্গে বাগ্্বিতণ্ডা পর্যন্ত করেন। সাত দিনের মধ্যেই কবি নির্মলেন্দু গুণ ছাড়া পান। আরেক মেধাবী ও প্রতিবাদী তরুণ কবি ছিলেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। রুদ্র যখন পাকস্থলীর আলসারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, ছফা ভাই তাঁকে নিয়মিত দেখতে যেতেন। রুদ্রকে দেখে তার সঙ্গে সময় দিতেন এবং ফিরে আসার সময় রুদ্রের বালিশের নিচে টাকাভর্তি খাম রেখে আসতেন।
শুধু তা-ই নয়, তার আগে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রথম কবিতার বই ‘উপদ্রুত উপকূল’ ছফা ভাইয়ের খরচে প্রকাশিত হয়। রুদ্রর জীবন উপাখ্যান ও তসলিমা নাসরীনের সঙ্গে বিবাহপর্বসহ অনেক কিছুতেই আহমদ ছফার প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। তিনি রুদ্রর পড়ার খরচসহ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তেমনি অকালপ্রয়াত তরুণ ছড়াকার বাপ্পী শাহরিয়ারসহ অনেকের বই প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আহমদ ছফা সাহায্য করেন। মেধাবী তরুণ কবিদের সাহিত্যজগতে পরিচিত করেন। অকালপ্রয়াত মেধাবী তরুণ কবি রকিবুল হক ইবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের ওপর প্রেরণাধর্মী একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন।
আহমদ ছফা লেখক-সাহিত্যিকদের স্বার্থে তাদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার প্রত্যয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম লেখক শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবিরে কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসসহ অনেক বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিক যোগদান করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি সাহিত্য আসরের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিয়মিতভাবে সেসব সাহিত্য আড্ডা জমে উঠেছিল। ড. আহমদ শরীফ, রনেশ দাশগুপ্ত, আলাউদ্দীন আল আযাদ, কাজী সিরাজ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, সরদার ফজলুল করিম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল হালিম, সৈয়দ আকরম হোসেনসহ অনেকেই সাহিত্য আসরে যোগ দিতেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কবি শামসুর রাহমান ওইসব সাহিত্য আড্ডায় যোগ দিতেন।
বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের মতে, মীর মশাররফ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলামের পরে জনপ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি মুসলমান জনপ্রিয় সাহিত্যিক হলেন আহমদ ছফা। তাঁর রচনায় আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবোধ ও বাংলাদেশি জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতির কাজে মানুষের অংশগ্রহণ হয় যেমন তার প্রবৃত্তি, অভ্যাস ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে; তেমনি দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আহমদ ছফা তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন।
বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রয়েছে আহমদ ছফার বিচরণ ও মননের ছাপ। তাঁর মেধা, মননচিন্তা, দর্শন ও সাহিত্যাদর্শের প্রতিটি শাখায় প্রেম, বিরহ, দ্রোহ, বেদনাবোধ, প্রকৃতি ও মানবকল্যাণের দিকনির্দেশনা বিদ্যমান। তাঁর কর্মজীবন, শিল্পবোধ ও সাহিত্য ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অংশ হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। সব দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাতাসের মুক্ত সাহিত্যাদর্শের ঔজ্জ্বল্যেই আহমদ ছফা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও অনির্বাণ হয়ে থাকবেন।
(২৮ জুলাই আহমদ ছফার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে লিখিত)
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক



 এবিএম সালেহ উদ্দীন
এবিএম সালেহ উদ্দীন