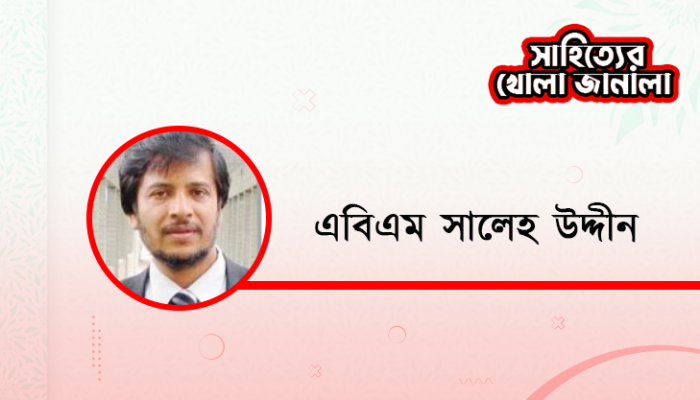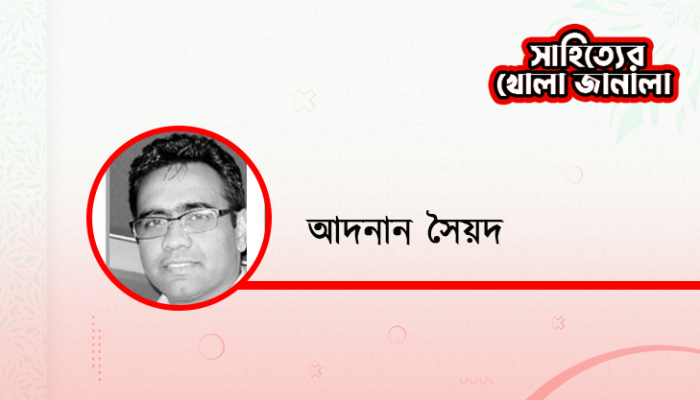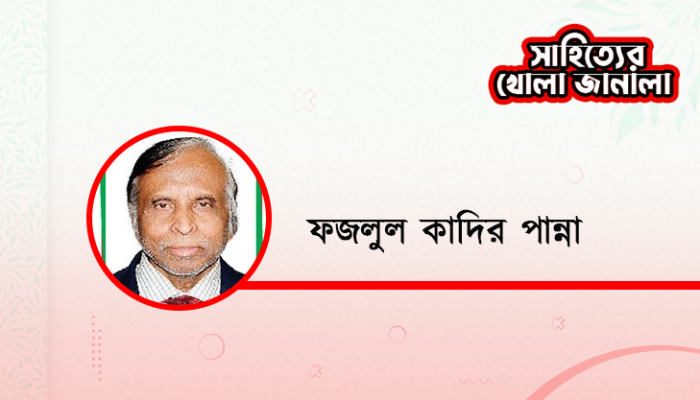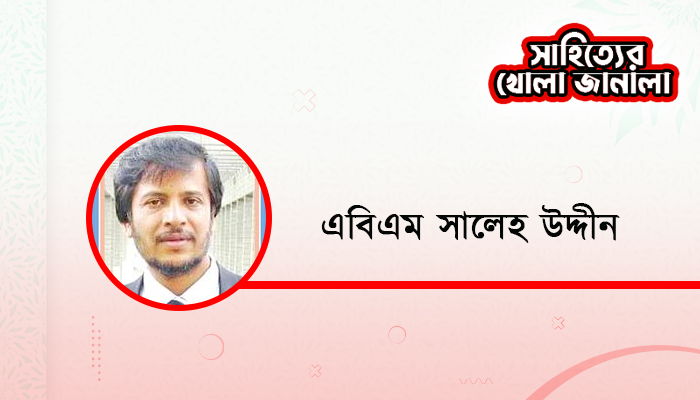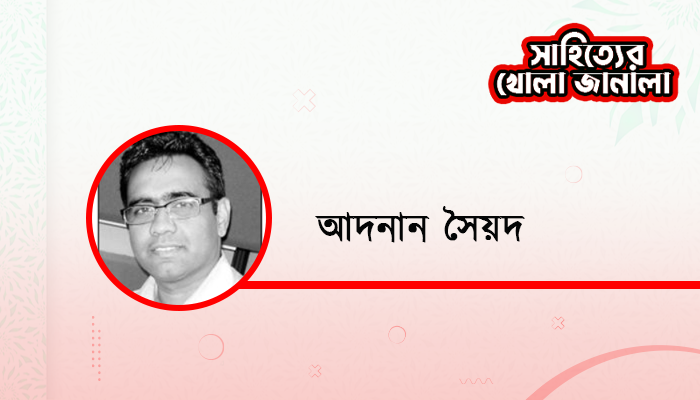ছোটবেলা থেকেই বিশ্বাসের আলো পেয়েছি বাবা-মা এবং গুরুজনের কাছ থেকে। বড় হয়ে বিশ্বাসের আলোতেই বড় মানুষের ভুবন দেখা ও জানার চেষ্টা করেছি। সুখে, দুঃখে, আনন্দ ও বেদনায় কতবার জীবন দোলায়িত হয়েছে। জীবননদীর বাঁকে বাঁকে ছন্দপতনের অভিধারায় মাঝে মাঝে হোঁচট খাই। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে যায়। আবার সংবিৎ ফিরে আসে।
বিশ্বাসের দীপ্তিই মূলত আমাদের জীবনের মূলধন। প্রত্যেকেই তাদের সেই সব মূলধন ধরে রাখতে চান। আমিও তার বিপরীত নই। জীবনের নানা রকম চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যেও বিশ্বাসের পথকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করি। এই প্রেরণা আমার মা ও বাবার নিকট থেকে পাওয়া। এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। বরং বিশ্বাসের দীপ্তির কথা ভেবে হৃদয়ে আনন্দ জাগে এবং তৃপ্তির ছোঁয়া অনুভূত হয়। নির্মেঘ নীল আকাশের নিচে স্রষ্টার লীলাভূমির সৌন্দর্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়। স্রষ্টার প্রতি অনন্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তা মানুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে।
পৃথিবী ও প্রকৃতির কত সহস্র রকমের স্নিগ্ধতা, শ্যামলীময় সবুজের বর্ণনা যেমন স্রষ্টা দিয়েছেন; তেমনি দিগন্তজুড়ে প্রকৃতি ও মানুষের জন্য দান করেছেন মুগ্ধতা আর মুগ্ধতা। সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনায় পৃথিবীর কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সুরের ঐশ্বর্য চিরন্তনভাবে গেঁথে রয়েছে, সেই মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টিতে।
সৃষ্টিকুলের মিলিত বন্ধনে ছড়িয়ে আছে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা। বন-বনানী ছায়াঘেরা চিরসবুজে আকীর্ণ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে কিংবা শান্ত নদীর বাঁকে বাঁকে সাজানো আমাদের গ্রাম, জন্মভূমি। নয়নজুড়ানো মাতৃদেশÑআমার প্রিয় মাতৃভূমি।
পৃথিবী ও প্রকৃতির পরতে পরতে মহামহিমের প্রবলতর মহিমার শেষ নেই। যদিও স্রষ্টার সৌন্দর্যের বিশালতা থেকে কিছুটা মানুষের জন্য বরাদ্দ। আমরাও সেই বরাদ্দের কিছুটা অংশীদার। আমাদের সকল প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়ার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। রাশি রাশি নক্ষত্রের পূর্ণায়ত আকাশের দিকে যখন তাকাই, পুণ্যবান হই তাঁরই সত্তার ঝলকে। তাই তো বিপুল আকুতিকে নিজেই গুনগুনিয়ে ব্যক্ত করি :
‘যদি চাহো, হতে পারো প্রেমময়
তবে, স্বকীয় শতরূপে হয়ে ওঠো পুণ্যবান
পরিপূর্ণ পুণ্যতায়...।’
আর রবীন্দ্রনাথ সেই মহামহিমের সৃষ্টিকুলের দিকে তাকিয়ে কী ভাবেন, যখন বিনিদ্র তপস্যায় জীবন সাহিত্যের মননশীলতায় মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের চিরন্তনী রূপকে নানান ভঙ্গিমায়, নানান আঙ্গিকে, বৈচিত্র্যের বৈভবের মহিমায় ফুটিয়ে তোলেন। তিনি তার শিল্প-সাহিত্যের সমুদ্রসম দিকনির্দেশনার মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা ব্যক্ত করেন। মানুষের জীবনের অনন্ত মায়াকে আনন্দ, বেদনা ও বিরহ-বিদ্রƒপের তুলিতে সুন্দরতম অবয়বে অঙ্কন করেছেন।
পৃথিবী, প্রকৃতির মাটি ও মানুষের ভুবনে তিনি থাকতে চেয়েছেন চিরকাল। রবীন্দ্রনাথ তারই ভাষায় বলেছেন :
‘আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে, কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে, বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;..’
শৈশবের পান্থপথ পেরিয়ে বড় হয়ে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্টি-সৃজনের অপার আনন্দে প্রকৃতির চিরায়ত সৌন্দর্যের বয়ান দিয়ে যাচ্ছেন :
‘ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।’
মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে মহামানবদের আগমনের ধারাবাহিকতায় মানুষের পৃথিবী ধন্য হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে এ বিশ্ব স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকুল সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। স্রষ্টার নিঃসৃত প্রেম আর প্রেমের চুম্বক আকর্ষণেই মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে মানুষেরই অন্তরে।
মহামানব গালিবের সুরে বলতে হয়। তিনি যেমন বলেন :
‘দুনিয়ার এই ভয়ানক উজাড় মজলিসে প্রদীপের মতো আমি প্রেমের শিখাকেই আমার সর্বস্ব জ্ঞান করলাম।’
তবু মহামহিম স্রষ্টার অপার সৌন্দর্যের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তিনি তাঁরই মহিমা গেয়ে যান :
‘হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সবচেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা-মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকাকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির,Ñ’
কী অনড় প্রত্যয়বোধ ও রুচি-বৈদগ্ধ্যের নিষিক্ত মায়ার কথনে মহান স্রষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশ।
খ্যাতিমান সাহিত্য গবেষক ও সাহিত্যের নির্মল চরিত্রের প্রাণপুরুষ আবু সয়ীদ আইউবের মতে : ‘যে বিশ্বাসটি সব ধর্মমতে বাস্তবিকই পাওয়া যায়, তা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস। সব ধর্মের মূলকথা হচ্ছে যে জগৎ শুধু নিয়মের রাজত্ব নয়, জগৎ ন্যায়নীতির রাজত্বও বটে।’
‘যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়ে যেয়ো না প্রভু !’
একধরনের অনাবিল বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার আলো বিচ্চুরিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে। আধ্যাত্মিকতার উন্মুল স্বভাবে তিনি সংগীতকে প্রার্থনার নিয়তসম্ভার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
তার চিরায়ত গানগুলো বারবার সেই স্বীকৃতি দিয়ে যায়।
‘অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হেÑ
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হেÑ
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হেÑ।’
শুধু সাহিত্যচর্চা কিংবা কবিতাই নয়; জীবনালোকের প্রতিটি স্তরের বিশুদ্ধ চরাচরে মানুষের নিয়তালোকের কঠিন বাস্তবতার নিদর্শন যার সাহিত্যের পরতে পরতে বিদ্যমান। তার সাহিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই। সীমার মাঝে অসীমের অপরূপ সৌন্দর্যই তার সাহিত্যের প্রকৃত ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র জীবনালোকের সকল অনুভব ও অনুভূতির শাণিত ঝংকারে তিনি সংগীতকেও চিরকালের জন্য স্থাপিত করে গেছেন। তিনি চিরস্মরণীয় ও চিরঞ্জীব। যিনি আমাদের দ্বান্দ্বিক জীবনের অগ্নিগর্ভ পথ ও প্রান্তরের বিস্ফোরণমুখী বৈষম্যের অগ্ন্যুৎপাত থেকে মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। মানুষের কল্যাণকামী দৃপ্ত প্রয়াসে তিনি তার সৃষ্টিশীলতায় নিখাদ প্রেমের রং দ্বারা শিল্প-সাহিত্যকে সাজিয়ে দিয়েছেন।
ধর্মের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দর্শন কিছুটা অপরিষ্কার থাকলেও মানবজাতিকে নিয়ে তিনি অনে্যর ধর্মীয় রীতিকে সম্মান করে যেসব চিন্তা করেছেন, তা সর্বজনবিদিত। ধর্মীয় বিশ্বাসে সর্বজনীনতার বিষয়ে সাহিত্যের শাখায় শাখায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।
১৯১৪ সালের ৮ জুলাই ব্রিটিশ কবি রবার্ট সেইমর ব্রিজকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘আমার ধর্মই আমার জীবনÑএটা আমার বয়সের সাথে সাথে বেড়ে উঠছেÑবাইরে থেকে কখনোই এটা আমার গায়ে লেখা হয়নি।’ (গু ৎবষরমরড়হ রং সু ষরভব—রঃ রং মৎড়রিহম রিঃয সু মৎড়ঃিয—রঃ যধং হবাবৎ নববহ মৎধভঃবফ ড়হ সব ভৎড়স ড়ঁঃংরফব.)। পরবর্তীতে ‘দ্য রিলিজিয়ন অব ম্যান’ (ঞযব জবষরমরড়হ ড়ভ গধহ) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তার নিজস্ব চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মকে তিনি মানবতাবাদ ও বিশ্বজনীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ‘ধর্ম মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।’
মানবপ্রেমের নিখাদ দীক্ষা নিয়ে তিনি স্রষ্টার নিকটতম পথের স্বরূপ-সন্ধান ও অবিরাম তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে গেয়ে ওঠেন :
‘হে দূর হইতে, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।’
...যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।’
Ñনৈবেদ্য
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে, যা তার সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনাশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি মনে করেন, এই আধ্যাত্মিকতা এবং সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একত্ববাদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি মানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বকে কখনো অস্বীকার করেননি। যেমন আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্যের কোলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েও পরবর্তীতে তার মনন চেতনায় অন্য রকম ঔজ্জ্বল্যে পরিণত হন। আধ্যাত্মিকতা (ঝঢ়রৎরঃঁধষরঃু) তার চিন্তা ও সাহিত্যকর্মের একটি কেন্দ্রবিন্দু বিষয়। তিনি কেবল একজন কবি বা সাহিত্যিকই ছিলেন না, বরং একজন গভীর আত্মসচেতন ও সমাজবিজ্ঞানী, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক।
‘খুদি’ বা আত্মসত্তার ধারণায় ইকবালের আধ্যাত্মিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো ‘খুদি’, অর্থাৎ আত্মচেতনা বা আত্মপরিচয়ের অনুভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, খুদি-চর্চা মানেই আত্মাকে শক্তিশালী করা, যা মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করে। সক্রিয় আধ্যাত্মিকতা (উুহধসরপ ঝঢ়রৎরঃঁধষরঃু) পোষণ করে ইকবালের আধ্যাত্মিকতা নিষ্ক্রিয় ধ্যানে সীমাবদ্ধ নেই, বরং কর্মমুখী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে। তার অবারিত কাব্য-দর্শন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। যেমন তার কবিতায় উঠে এসেছে :
‘তোমার আত্মাকে এত উচ্চে উন্নীত করো,
যাতে তোমার ভাগ্য নির্ধারণের আগে,
Ñনিজেই তোমার ইচ্ছা জিজ্ঞেস করেন।’
রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তার মাঝেও স্রষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্পণ হওয়ার নিখুঁত প্রেরণা বিদ্যমান, যা মানুষকে মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠতম স্থানে পৌঁছে দিতে পারে।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্যার আল্লামা ইকবাল ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের দুই মহামানব, যারা তাদের সময়ের সাহিত্য, দর্শন ও সাংস্কৃতিক চেতনায় রেনেসাঁস এবং মানুষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখেন। আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে কুমিল্লার একটি আশ্রমের উৎসবে কবিকে সংবর্ধনার উত্তরে বলেছেন, ‘আত্মাই শক্তির উৎস। এই শক্তির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে হবে। অভয় আশ্রমের কর্মীরা এরূপ আত্মত্যাগ করছেন বলে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি এখানে এসেছি।’
Ñইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ (পৃষ্ঠা-৫২)
ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, ‘এটা স্পষ্ট যে আমার ধর্ম একজন কবির ধর্ম এবং কোনো গোঁড়া ধার্মিক লোকের মতন নয় এবং কোনো ধর্মতাত্ত্বিকের মতো হবে না। ধর্ম আমার গানের অনুপ্রেরণার মতো অদেখা এবং কোনো নাম না-জানা পথ ধরেই আমার নিকট এসেছে। যেখানে আমার ধর্মবিশ্বাস, আমার কাব্যিক জীবনের মতো একই রহস্যময় পথের অনুসরণ করেছে। তারা কোনো না কোনোভাবে একে অপরের সঙ্গে মেলবন্ধনে সংগোপনে আবদ্ধ হয়েছে।’
আমাদের সাহিত্যজগতের নাস্তিক্য ধ্যান-ধারণার অনেকে বোঝাতে চান, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিশীল ও নাস্তিক। ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে থেকে তিনি এমন এক আদর্শের কথা বলেছিলেন, যেখানে ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। তাদের সেই ধারণার কোনো দলিল নেই। কিন্তু তিনি যে সারা জীবন আস্তিক্যবাদী ও উদার মনোভাবাসম্পন্ন মানবতাবাদী মহাকবি ছিলেন, তার অসংখ্য প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, ধর্ম পালনে তার অনীহা না থাকলেও তিনি তার মতো করে পালন করতেন। কারও কারও মতে, রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সজ্ঞানে পরিহার করতেন, কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অনেকের অনেক ধরনের ধারণা রয়েছে। তবে এ কথা সত্যি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মচিন্তা ছিল অদ্বৈতবাদী ও মানবতাবাদী। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, তবে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও গোঁড়ামির বিরোধিতা করতেন। তার ধর্মচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও মানবতাবাদ এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করা। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটে মানুষের সেবায় এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে।
পরোপকার, মানবসেবা ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।
ইসলাম ও মুসলমানদের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ছিল পরিষ্কার। তিনি মনে করতেন, ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের মতো গুটিকয়েক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তুলনা করা যায়। বৃহৎ পরিসরে মুসলিমরা জীবন দিতেও দ্বিধা করেন না।
কুসংস্কারের বাইরে সব ধর্মের মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অটুট। হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্মণ ধর্ম ছাড়াও বাংলার বাইরে একসময় তিনি শিখদের তীর্থস্থল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। মিসর, ইরান, ইরাক, তুরস্কসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে রবীন্দ্রনাথ সফর করেছেন। সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে তিনি বিপুল সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রতিটি দেশে তাকে রাজকীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। মুসলমানদের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থানসমূহের প্রতি তার মুগ্ধতা ও মোহময় টান ছিল। তবে তার সমসাময়িক কালে এমন কথাও উঠেছিল, মুসলিম জনগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে পরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করেছিল, সে তুলনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। তিনি চাইলে তার সাহিত্যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের কথা অনেক বলতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের তুলনায় তিনি হিন্দুদের প্রতি ছিলেন উদার। হিন্দুদের মানবাধিকার প্রসঙ্গে অনেক লিখেছেন এবং তাদের ইতিহাসকে তার সাহিত্যে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ নিজের জমিদারির প্রজাদের বাইরে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তিনি তেমন কিছুই করেননি। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক ও বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা অনেক আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি প্রবন্ধে লেখেন :
‘রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার জীবনের মহত্তম মানুষ। জীবনের সমস্ত রকমের সমস্যা সংকটে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেছি। বোধবুদ্ধি যখন সেয়ানা হয়ে উঠল, একটা প্রশ্ন নিজের মধ্যেই জন্ম নিল। আমি মুসলমান চাষী সম্প্রদায় থেকে আগত একজন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কিছু লেখেননি কেন? ... আমার মন যেভাবে বলছে আমি প্রশ্নটা সেভাবে করব। এখানকার রবীন্দ্রভক্তরা হয়তো একটু রুষ্ট হবেন। তবে আমি নিশ্চিত, রবীন্দ্রনাথের রুহ মোবারক আমার প্রশ্নে কষ্ট পাবে না। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি ফুলের গন্ধ, পাখির গান, এমনকি গোধূলির আলোর কাছেও নিজেকে ঋণী ভাবতেন...।
‘আমার প্রশ্নটিতে আসি। অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রশ্ন। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। রবীন্দ্রনাথ তার মুসলমান প্রজাদের নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প কিংবা উপন্যাস কেন লিখলেন না? এই মুসলমান প্রজারাই তো রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বের ঠাকুর জমিদারদের অন্ন সংস্থান করত।
‘এই মুসলমান প্রজাদের জীবনের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যত বেশি জানতেন, গোটা ভারতবর্ষে সেরকম আর একজন মানুষও ছিলেন কি না সন্দেহ। এই প্রজাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চারণ করেছেন। কিসে তাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং নানা বাস্তব কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছেন। এ প্রজাদের কল্যাণের আকাক্সক্ষায় একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে এনেছিলেন। তার পরও রবীন্দ্রনাথ মুসলমান চাষাদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প লিখতে পারলেন না কেন?’
(আহমদ ছফা : ব্যক্তি, সমাজ সাহিত্য : ১৩৯-১৪০)
যা-ই হোক, আগের কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম রাজা-বাদশাহ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব মুসলিম কবি-সাহিত্যিক পছন্দ করতেন এবং এখনো তিনি সেই মর্যাদায় ভূষিত রয়েছেন। তিনি তার অনেক লেখায় ইরানের বিশ্ববিখ্যাত কবি হাফিজ, শেখ সাদি, ওমর খৈয়াম ও ফেরদৌসীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে তার সম্মানবোধ ছিল অসামান্য। লেখক অমিতাভ চৌধুরী বইতে আছে, ১৯৩৮ সালে কামাল পাশার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮ নভেম্বর আয়োজিত এক শোকসভায় বলেন, ‘তিনি (কামাল) তুর্কিকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তিনি তুর্কিকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন।’
(ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ : ১৬)।
রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার ইরানে গিয়েছিলেন। বয়সের চাপে ন্যুজ না থেকে পঁচাত্তর বছরের উপান্তে পৌঁছেও পারস্যের ইরানে হাফিজের সিরাজ এবং শাহনামার ফেরদৌসীর কবরে গিয়েছেন। ১৯২৬ সালে মিসরের কায়রোতে রাজকীয় সম্মানে কয়েক দিন থাকার সময় একদিন তৎকালীন আরব্য কবি আহমদ সৌকির বাড়িতে বেড়াতে যান। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে মুসলমানদের উদ্যোগে অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। এখনো রবীন্দ্রনাথের অবস্থান উপরে। ১৯২৬ সালের ২৯ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ কায়রোর বিশ্ববিখ্যাত জাদুঘর পরিদর্শনে গিয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ নামক বইতে রবীন্দ্রনাথ মিসরের বাদশাহ ফুয়াদের সঙ্গে কয়েক হাজার বছর আগের শিল্প-সাহিত্যের ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ‘কায়রো জাদুঘরের’ বিশদ বর্ণনা করেন।
রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও প্রখর ধর্মবোধ থাকার ফলে তিনি ঈশ্বর উপাসনার অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। যেমন :
‘আমার পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গা
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।’
এই গানে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য কামনা করেছেন।
তেমনি ‘হে মোর চিত্ত, ফুল্ল মালঞ্চে’ গানটিতে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহান স্রষ্টার নিকট নির্মোহ, নির্মল পৃথিবী ও মানুষের জীবনের সৌন্দর্যের সন্ধানেও কবি ব্যাকুল। তাই তো তিনি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন :
‘আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার
ঢাকা ধুইয়ে দাও।’
সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গান রয়েছে :
‘দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
কাছে থেকে চিনতে নারি,
কোন্ দিকে যে কী নেহারি ॥’
রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের সৌন্দর্য, গতিশীলতা, সাহিত্যের বিশালতা, জীবনবোধ ও সাহিত্যকর্ম এবং তার সৃষ্টিক্ষমতার বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবোধ ছিল বলেই অসংখ্য গান এবং কবিতার সুরে সুরে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে মানুষের ধর্মীয় বাণীর মিলিত সম্ভারে অবিস্মরণীয় ও অনির্বাণ হয়ে আছেন।
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক।



 এবিএম সালেহ উদ্দীন
এবিএম সালেহ উদ্দীন