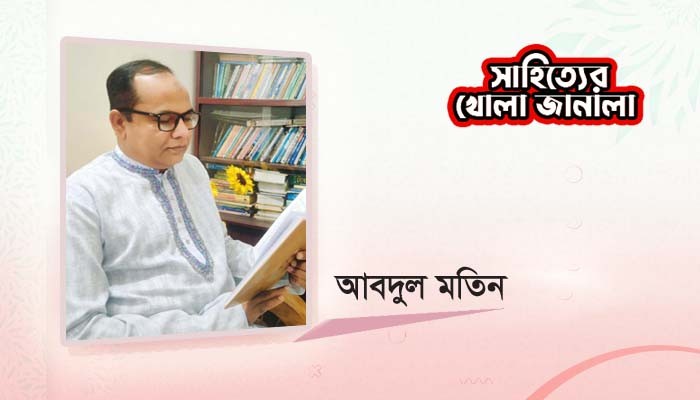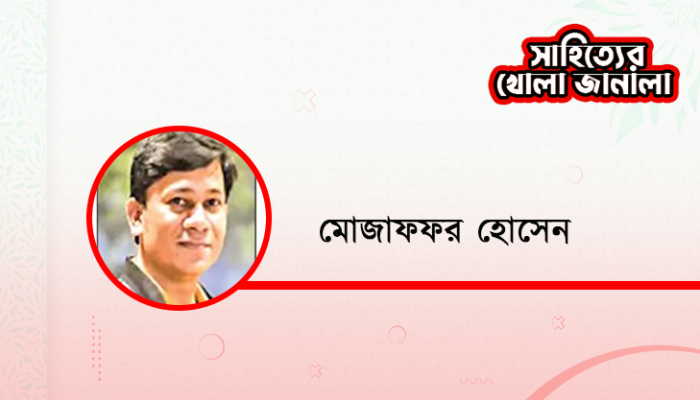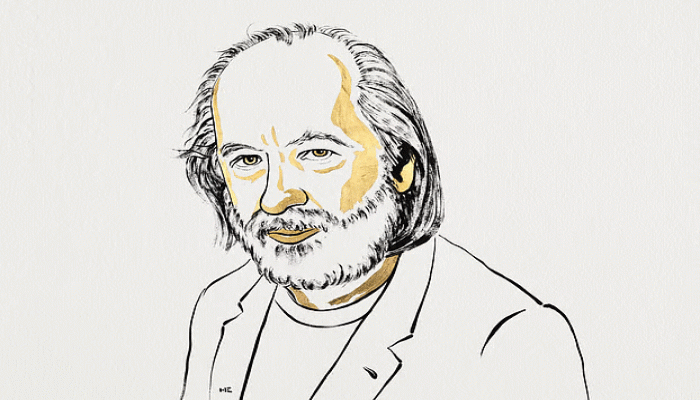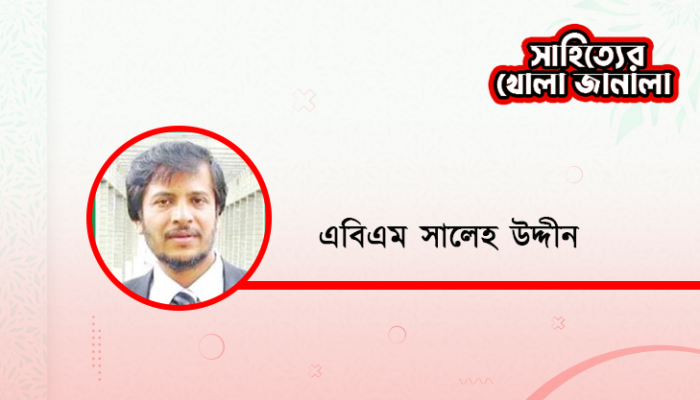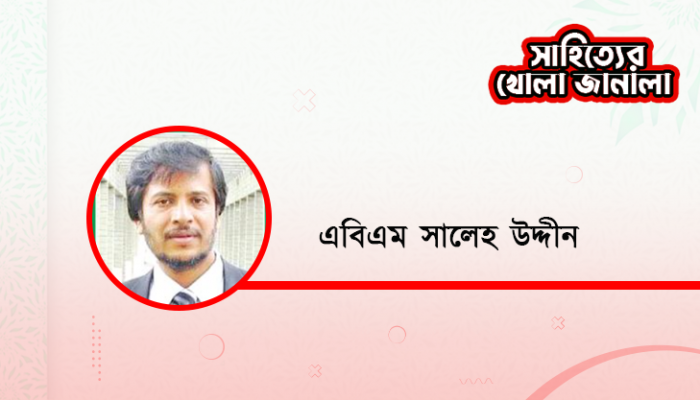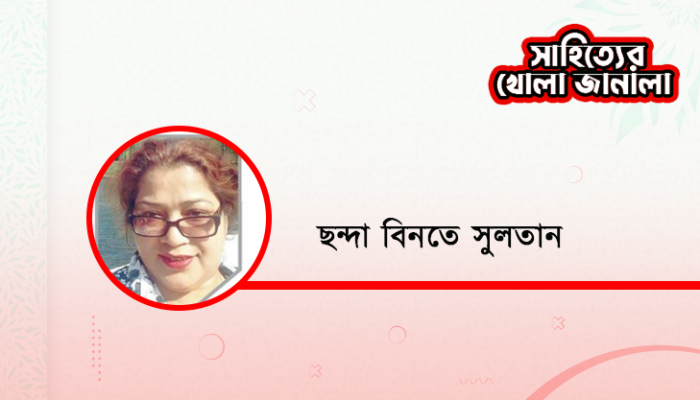ছোটো বেলায় পড়া, ঈশপের সেই মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের গল্পটি দিয়ে শুরু করা যাক। গল্পটি আমি একা পড়িনি - আমার সময়ে, আমার আগে পিছে সবাই পড়েছে। অবশ্য এখনকার ছেলেমেয়েরা পড়ে কিনা, তা বলতে পারছি না। যদি এখন পর্যন্ত কোনো একজন তার ছেলেবেলায় না পড়ে থাকেন, তাহলে তার উদ্দেশ্যেই গল্পটি আর একবার বলা যেতে পারে :
এক গ্রামে ছিল এক রাখাল বালক। গ্রামটি ছিল বিশাল এক বনের ধারে। রাখাল বালক সে বনের কাছেই গরু চড়াতো আর নানান মিথ্যা দিয়ে গ্রামের মানুষদের বোকা বানিয়ে মজা পেতো। একদিন সে বনের ধারে গরু চড়ানোর সময়, কেবলই মজা করার জন্যে 'বাঁচাও বাঁচাও, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে ', বলে চিৎকার করতে লাগলো। গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে বালকটিকে উদ্ধার করতে ছুটে এলো। কিন্তু এসে দেখে, সব মিথ্যে - কোথাও বাঘ নেই। রাখাল বালক মজা পেলো, গ্রামবাসী কিছুটা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলো। কিছুদিন পর কেবল মজা পাওয়ার জন্যে রাখাল বালক আবার 'বাঘ বাঘ' বলে চিৎকার করলো। গ্রামবাসীও আগের মতোই লাঠিসোটা নিয়ে এসে বোকা বনে ফিরে গেলো। তৃতীয় দিন সত্যিই সত্যিই বাঘ এসে রাখাল বালককে আক্রমণ করলো। রাখাল বালক তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে 'বাঘ বাঘ' বলে আপ্রাণ চিল্লাতে লাগলো, কিন্তু বারবার ধোঁকা খেয়ে গ্রামবাসী এবার আর তার সত্যি কথাটাও বিশ্বাস করলো না। ফলে বাঘের কাছে তাকে প্রাণ দিতে হলো।
ঈশপের গল্পগুলোর শেষে একটি শিক্ষামূলক উপদেশ থাকে। এ গল্পেও ছিল। এখানে শিক্ষণীয় বিষয়টি ছিল :
কখনো মিথ্যা বলতে নেই। বারবার মিথ্যাচার করলে এক সময় সত্য কথাটাও মানুষ বিশ্বাস করে না, আর পরিনামে তার ফল ভোগ করতে হয়।
ঈশপের অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পটিও একটি সরল গল্প। এখানে রাখাল ছেলেটি মিথ্যাচার করতো কেবল কৌতুক বশে, মিথ্যা দিয়ে কোনো ফায়দা নেয়ার অভিপ্রায় তার ছিল না। মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর কোনো চেষ্টাও সে করেনি। তবে বারবার মিথ্যা বলে বলে সে নিজেই তার অজান্তে নিজের উপর বিশ্বাসের একটা সংকট অবস্থা তৈরি করেছিল। যার ফল তাকে একাই ভোগ করতে হয়েছে, অন্য কেউ এর ফলভোগী নয়। কিন্তু প্রাচীনকালের এ সরল গল্পটির প্রভাব কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে বর্তমানে এসে সাংঘাতিকভাবে জটিল আকার ধারণ করেছে। এখন মানুষ মিথ্যা বলে কৌতুক বশে, মিথ্যা বলে ফায়দা লোটার জন্যে, মিথ্যা বলে মিথ্যাকে সত্য রূপে চালিয়ে দেয়ার জন্যে, মিথ্যা বলে মিথ্যার উপর ভর করে চরম জিঘাংসা হাসিল করার জন্যে।
এখন মানুষ কেবল গল্পচ্ছলেই মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলে পরিকল্পনা করে - ঠাণ্ডা মাথায়। এখন মানুষ একা একা মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলে দলবেঁধে - সংঘবদ্ধভাবে। এখন মিথ্যা কেবলি একটি গল্পের বিষয় নয়, এখন এটি একটি পরিকল্পিত রূপরেখার বিষয়।
আজকাল মিথ্যারও শৈল্পিক রূপ তৈরি হয়েছে। মিথ্যার শৈল্পিক রূপটি প্রথমে শুরু হয়েছিল জার্মানিতে - যুদ্ধবাজ একনায়ক হিটলারের সময়ে। হিটলারের মোসাহেব প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস মিথ্যাচারের উপরে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল।
তত্ত্বটি হলো :
আপনি যখন কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলবেন এবং সেটি সবার সামনে বারবার বলতে থাকবেন, তাহলে একসময় দেখবেন লোকে সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।
মিথ্যার উপর গোয়েবলসের তত্ত্বকথাটি তৎকালীন জার্মান সমাজে দারুণ কাজ করেছিল।
একনায়ক হিটলার কোনো নির্জলা মিথ্যাকে রংচং মাখিয়ে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গোয়েবলসের অতুলনীয় পারদর্শীতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং নিপুণতার সাথে এ কাজটি সম্পন্নের নিমিত্ত তাকে প্রচার মন্ত্রী বানিয়েছিল। মিথ্যাকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে গোয়েবলস তার চাকরিদাতা হিটলারের প্রতি অনুগত হয়ে নিষ্ঠার সাথে, সুনিপুণভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছিল এবং মনিবসহ নিজেকে ধ্বংসের আগমুহূর্ত পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিল।
এটা সর্বজন বিদিত যে, ইহুদিদের উপর হিটলার সাংঘাতিকভাবে নির্মম ছিল। এ কারণে সে ইহুদি নিধনে ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য গনহত্যা পরিচালনা করেছিল। কী কারণে সে ইহুদিদের উপর বেমাত্রায় ক্ষিপ্ত ছিল, তা নিয়ে নানা জনের নানা মতবাদ, নানান তত্ব্বকথা চালু আছে। সে যাইহোক হিটলারের ইহুদি নিধনের মিশনকে গোয়েবলস নানান মিথ্যাচারের বেসাতি দিয়ে জার্মানদের সামনে উপস্থাপন করেছিল। উপর্যুপরি মিথ্যার বেসাতিতে বিভ্রান্ত হয়ে জার্মানরা বিশ্বাসের সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। এক পর্যায়ে তারা (সবাই নয়) বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ইহুদি নিধন তেমন কিছু পাপের কাজ নয়। হিটলারের নাৎসি পার্টি এবং নাৎসি বাহিনীর সদস্যরা তো ইহুদি নিধনকে পূণ্যের কাজ হিসেবে মনে করতো। বস্তুত গোয়েবলস, তার গুরু হিটলারের সকল প্রকার জিঘাংসা ও উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার নিমিত্ত বহুমাত্রিক কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিল এবং অধিকাংশ জার্মানকে এটা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, হিটলার যা করছেন তা জার্মানদের মঙ্গলের জন্যই। একজন গোয়েবলসের কূটকৌশল আর ধোঁকাবাজির কাছে সিংহভাগ জার্মানের বিশ্বাস সংকটে পড়েছিল, ফলে এর খেসারত জার্মানদের তো বটেই বাদবাকি বিশ্বের সকল মানুষকেই কমবেশি দিতে হয়েছিল।
সে যাই হোক, গোয়েবলস বা হিটলার এখন অতীত। তাছাড়া গোয়েবলস, হিটলার, এরা ছিল জার্মান। জার্মানি আমাদের থেকে বহু দূরের একটি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজিক কাঠামো, সংস্কৃতিগত আচরণ, - কোনোকিছুতেই জার্মানদের সাথে আমাদের কোনো মিল নেই। কাজেই জার্মানদের কথা বাদ। এরচেয়ে বরং আমাদের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক আচরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির আলোকে আমাদের জাতিগত বিশ্বাসের স্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক।
এতোক্ষণ তো হিটলার, গোয়েবলসের সমালোচনা খুব নির্ভয়ে করে গেলাম। কিন্তু অন্যদের সমালোচনা করা যতো সহজ, নিজেদের বেলায় তা ততো কঠিন, - নয় কি? বিশেষ করে আমরা জন্মগতভাবে এমন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার ফলে আমরা অন্যের সমালোচনায় যতো মুখর, আত্মসমালোচনায় ততো নিরব। আর অন্যের দ্বারা নিজের সমালোচনা তো একেবারেই অসহ্য, ক্ষেত্র বিশেষে মারমুখী। তাই দুরুদুরু বুকে, ভয়ে ভয়ে নিজেদের জাতিগত বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনার সাহস দেখাচ্ছি।
বলছিলাম বিশ্বাসের সংকট বিষয়ে। আমাদের বিশ্বাসের স্তর কতটা পুরু তা বুঝতে একটা তুলনামূলক উদাহরণ দেয়া যাক :
অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, এদেশের সাহিত্যাঙ্গনে অতি পরিচিত একটি নাম। প্রগতিশীল লেখক হিসেবে নিজস্ব ভাবধারায় পৃথক একটা জগৎ তৈরি করেছিলেন তিনি। তিনি যা কিছু বুঝতেন, যা কিছু চিন্তা করতেন, অকপটে তা লিখে ফেলতেন। তার এসব লেখা কার পক্ষে গেলো আর কার বিপক্ষে, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করতেন না। এতে করে ডানপন্থী, বামপন্থী, উদারপন্থি, মধ্যপন্থি, উগ্রবাদী, মৌলবাদী - ইত্যাদি বহুবিধ বাদী আর পন্থিদের অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। তবে তিনি সম্ভবত সবচাইতে বেশি চটিয়েছিলেন মৌলবাদীদের। তারই ফলে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলা থেকে রাতে বাসায় ফেরার পথে একদল ধর্মীয় জঙ্গির নৃশংস আক্রমণের শিকার হন। তবে সে যাত্রায় তিনি দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসা নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যান। একই বছর আগস্টে তিনি জার্মানির কবি হেনরিক হাইনে'র উপর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে জার্মানির মিউনিখে যান। সেখানে অবস্থান কালে ১২ আগস্ট রাতে এক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে নিজ ফ্ল্যাটে ফেরার পর সে রাতেই রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়। জার্মান সরকারের পক্ষ হতে ডাক্তারি রিপোর্টের বরাতে জানানো হলো - হৃদযন্ত্রের কর্মটি বন্ধ হয়ে যাওয়াই তার মৃত্যুর কারণ।
কিন্তু আমাদের সন্দিগ্ধ মন স্বভাবতই সে রিপোর্টের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। বিভূঁইয়ে তাঁর এমন হঠাৎ মৃত্যুতে আমাদের নানা জনের নানা মনে, স্বভাবসুলভ নানা রকমের সন্দেহ দানা বাঁধে। একদলের সন্দেহ, ধর্মীয় জঙ্গিরা তাঁকে খাবারে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলেছে ; অন্য একদল সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আবার অন্য একটি ক্ষুদ্র দল দুগুরবুগুর বিশ্বাসের উপর ভর করে খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে জার্মান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টের উপর আস্থা রাখতে পেরেছে। রিপোর্ট নিয়ে নানা জনের নানামুখি সন্দেহ দূর করার জন্যে, জার্মান সরকারের পক্ষে সে দেশের রাষ্টদূত আমাদের হগগোল সাংবাদিক ভাইদের ডেকে পাঠান। উপস্থিত সাংবাদিকগণ রাষ্ট্রদূতের নিকট সমস্বরে জানতে চান, তিনি এই স্বাস্থ্য রিপোর্টে বিশ্বাস রাখেন কি না। রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের এমন স্পর্শকাতর প্রশ্নের সাদামাটা কথায় অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন - রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাটির উপর আমাদের 'আস্থা' আছে।
-ব্যাস, উত্তেজনার সারা শরীর জুড়ে পানি ঢেলে দিয়ে এক্কেবারে ঠান্ডা করে দিলেন।
প্রশ্ন উঠতে পারে, - এটা এমন কী আহামরি বয়ান হলো। আমরা তো কতো বড় বড় ঘটনা এককথায় ভ্যানিশ করে ফেলি, আবার কথার ফুলঝুরিতে তিলকে নিমিষেই তাল বানিয়ে ফেলি - কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি নিজস্ব গন্ডিতে। এই বেটা রাষ্ট্রদূত যা বলেছে, তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে! সে কি মিথ্যা বলতে পারে না?
- হুম, তাই তো, বিশ্বাসে অবিশ্বাস করার প্রশ্নে আমিও আপনাদের দলে। আমিও কোনো বিষয়ে হাজারবার সন্দেহ পোষণ না করে ধুরুম করে কিছুই বিশ্বাস করি না। আর যাইহোক আপনি, আমি - আমরা তো সেই জন্মের পর হতেই বিশ্বাসের এমন সংকটের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছি।
কিন্তু এমন তো হওয়া উচিৎ না। একজন মানুষ একটি বিষয়ে কথা বলছে, স্বাভাবিকভাবে তার সে কথা বিশ্বাস করাই উচিৎ। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। সবাই যে করে না, তা কিন্তু নয়। আমাদের মাঝেও অনেকেই আছেন, যিনি বিশ্বাস করেন যে, - মানুষকে বিশ্বাস করা উচিৎ। বলা বাহুল্য, তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাসের প্রতিদান পান অবিশ্বাস দিয়ে। বিশ্বাস করতে যেয়ে তিনি পদে পদে ঠকেন। এমন মানুষকে আমাদের সমাজে সহজসরল, আলাভোলা বা বোকা মানুষের তকমা লাগিয়ে দেয়া হয়।
আবারো প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশ্বাসের এহেন সংকট অবস্থা কি শুধুই আমাদের দেশে? পৃথিবীর অন্য কোথাও কি এমনটি নেই?
-আছে, পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি আছে। পার্থক্য হলো, আমাদের দেশে সেটি মহামারী রূপে বিদ্যমান।
কিন্তু, এর কারণ কী?
-কারণ অবশ্যই আছে এবং এটা খুঁজতে আমাদেরকে খুব বেশি দূরে যেতে হবে বলে আমার মনে হয় না।
পরিবারই হচ্ছে সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। পরিবারের মানুষ দিয়েই তৈরি হয় সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি। কাজেই একটা পরিবারের মানূষজনের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে একটা জাতির উপর। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোর দিকে তাকালে আমরা কোন চিত্র দেখতে পাই?
আমরা দেখতে পাই , পরিবারের সদস্যরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না - বাবা-মা সন্তানকে , সন্তান বাবা-মাকে, স্বামী স্ত্রীকে আবার স্ত্রী স্বামীকে ইত্যাদি, ইত্যাদি।
বিশ্বাসটা কেন নেই?
-কারণ বিশ্বাস স্থাপন করার মতো কোনো আদর্শ কেউ কারো সামনে স্থাপন করতে পারেনি। দেখা যায়, খুব সামান্য স্বার্থের কারণে বাবা-মা সন্তানের সামনে, সন্তান বাবা-মা'র সামনে কিংবা স্ত্রী স্বামীর সামনে আবার স্বামী স্ত্রীর সামনে দেদারসে মিথ্যা বলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মিথ্যাচারের এহেন গুণধর কর্মটি তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োগ করে এর অবিরাম ধারা অব্যাহত রাখছে। আমি বলছি না যে, দেশের সব পরিবারই হেনরূপ গুণে গুণান্বিত - ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমের এ সংখ্যাটি কতো হতে পারে? - হাতে গোনেই তা বলে দেয়া যায়। দুঃখজনক বিষয় হলো যে, পরিবারের সদস্যদের মাঝে এ চর্চাটি শুধুমাত্র পরিবারের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এটি ছড়িয়ে পড়েছে পরিবার থেকে পরিবারে, সমাজ থেকে সমাজে, সবশেষে জাতীয় পর্যায়ে এবং তা মহামারী আকারে। মিথ্যাচারের এ রূপটি পরিবার থেকে উৎসারিত হয়ে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে, আকারে ও কলেবরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমাজ থেকে জাতীয় পর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে চর্চিত হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, কোনো একটি পরিবার থেকে উঠে আসা সবচেয়ে চৌকস কিন্তু ধূর্ত একজন বড় পরিসরে ভাই বা বড়ভাই উপাধি পেয়ে সমাজপতির আসনে বসে গেছে। এমন বড় ভাই কেবল একজন নয়, হাজারো বড় ভাই আমাদের চারপাশে আমরা দেখতে পাই।
এক পাড়ায় বা মহল্লায় একজন বড় ভাই থাকলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এক বনে যেমন দুই সিংহ একসাথে থাকতে পারে না, তেমনি একই এলাকায় দুইজন বড় ভাই থাকলেই আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ক্যাচাল লাগে - শুরু হয় মারামারি, এমনকি খুনাখুনি। খুনের ঘটনা ঘটে গেলে দুই পক্ষ থেকেই পক্ষে বিপক্ষে হাজারো সাক্ষী জোটে যায় কিন্তু নিরপেক্ষ সাক্ষী একজনও পাওয়া যায় না। যদি খুন হওয়া মানুষটি হয় একজন নিরীহ ব্যাক্তি, আর খুনি ব্যক্তিটি যদি হয় এলাকার তথাকথিত বড় ভাই নিজে, তাহলে তো বেচারা জানহারা মরহুমের পক্ষে কোনো সাক্ষীই খুঁজে পাওয়া যায় না। কে দেবে সাক্ষী, কার ঘাড়ে আছে দুটি মাথা যে, একটি ছিনতাই হয়ে গেলে অন্যটি নিয়ে টিকে থাকা যাবে! তাই দেখা যায়, চাক্ষুষ সাক্ষী জানের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তবে হ্যাঁ, সেই বড়সড় বড় ভাইটির পক্ষে সাফাই গাওয়ার লক্ষে তার সাগরেদরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যায়। শেষে প্রমানিত হয়, খুনি - কথিত সমাজ দরদি বড়ভাই, ঘটনা ঘটার সময় এলাকাতেই ছিলেন না। তিনি তখন ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে কোথাও বিপদগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণে ব্যস্ত ছিলেন। সাধারণ জনগণের মাঝে এ বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সাগরেদরা এমনভাবে প্রচার শুরু করে যে, বেচারা গোয়েবলস অন্তরিক্ষ থেকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এই প্রবোধে যে, মর্ত্যে রেখে আসা তার তত্বটি পৃথিবীর আর কোথাও না হোক অন্তত এ বাঙ্গাল সমাজে ঠিকঠাকমতো কাজ করছে।
যাইহোক, গোয়েবলসের গুরুযোগ্য আমাদের এসব বড় ভাইদের চেলাদের অব্যাহত প্রচারে আমরা আমজনতা বিভ্রান্ত হয়ে বিশ্বাসের সংকটে পড়ি। গোয়েবলসের তত্ত্বটিকে সম্মান জানিয়ে আমরা একপর্যায়ে বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, বেচারা নিতান্ত ভদ্রমানুষ - বড় ভাই। তিনি বোধ হয় এমন জঘন্য কাজটি করেননি।
বিষয়টি যদি কেবলই বড়ভাই আর বড়ভাইয়ের সাগরেদ ছোটভাইদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেও হয়তো কিছুটা স্বস্তির জায়গা থাকতো। কিন্তু গোয়েবলসীয় এহেন তত্বটি যখন সকল গণ্ডি পেরিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথা রাজনৈতিক অঙ্গনে ঢোকে যায় তখন স্বস্তির জায়গাটিতে বোধ হয় অবশিষ্ট বলে কিছু থাকে না।
বাস্তবতা হচ্ছে, এদেশে আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। কাউকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে আমরা খুবই সাবধানে থাকি, কারণ বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়।
বর্তমান সময়ে মিথ্যার বহুমাত্রিক বিস্তার, বহুমাত্রিক প্রয়োগ কৌশল, বহুমাত্রিক সমঝদারি ইত্যাকার কারণে তৈরি হয়েছে বিশ্বাসের হেন সংকট। আমরা বুঝতে পারি না - কোনটা বিশ্বাস করবো। আমরা এখন বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে সত্যকে মিথ্যার সাথে বা মিথ্যাকে সত্যের সাথে গুলিয়ে ফেলি - সত্যমিথ্যার গোলকধাঁধায় পড়ে প্রায়ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, আবার নিরেট সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে দশবার ভাবি। এদিকে আমাদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে নিমগ্ন থাকা অবস্থাতেই সত্যের উপর মিথ্যা জেঁকে বসে। আর এভাবেই সর্বত্র আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে সত্যের পরাজয়ে মিথ্যার বিজয়োল্লাস।
তাহলে সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী?
উত্তর হলো - এর জন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্র নেই, পদ্ধতি নেই । তবে আমি মনে করি এ জন্যে আমাদেরকে যেতে হবে পরিবারের কাছেই। সদা, সর্বাবস্থায় আমাদেরকে পরিবার থেকেই সত্যপাঠে অভ্যস্ত হতে হবে। দেশের সবগুলি পরিবার যখন হয়ে উঠবে সত্য পাঠের পাঠশালা, তখন এর ধারাবাহিকতায় একদিন সমাজে, রাষ্ট্রে সত্যকথনে অভ্যস্ত ও সাহসী লোকের দেখা মিলবে। আর তখনই মানুষ মানুষকে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করতে পারবে - জাতি মুক্তি পাবে বিশ্বাসের সংকট থেকে।
কিন্তু সেটা কবে!
লেখক : সোনালী ব্যাংকের ডিজিএম



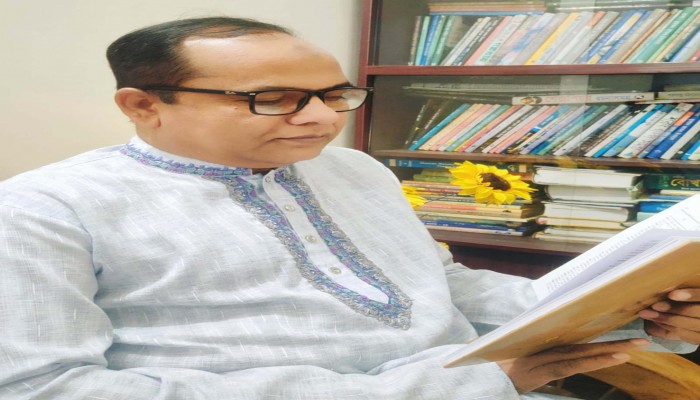 আবদুল মতিন
আবদুল মতিন