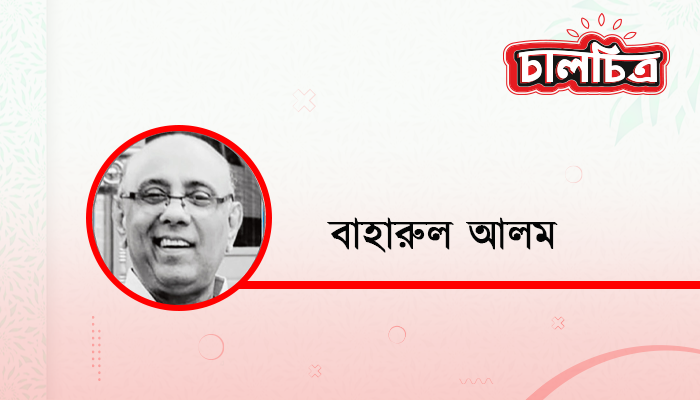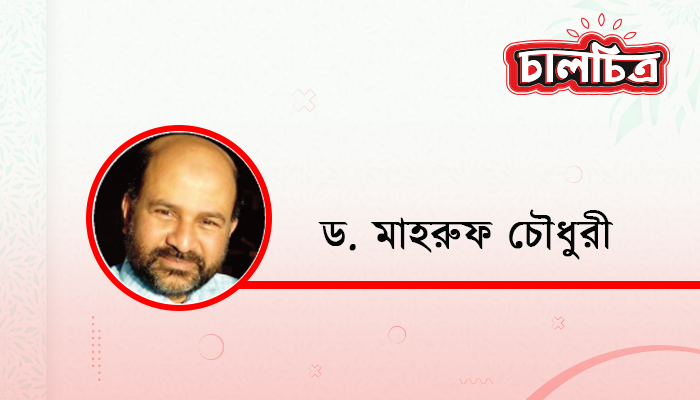বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, বিকাশের সূত্রাবলি সম্পর্কে ধারণা এবং ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের সামর্থ্য বা পারঙ্গমতা আমার আদৌ নেই বললেই চলে। এতৎসত্ত্বেও নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিজস্ব বানান রীতি, বাক্য গঠন-প্রক্রিয়া, যতি বিন্যাসের ধরন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে সম্যক উপলব্ধি করা যায় যে বাংলা ভাষার ক্রম অবক্ষয় আশঙ্কাজনক স্তরে উপনীত হয়েছে। কারণ প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোর বানান রীতি স্বতন্ত্র, বাক্য গঠন-প্রক্রিয়া একান্তই নিজস্ব এবং যতি বিন্যাসের ধরন-ধারণ বস্তুত বাংলা অভিধান কিংবা ব্যাকরণের নিয়মরীতির তোয়াক্কা করে না। যাহোক, জানামতো, একমাত্র বাংলা ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো ভাষার জন্য দামাল ছেলেদের হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জনের কাহিনি পাঠ করার কিংবা শোনার সুযোগ স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে হয়নি। আবার নব্বইয়ের দশকে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ঠিকানা পত্রিকার সঙ্গে প্রায় ২৫ বছরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ততার সুযোগেও অন্য কোনো ভাষার জন্য নিজস্ব ভাষাভাষীর আত্মাহুতির খবর পড়ার বা জানার সুযোগ আমার হয়নি। আমার বিশ্বাস, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করলেও ভাষাশহীদদের রক্তঝরা সোপান বেয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে এবং বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে বলা যায়, বায়ান্নর ভাষাশহীদের আত্মাহুতির দুর্মর অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে বুকে ধারণ করেই একাত্তরে ৩০ লাখ মুক্তিযোদ্ধা এক সাগর রক্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর দুই লক্ষাধিক সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং সর্ববয়সী ও সর্বস্তরের বাঙালি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ত্যাগের সোনালি ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ মুক্তিকামী বিশ্ববাসীর জন্য সন্দেহাতীতভাবে অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। অবশ্য সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই সৃষ্টি ও প্রলয়, উত্থান ও পতন, পরার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, সার্বজনীন কল্যাণ ও স্বার্থপরতা, মনুষ্যত্ববোধ ও পাশবিকতা, র্যাশন্যালিটি ও অ্যানিমেলিটি হাত ধরাধরি করে চলে আসছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক সাগর তাজা রক্তের বিনিময়ে একাত্তরে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও সেই রাহুগ্রাসের মোহবন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি। উল্টো ব্যক্তিস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিভক্তি ও মসনদের দুর্মর বাসনা সদ্য স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে শকুনের পদচারণা ঘটিয়েছিল। ১৯৭১ সালের শেষ পর্যায় থেকে ২০২৪ সালের রক্তাক্ত জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনির প্রতি সামান্য আলোকপাত করলেই তা সন্দেহাতীতভাবে গিবত বা পরচর্চার মতো জঘন্য পাপাচারের পর্যায়ে পড়বে। অগত্যা ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা।
কথায় বলে, অর্থ-বিত্ত-প্রাচুর্য-শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি মানুষের মন-মানসিকতা, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-জীবনাচরণ এবং চলন-বলনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। এরই দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় বিগত কয়েক দশকে স্বাধীন বাংলাদশে একশ্রেণির কোটিপতি, শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত ও অতি পণ্ডিতদের চলন-বলন ও জীবনাচরণে। বিশেষত, রাজনীতির আশীর্বাদে কিংবা অন্য কোনো অনৈতিক উপায়ে হতদরিদ্র কিংবা নুন আনতে পান্তা ফুরায় শ্রেণির লোকজন বিত্তশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচার-আচরণে রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নেমে আসে। তারা চিরায়ত ও সনাতনী বাংলায় কথাবার্তা বলার পরিবর্তে ভুল ইংরেজি আওড়ে আভিজাত্য জাহিরের বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর উঠতি কোটিপতি, শিক্ষার লেবাসধারী উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিতম্মন্যরা বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চাকে আভিজাত্যের পরিপন্থী জ্ঞানে পারতপক্ষে বাংলার ব্যবহার এড়িয়ে যান। ইংরেজিসহ ভিন্ন ভাষার প্রতি দুর্দমনীয় আসক্তির বশে তারা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নিজে এবং পোষ্যদের ইংরেজি অনুশীলন ও গলাধঃকরণে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের অজপাড়া গাঁ ছাড়া মাতৃভাষার অনুশীলন ও চর্চা সম্প্রতি অতি শিক্ষিত-অভিজাত এবং অঢেল বিত্তশালীদের সুরম্য হর্মের চৌকাঠ মাড়াতে সক্ষম হচ্ছে না। আবার ভাষার সঙ্গে রুটিরুজির প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিধায় মধ্যম শ্রেণির বাঙালিদের অনেকেও সন্তানদের বাংলা শিক্ষার পেছনে আর্থিক বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। তাই শহীদদের রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশে বিগত ৫৩ বছরে বাংলা ভাষার কাক্সিক্ষত সমৃদ্ধি ও বিশ্বায়ন আশানুরূপ হয়নি বললে সত্যের অপলাপ হবে না। বিশেষত, বাংলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ একশ্রেণির উন্নাসিক বাঙালির অবজ্ঞা-অবহেলা-তুচ্ছতাচ্ছিল্য বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথকে অবরুদ্ধ করছে। পণ্ডিতম্মন্যদের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে বাংলা ভাষা সনাতনী যুগের সর্বজনীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে বর্তমানে বহুলাংশে চাষা-ভূষা ও নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীর ভাষায় পরিণত হতে চলেছে।
বর্তমান বাংলাদেশে একদিকে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হু হু করছে বাড়ছে, অন্যদিকে কোটিপতি ও উঠতি কোটিপতিদের চোখ ঝলসানো আকাশ-আড়াল-করা হর্মরাজিতে ঢাকাসহ গোটা দেশ ভরে যাচ্ছে। আর বিলাসবহুল প্রাসাদে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ২% বাঙালির দুগ্ধপোষ্য শিশুদের বাকস্ফূরণ হয় মম-মমি-ড্যাড-ড্যাডি-পাপা-আঙ্কেল-কাজিন ইত্যাদি বিদেশি শব্দ দিয়ে। এসব কোমলমতি শিশুর আনুষ্ঠানিক বর্ণপরিচিতি ঘটে অ্যা ইজ ফর অ্যাপেল, বি ইজ ফর বয়, সি ইজ ফর ক্যাট ইত্যাদি লেটার দিয়ে। সনাতনী আমলের অ, আ, ই, ঈ বর্ণমালা এবং মা-বাবা-চাচা-চাচি ইত্যাদি আধুনিক আশরাফ বাঙালি শিশু-কিশোরদের স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের ঘোর বিরোধী। আভিজাত্যের বাতিকগ্রস্ত এ শ্রেণির বাঙালিদের স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়েরা বাংলার পরিবর্তে জগাখিচুড়ি মার্কা ইংরেজি বকাঝকা করে আভিজাত্য জাহির ও আত্মতুষ্টি লাভ করে। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা হয়, বাঙালি সংকর জাতি এবং বাংলা সংকর ভাষা। আরব-অনারব-আঞ্চলিক-সংস্কৃত-দেশি-বিদেশি-বার্মিজ-পর্তুগিজ-ইংরেজি-হিন্দি-উর্দু ইত্যাদি ভাষার শব্দাবলি বাংলা ভাষার মেল্টিং পটে গলে-মথে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে সংস্কৃত পণ্ডিত, উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাংলার প্রতি কখনো শোভনীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। নেহাত চাষা-ভূষা-অশিক্ষিত-মূর্খ এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাষাজ্ঞানে বাংলার ব্যবহার তারা পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতেন। তাদের দাম্ভিকতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে মধ্যযুগীয় কবি আবদুল হাকিম লিখেছেন, যে জন বঙ্গেতে জন্মি নিন্দে বঙ্গবাণী/ সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
বলার অপেক্ষা রাখে না, পুঁথিসাহিত্য, টক্কা, লোককাহিনি ইত্যাদি হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হালিম, মধ্যযুগীয় মহাকবি আলাওল প্রমুখের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল। নানা বৈরিতার সাগর পাড়ি দিয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র, অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাম্যমাণ বিশ্বকোষ খ্যাত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মীর মশাররফ হোসেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লিকবি জসীম উদ্্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বিশ ও একুশ শতকে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে। এ পর্যায়ে অসংখ্য প্রাতঃস্মরণীয় কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-ভাষাবিদ-পণ্ডিত-নাট্যকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা-ত্যাগ ও সাধনায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিশ্ব পরিমণ্ডলেও মর্যাদার আসন দখল করেছে। তবে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ম-রীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ শতকের শেষ ভাগ এবং একুশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই ভিন্ন ভাষার প্রতি একশ্রেণির বাঙালির দুর্দমনীয় আসক্তি ও মোহ বাংলা ভাষাকে সমূহ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
শিক্ষানুরাগীমাত্রই অবহিত, মান্ধাতার আমলে গুরুগৃহই ছিল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের আলয় বা গৃহ। বটতলা এবং খোলা আকাশ ছিল উন্মুক্ত বিদ্যালয়। গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী অভিন্ন মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করত। মোগল শাসনামলে এবং ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালীদের কাছারি, মঠ, টোল, মক্তব, স্কুল-মাদ্রাসায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু হয়। আর ১৯৪৭ সালের পর পাকা দালানে ও পাকা ইটের প্রাচীরবেষ্টিত টিনের ছাউনিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে। এ পর্যায়ে শারীরিক নির্যাতন বা স্পেয়ার দ্য রড, স্পয়েল দ্য চাইল্ডÑশিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিদায় নেয়। পাশ্চাত্যের আদলে পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিসহ বিচিত্র রং ও ঢঙের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষাপোকরণের আমদানি ঘটে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে। এ ধাপেই বিত্তশালী ও উচ্চশিক্ষিত আমলা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদেরা স্বদেশি ভাষার সঙ্গে বিদেশি ভাষা, বিশেষত ইংরেজি ভাষা অনুশীলনের জোর তাগিদ বোধ করেন। ফলে পাঠ অনুশীলন ও আত্মীকরণের স্থলে গলাধঃকরণের তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় একধরনের শিক্ষার্থীর মাঝে। শিশুর বয়স-সামর্থ্য-আগ্রহ ও প্রবণতা শিক্ষাদান এবং অপরিহার্য শর্ত হলেও এসব শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় নেয়। সাহায্যকারী উপকরণ ও বই-পুস্তকের ভারে কোমল-কচি শিশু-কিশোরদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। তোতা-ময়নার মতো পাঠ মুখস্থ বা গলাধঃকরণ এবং পরীক্ষাকক্ষে মুখস্থবিদ্যা করে কাক্সিক্ষত সার্টিফিকেট লাভের মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট ব্যবসার রমরমা বাণিজ্য শহর-নগর-গ্রামগঞ্জ তথা সারা দেশের আনাচ-কানাচে, অলি-গলি ও পল্লিতে ছড়িয়ে পড়ে। আবার উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণির অভিভাবকেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিদেশের আদলে কিন্ডারগার্টেন, বিশেষ ধরনের নিকেতনে শিশুসন্তানকে নামমাত্র বাংলা বর্ণমালা শেখানোর পাশাপাশি ইংরেজি গলাধঃকরণের তোড়জোড় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক চর্চা ও বিকাশের চিরায়ত ধারা বহুলাংশে মুখ থুবড়ে পড়ে। সংগত কারণেই উল্লেখ করতে হচ্ছে, ভাষার উৎপত্তি-বিবর্তন-বিকাশের সূত্র জানা এবং শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের উদ্দেশ্যেই একদা ব্যাকরণের সূচনা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে হাল আমলে ব্যাকরণের পাঠদান স্কুল-কলেজে অপাঙ্্ক্তেয় হয়ে যায়।
পঞ্চাশের দশকে ভাবসম্প্রসারণ, কারক-বিভক্তি, বাক্য সংকোচন, প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ, চিঠিপত্র ও রচনা লেখা ইত্যাদি ছিল ভাষা শেখা ও ভাব বিকাশের প্রধানতম অবলম্বন। বর্তমান পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচিতে এসব অনাবশ্যক। আর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তরের স্থলে বহুনির্বাচনীমূলক প্রশ্নপত্রের প্রবর্তন শিক্ষার্থীর ভাষা আয়ত্তকরণ, যুক্তিযুক্ত চিন্তনক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানের এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বায়ান্নর ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগ ইংরেজি অনুশীলনের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেবে বলে আমাদের আশঙ্কা। অনেকে জোর গলায় দাবি করেন, একুশের বইমেলা জাতীয় সরকারি উদ্যোগগুলো বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। আবার অনেকের বিশ্বাস, জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো সাড়ম্বরে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্্যাপন করায় বাংলা ভাষা বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। বাস্তবতার মানদণ্ডে বিষয়টি পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। কারণ মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, ভালোবাসা দিবস, আন্তর্জাতিক বুড়ো দিবস ইত্যাদি সাড়ম্বরে পালনের ছত্রচ্ছায়ায় আমরা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ববোধকে সজ্ঞানে উপেক্ষা করছি। বিশেষ বিশেষ দিবসে ভুরিভোজনের আয়োজন, ফুলের তোড়া, মূল্যবান পোশাকসামগ্রী উপহার ইত্যাদির মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততির নৈতিক দায়িত্ব পালন করা হয় না। শৈশব ও কৈশোরের অসহায় সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতা-মাতার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা, আত্মত্যাগের স্থলে জীবনসায়াহ্নে বিশেষ দিবসের উপহারসামগ্রী মূলত পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্বের প্রতি নির্মম প্রহসনের নামান্তর। অনুরূপভাবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, শিশু-কিশোরদের বাংলা অনুশীলনে বাধ্য না করে বিশেষ দিবসে ভাষার স্তুতিবাদ কিংবা ভাষাশহীদদের প্রতি বন্দনা নির্ঘাত ভণ্ডামি। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার নামে প্রচলিত ভণ্ডামির অবসান দেশবাসীর কাম্য।
ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ব্রিটিশশাসিত ভারত উপমহাদেশে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী লর্ড ম্যাকেলে ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিওরির (উপর থেকে নিচ দিকে চুইয়ে পড়া) প্রণয়ন করেছিলেন। ম্যাকেলের ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশনের থিওরির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে বাদামি রঙের বা ব্রাউন কলারের ভারতীয় শিক্ষিত তৈরি করা। ম্যাকেলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আশীর্বাদধন্য ভারতীয়রা শুধু গাত্রবর্ণ বা গায়ের রঙে বাঙালি থাকলেও মন-মানসিকতা এবং জীবনাচরণে পুরোপুরি স্বদেশ ও স্বভাষা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এ শ্রেণির শিক্ষিতরা ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বা ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছিল। তারা নিজস্ব ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি- ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্বাসনে দিয়ে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য যুগের পর যুগ প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে স্বল্পসংখ্যক ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান, যেমন মাস্টার দা সূর্য সেন, প্রীতিলতা সেন, শহীদ তিতুমীর, ফকির মজনু লাল, শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুবাস বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ দেশপ্রেমিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে ১৯৪৫ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানের বড় লাট কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিমাতাসুলভ আচরণই শেষ পর্যন্ত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কালোত্তীর্ণ অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। আর বায়ান্নর রক্তস্নাত পথের সোপান মাড়িয়ে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন ও সর্বস্তরের বাঙালির অপরিসীম ত্যাগের ফসল হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কিন্তু গঠনমূলক পরামর্শ ও সুচিন্তিত পদক্ষেপের অভাবে বিগত ৫৩ বছরেও বাংলা ভাষার কাক্সিক্ষত সমৃদ্ধি চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। এমনকি উঠতি কোটিপতি ও উন্নাসিক উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদের নির্মম অবহেলার শিকার হয়ে বাংলা ভাষা রুগ্্ণ-শয্যাশায়ী এবং মুমূর্ষু দশায় উপনীত হওয়ার উপক্রম। তাই বাংলা ভাষার সুরক্ষা-সমৃদ্ধি ও বিকাশে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন সময়ের দাবি।
লেখক : সহযোগী সম্পাদক, ঠিকানা, নিউইয়র্ক।


 মুহম্মদ শামসুল হক
মুহম্মদ শামসুল হক