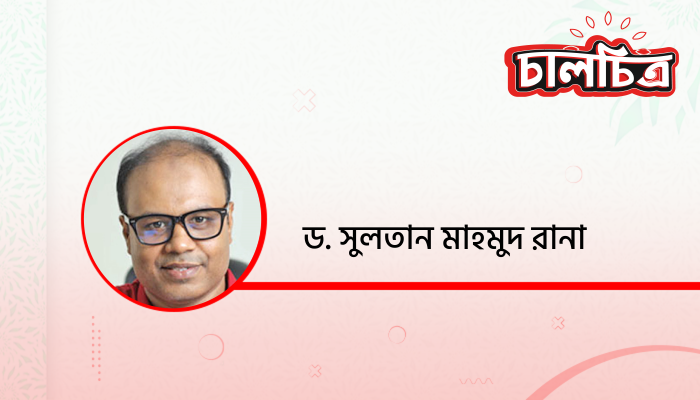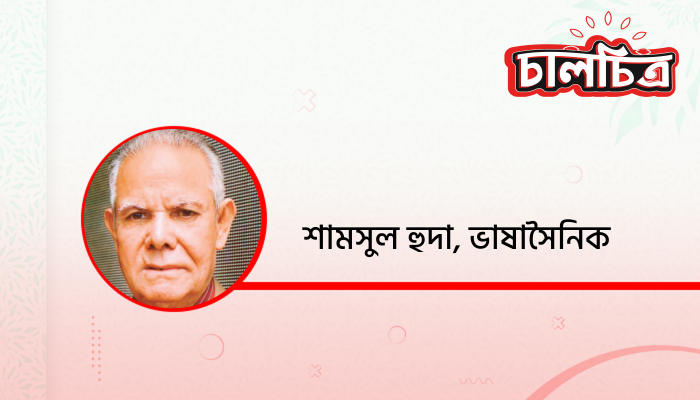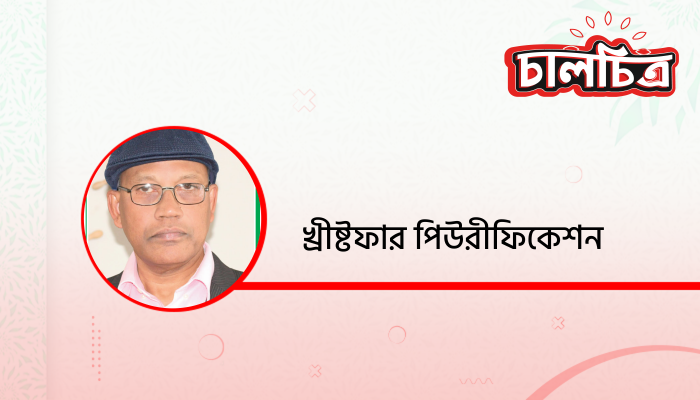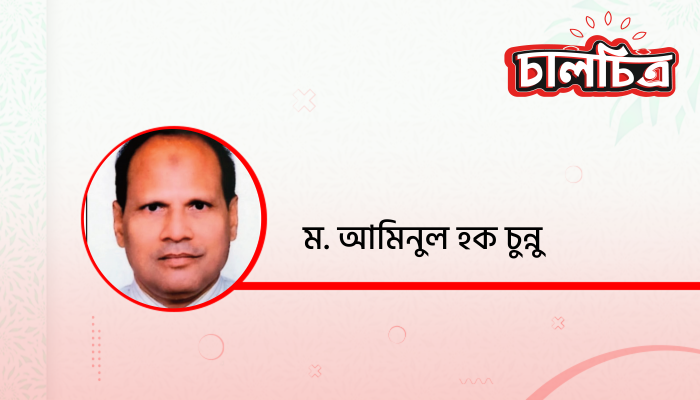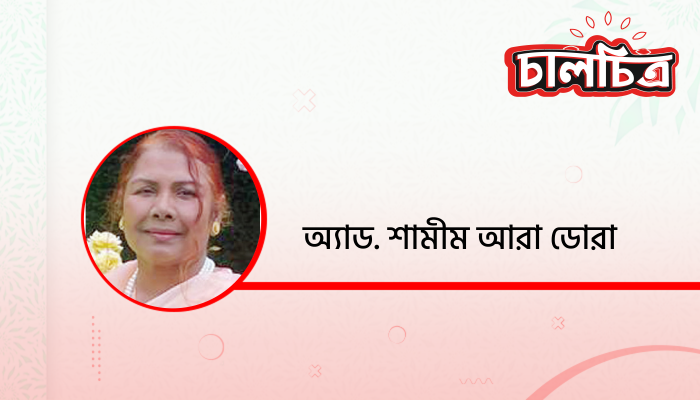সাধারণত উন্নত জীবনযাপন, খাদ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ব্যবসা ইত্যাদির জন্য মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। যারা অন্য দেশে যায় তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালো থাকতে পারছেন। আবার অনেকেই আছেন যারা মোটেও ভালো নেই। ভালো থাকা এবং ভালো না থাকা এই দুই প্রকারের মাঝামাঝিতেও আছেন অনেকেই।
এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে এক বছরের বেশি সময় থাকলে তাকে সাধারণ অর্থে অভিবাসী বলা হয়। বিশেষ করে নিজ দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে বা পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও মানুষ অভিবাসনের পথ বেছে নেয়।
আবার অনেকেই আছেন নিজ দেশে নিজ পরিবারে অনেক প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন একটি দেশে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে কিংবা নিছকই ভালো লাগার জন্য যেতে চান কিংবা যাচ্ছেন। এক কথায় বলা যায়, কেউ স্বেচ্ছায় অভিবাসন গ্রহণ করছেন, আবার কেউবা বাধ্য হয়ে।
অভিবাসন প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। অনেক সময় প্রস্তুতির অভাব, নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা, স্থানীয় ব্যবস্থাপনার জটিলতা, ভাষাগত অসুবিধা, সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি অভিবাসীদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
আবার অনেকেই আছেন নিজ দেশে স্নাতক শেষ করে অন্য দেশে পড়াশোনা করার উদ্দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। অনেক সময় দেশ ভেদে গ্রিন কার্ড কিংবা নাগরিকত্ব লাভ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ উন্নত জীবনযাপন, উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার সন্ধানে ইউরোপ ও আমেরিকায় অভিবাসী হচ্ছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা অভিবাসী জনসংখ্যা এক দশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো বা আদমশুমারি অধিদপ্তরের ২০২৪ সালের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০১০ ও ২০২২ এর মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীদের সংখ্যা ২৯ লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ৪৬ লাখে পৌঁছেছেÑ যা প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি।
বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এই সংখ্যা আরও অনেক বেড়েছে। দেশ ভেদে অভিবাসনের এই হার প্রায় দেড় শতাধিক শতাংশের চেয়েও বেশি। তা ছাড়া অবৈধভাবে অভিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যায় রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্য ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ৬ লাখ ৬ হাজার অভিবাসী নিয়েছে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এই সংখ্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও এটি জানা গেছে যে, আগের বছরের চেয়ে সেটি আরও বেড়েছে।
বলা যেতে পারে সাম্প্রতিক ইতিহাসে রেকর্ড হয়েছে। ২০২২ যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী গেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের বাইরে থেকে। আর এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যাটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে। তারা মূলত চাকরি, পড়াশোনা ও মানবিক বিভিন্ন কারণে দেশটিতে বসবাস করার উদ্দেশে গেছেন।
যুক্তরাজ্যে যাওয়া অভিবাসীদের মধ্যে রয়েছেন রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেন থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকজনও। এ ছাড়া হংকংয়ের অনেক বাসিন্দাও ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে গেছেন। হংকংয়ে নাগরিক অধিকারের ওপর চীনের দমন-পীড়ন শুরুর পর সেখানকার বাসিন্দাদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে শিথিলতার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অভিবাসনের ধরন কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা জরিপের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়। যদিও লাতিন আমেরিকা একসময় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের প্রধান উৎস ছিল এবং এখনো তারা বিদেশে-জন্মগ্রহণকারী জনসংখ্যার অর্ধেক।
তবে এখন আরও অভিবাসী এশিয়া, আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে যাচ্ছে। সেন্সাস ব্যুরো দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে ১০টি দেশকে হিসেবে ধরেছে। দেশগুলো হচ্ছেÑ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, ইরান, কাজাখস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও উজবেকিস্তান। সংস্থাটির বিদেশে জন্মানো জনসংখ্যা আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভে নামে পরিচিত একটি বার্ষিক জরিপের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে। তবে এ ধরনের অনুমানে ত্রুটি থাকতে পারে। কারণ অনুমান মানেই ত্রুটি থাকবেÑ সেটি অনেকটা স্বাভাবিক।
তবে এমনও অনেক দেশ আছে, যেখানে অভিবাসীরা টিকে থাকার লড়াইয়ে রয়েছেন। উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডাতে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ পাড়ি জমান ভালো জীবনযাপনের প্রত্যাশায়। সেই দেশে জীবনযাপনের খরচ অনেক। সেখানে বসবাসের উপযোগী বাড়ি কম থাকায় সেটি অনেকটা ব্যয়বহুল। অভিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক বাড়ার মধ্যে নতুন আগত যারা এই দেশকে নিজের বাসভূমি বানাতে চেয়েছেন, তাদের অনেককেই ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে।
কানাডার জনসংখ্যা কম ছিল। বাড়ছিল বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। পরিস্থিতি সামলাতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার অভিবাসনকে বেছে নেয় প্রধানতম হাতিয়ার হিসেবে। এ কৌশল তাদের কাজে দিয়েছে। দেশটির অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সরকারের পরিসংখ্যান বিষয়ক দপ্তর স্ট্যাটিসটিকস কানাডা জানিয়েছে, ছয় দশকের মধ্যে কানাডার জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে। তবে ২০২৩ সালের প্রথম ৬ মাসে ৪২ হাজার মানুষ কানাডা ত্যাগ করেছেন। ২০২২ সালে কানাডা ছাড়েন ৯৩ হাজার ৮১৮ জন, তার আগের বছর ৮৫ হাজার ৯২৭ জন দেশটি ছেড়েছিলেন বলে সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। এভাবে অনেকেই সংকটে পড়েছেন।
অভিবাসীদের কানাডা ত্যাগের সংখ্যা দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ২০১৯ সালে। ওই বছরে দুই লাখ ৬৩ হাজার মানুষ কানাডায় যান স্থায়ীভাবে থাকতে। সুতরাং কানাডা ত্যাগ করা মানুষের সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম। ২০২৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ মানুষ কানাডায় নতুন বসতি স্থাপন করতে পারবেন।
এ কথা সত্য যে অভিবাসীদের অনেকের জীবন খুব আকর্ষণীয়। বিশেষ করে যারা পছন্দমতো দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন। পছন্দমতো দেশ, পেশা এবং বসবাস নিয়ে তাদের জীবন অনেকটা আকর্ষণীয়। কিন্তু অপরদিকে যারা নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, কিংবা সন্তানদের ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করানোর জন্য নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস করছেন, তাদের অনেকের জীবনই দুঃখ-দুর্দশায় ভরা।
অভিবাসন মানুষকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখালেও সংকট ও সমস্যা তাদের তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে থাকে চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতা। এটি অস্বাভাবিক নয়। অভিবাসীরা সুখ ও দুঃখের মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামনে আগায়। উন্নত দেশগুলোয় ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে অভিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হন এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেন।
২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী অভিবাসীরা প্রায় ৮৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স প্রেরণ করেন। উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অনেক অভিবাসী নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি মজবুত করেন। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় অভিবাসনের প্রবণতা ব্যাপক। নতুন দেশে অভিবাসীরা নতুন নতুন সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং মানসিকতার বিকাশ ঘটান।
বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য তরুণ-তরুণীরা অভিবাসী হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার শিক্ষার্থীদের খবর জানি। তারা অনেকেই প্রতি বছর বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। বিদেশে পড়াশোনার জন্য আমার কাছ থেকে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ সুপারিশপত্র (রিকমেন্ডশন লেটার) নিয়ে থাকে। যারা রিকমেন্ডশন লেটার নিতে আসে তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কেন তারা দেশ ছাড়তে চাইছেন। বেশির ভাগই উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় দেশ ছাড়ছেন বলে আমাকে জানায়।
সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর শ্রমবাজারে ২০ থেকে ২২ লাখ তরুণ-তরুণী নতুন করে যুক্ত হচ্ছেন। দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান হয় ১২ থেকে ১৩ লাখের। তাদের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান হয় মজুরিভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক খাতে, অন্যরা ভালো এবং সন্তোষজনক চাকরিতে যান। সেই হিসাবে প্রতি বছর তিন লাখের মতো সন্তোষজনক চাকরি হয়। আর প্রতি বছর ৮ থেকে ৯ লাখ মানুষ প্রবাসে যান। তবে ২০২২ ও ২০২৩ সালে প্রতি বছর ১০ লাখের বেশি নারী-পুরুষ কাজের জন্য প্রবাসে গেছেন।
অনেক অভিবাসী নতুন দেশে বৈষম্য এবং বর্ণবাদী আচরণের সম্মুখীন হন। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচিতি রক্ষার চ্যালেঞ্জ থাকে। ভাষাগত পার্থক্যের কারণে অনেক সময় অভিবাসীরা নতুন দেশে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সমস্যায় পড়েন। প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মসংস্থান না পাওয়া, নিম্ন আয়ের চাকরিতে কাজ করা এবং স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অভিবাসীদের কষ্ট করতে হয়।
বহু অভিবাসী ভিসা, কাজের অনুমতি এবং নাগরিকত্ব পেতে দীর্ঘমেয়াদি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান, যা তাদের মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলে। ভারত, মেক্সিকো, চীন এবং ফিলিপাইন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অভিবাসী প্রেরণকারী দেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও কুয়েতের মতো দেশগুলোয় অভিবাসীরা মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ (৭০-৮০ শতাংশ) দখল করেন।
উন্নত দেশে অভিবাসন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। উন্নত জীবনমান, উচ্চ আয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবার কারণে অভিবাসীরা উন্নত দেশে বসবাসে আকৃষ্ট হন। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা উন্নত দেশে অভিবাসনের আরেকটি প্রধান কারণ। উদাহরণস্বরূপ, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো অভিবাসীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার গড়ার চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।
নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়া অনেক অভিবাসীর জন্য মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা, ভিসা প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এবং কর্মক্ষেত্রে শোষণ তাদের জীবনকে আরও জটিল করে তোলে। তাই উন্নত দেশে অভিবাসনের সুযোগ কাজে লাগাতে হলে এসব সমস্যার কার্যকর সমাধানে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা ন্যায্য এবং জরুরি। অভিবাসন শুধু একক ব্যক্তির জন্য নয়, এটি বিশ্বব্যাপী মানুষের ঐক্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি বড় উদাহরণ। তাই অভিবাসীদের সুখ-দুঃখের গল্প গুরুত্ব দিয়ে শোনা উচিত এবং তাদের সমর্থনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।


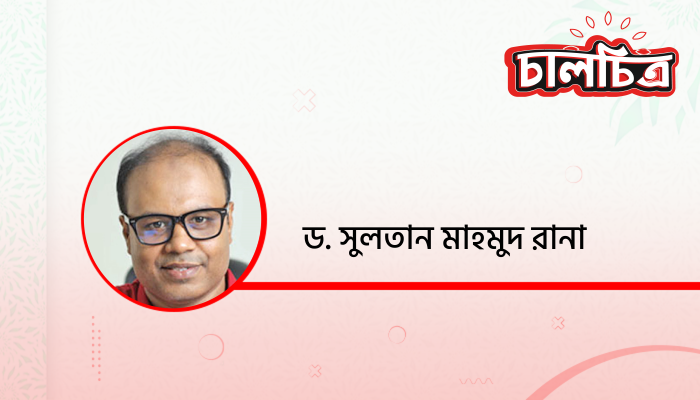 ড. সুলতান মাহমুদ রানা
ড. সুলতান মাহমুদ রানা