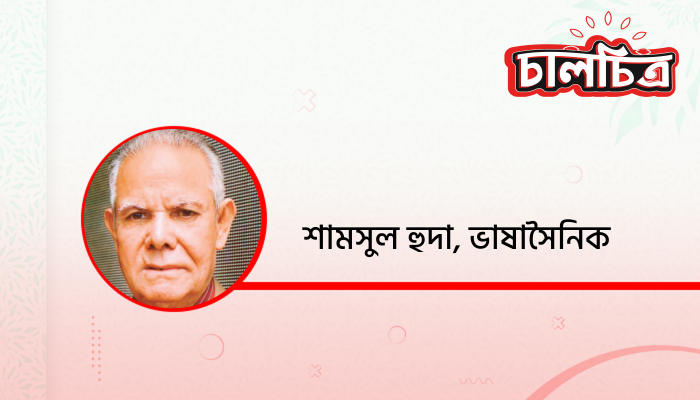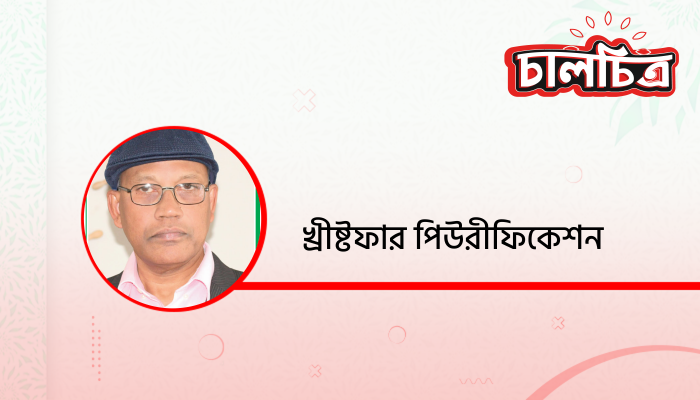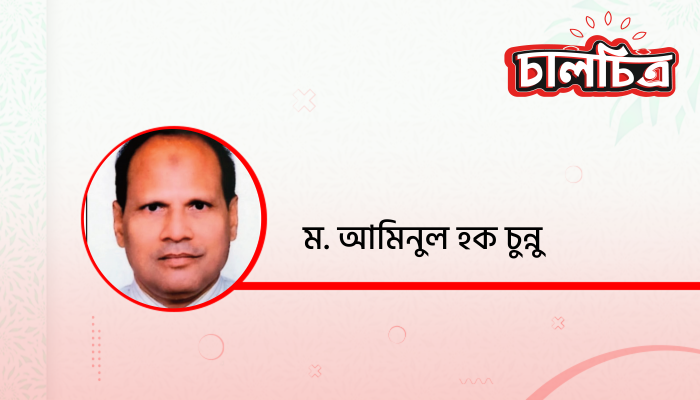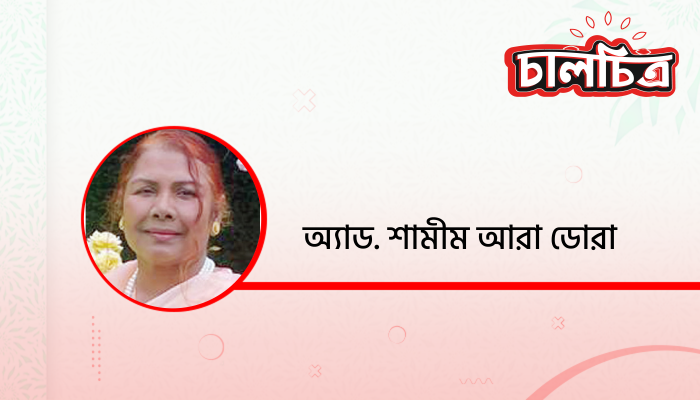সে ছয় যুগ আগের কথা। ছোট্ট শহর আলমডাঙ্গা। সেখানকার ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পড়ার জন্য পাড়ি দিলাম রাজশাহী কলেজে। সালটা ছিল ১৯৫১। কলেজের রঙিন আর ঝলমলে বিরাট বিরাট ইমারতগুলো দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এখানে পড়ব। উৎসাহটা চরমে। তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম ভর্তি হওয়ার ফরমের জন্য। ফরম তো পেলাম। কিন্তু পূরণ করার সময় মহা বিপদ। অভিভাবকের সই লাগবে। তাহলে কি আবার বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। বিরাট দুর্ভাবনা। অফিসের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, অভিভাবকের হয়ে সই করে দাও। ভরসা পেলাম না। আবার কোন ফ্যাসাদের ভেতর জড়িয়ে না পড়ি। সোজা প্রিন্সিপালের ওখানে। অঙ্কের প্রফেসর করিম সাহেব তখন প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন। বড় ভালো মানুষ। খুবই অমায়িক। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছ তো এই কলেজে পড়ার। তাহলে আর কি। তিনার হয়ে সইটা করে দাও।
ভর্তির পর্বটা শেষ হতে না হতেই আরেকটা বিরাট চাপ পড়ল মাথার ওপর। পড়ার বিষয়গুলো কী হবে। দশটি পেপার ছিল আমাদের পাঠ্য।
এর ভেতর আবার এক পেপার ইংরেজি আর এক পেপার বাংলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। এখন পছন্দ করে নিতে হবে চারটি বিষয়। প্রতিটি বিষয়ে দুটো করে পেপার। বহুবার শুনতে হয়েছে কী সব ইললজিক্যাল কথাবার্তা বলিস। তাই একটু চৌকস হওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম লজিকের ওপর। এ ছাড়া অনেকের কাছে শুনেছি, লজিকে নাকি নম্বর ওঠে খুব ভালো। অভিজ্ঞদের কাছ থেকে জানা যে চাকরির বাজারে ইকোনমিকস হলো একটা শক্ত খুঁটি। আর কি, আঁকড়ে ধরলাম সিভিক্স আর ইকোনমিকস। ইস্কুলে থাকতে প্রবল আকর্ষণ ছিল ইসলামের ইতিহাসের ওপর। এরপর যখন দেখলাম, সিলেবাসে রয়েছে তুরস্কের ইতিহাস, যেটার শুধু নামই শুনেছি এত দিন, তখন সিদ্ধান্তটার জন্য আর কোনো কসরত করতে হয়নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিল কবিতা আর শেক্সপিয়রের বেশ কিছু পাতা পড়ে, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে একটা গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। চিন্তা-ভাবনাটা যাতে এখানেই আটকে থাকে, সে জন্য অনেকেই মনে করিয়ে দিতেন যে ইংরেজি সাহিত্যের রসটা মধুর বটে, তবে পরীক্ষার খাতায় মিলবে শুধু তিক্ততা। হয়তো হারাতে হবে ডিভিশনটা। যা হোক, এই একটা বিষয় যেখানে বাস্তবতাটাকে উপেক্ষা করে প্রাধান্য দিয়েছিলাম আবেগকে।
প্রফেসরগণ
আমাদের সময়ে সরকারপক্ষ থেকে জোরালোভাবে সব সময় বলা হতো, এই মুসলিম লীগ সরকার যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে পাকিস্তান বলে আর কিছু থাকবে না। আমরাও অনেকটা বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলাম। প্রফেসর বাগচীর সিভিক্স ক্লাসে যখন রাষ্ট্র, সরকার নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, তখন তিনি বললেন সরকার আসবে যাবে, রাষ্ট্র কিন্তু থেকে যাবে। দেখো না কত দেশে নির্বাচনের পর সরকার তো বদলেছে, আবার সাথে সাথে সেসব রাষ্ট্র তো অটুটই আছে। চোখের ওপর থেকে বিরাট একটা পর্দা সরে গেল। প্রফেসর বাগচী বেশি দিন ছিলেন না। আমরা থাকতেই ভারতে চলে গেলেন। জানি না তিনার এসব খোলামেলা আলোচনা সরকারের কুনজরে পড়েছিল কি না। যা হোক, অভিযোগে ভরা তিনার একটা বিরাট বিবৃতি নাকি কলকাতার নামকরা একটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।
বারবারা, সিলারেন্ট, ডেরিয়ায়, ফেরিয়ো, ডিডাকটিভ লজিকের সিলোজিসমের ভেতরের এসব মালমসলা আজও মন থেকে মুছে যায়নি। যাবেই-বা কী করে। পড়িয়েছেন তো প্রফেসর জব্বার। আসতেন শেরওয়ানি পরে। নামতা পড়ার মতো আমাদের সবাইকে একসাথে করে মুখস্থ করিয়েছেন বারবারা, সিলারেন্ট থেকে শেষ পর্যন্ত। ক্লাসে রীতিমতো আলোড়ন এনেছিলেন ‘ফ্যালাসির’ ভেতর এসে। বললেন, ধরো, আমরা যদি বলি (১) ভগবান সৃষ্টি করেছেন মানুষ, মানুষ সৃষ্টি করেছে পাপ, অতএব ভগবান সৃষ্টি করেছেন পাপ। এখন তোমাদের চিন্তা-ভাবনায় এটার উত্তর কী হওয়া উচিত। পরের বছর ইনডাকটিভ লজিকের ভেতর এসে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে মারাত্মক ভুলটা আমরা সাধারণত করে থাকি, সেটাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন মাথার ওপর কাক ডাকলে অমঙ্গল ঘটবে, এই তো অমুক অমুকের বেলায় এটা ঘটতে দেখা গেছে। ভুলটা হলো যাদের বেলায় ঘটেনি, সেগুলোকে বেমালুম চেপে যাওয়া।
পাঠ্যের বাইরে ফিলোসফির সঙ্গে পরিচয়টা জোরালো করার আকাক্সক্ষাটা ছিল প্রবল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, পড়ান প্রফেসর অবনী মোহন দত্ত। শুধু তা-ই নয়, তিনি যখন ক্লাস নেন, তখন আমার বিরতি। একদিন অনেক সাহস সঞ্চয় করে তিনার ক্লাসরুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাকে দেখে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার। আমি তিনার ক্লাসে বসার অনুমতি চাইলে আসতে বললেন। সেদিনের আলোচনাটা ছিল ডেকারতের ওপর। অবাধ গতি ছিল তিনার বাসাতে। ফেরার সময় হাতটা খালি থাকত না। তিনার কালেকশন থেকে লজিকের ওপর অন্য লেখকের একটা বই দিতেন। বছর আষ্টেক পরে চাকরিসূত্রে চট্টগ্রামে যেতে হয়েছিল। প্রফেসর দত্ত তখন চট্টগ্রাম কলেজে। হাজির হলাম তিনার বাসায়। সেদিন ফেরার সময় হাতে লজিকের কোনো বই ছিল না বটে, তবে সঙ্গে ছিল একরাশ স্নেহ।
বাংলা গদ্যের অংশটার তালিম দিতেন প্রফেসর সুধীন। পড়াতেন বেশ ভালোই। তবে তিনার একটা অভ্যাস ছিল যে একটু পর পরই বলতেন : বুঝতে পেরেছ। অনেকবার শুনতে হতো ক্লাস পিরিয়ডটার ভেতর। একদিন তিনার বুঝতে পেরেছ বলাটা শেষ হতে না হতেই একজন ছাত্র বেশ জোর গলায় বলল, বুঝতে পেরেছি। নিমেষে সুধীন বাবুর চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। পারলে গিলে খেতেন। তবে মুখে কিছু বলেননি।
বাংলা গ্রামারের টুকরাটাকে খুব যত্ন করে ক্লাসে আনতেন প্রফেসর লাহিড়ী। ফিনফিনে ধুতি আর মিষ্টি হাসি; নীরস গ্রামারের ভেতর একটা অপূর্ব সজীবতা নিয়ে আসত। কোনো ছাত্রকে তিনার ক্লাস ফাঁকি দিতে দেখিনি। একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন প্রেমডোর শব্দটির সমাস নিয়ে।
তুরস্কের ইতিহাসের ওপর এভারসলি চিরোলের বইটা আমাদের কাছে কিছুটা গল্পের মতো লাগত। এর সঙ্গে প্রফেসর হাশমির সাবলীল পরিবেশন বিষয়টাকে উপন্যাসের ধারেকাছে নিয়ে আসত। ক্লাসে ঢুকতেন বিরাট একটা ম্যাপ নিয়ে। সাম্রাজ্যের বিস্তার কোন দিকে হচ্ছে, যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের সৈন্যরা কীভাবে এগোচ্ছে, এসব আমাদের জানা হয়ে যেত। প্রফেসর হাশমি অবাঙালি হলেও আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে গিয়েছিলেন। ইসলামের ওপর তিনার অগাধ পাণ্ডিত্যের কিছু ছিটেফোঁটা আমরাও পেয়েছি। পছন্দ করতেন খোলামেলা আলোচনা। কেউ কেউ আবার সেটাকে অন্য চোখে দেখত।
আমরা আরবের ইতিহাসের ভেতর চলাফেরা করতাম প্রফেসর মোখলেসুরের সঙ্গে। খুবই অমায়িক আর বয়সটা অনেক কমের দিকে থাকায় কিছুটা বড় ভাইয়ের মতো। থাকতেন কাছেই। তাই বাসাতে আসা-যাওয়ার অভাব ছিল না। ক্লাসের বক্তৃতায় বিতর্কিত বিষয়ের ভেতর এলে যেমনÑহজরত ওসমানের মৃত্যু, হজরত আলী আর মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বÑকোনো পক্ষ নিতেন না। সবদিকটাই পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করতেন। ক্লাসে অমনোযোগীরা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত ইসলামের ইতিহাসের ওপর সদ্য প্রকাশিত কে আলীর বইটার ভেতর ডুব দিয়ে। যাদের লক্ষ্য অনেক ভালো করার, তারা আমির আলি আর হিট্টির বই দুটোর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব করত।
ইকোনমিকসের শুষ্ক থিয়োরির ভেতর কিছু প্রাণ সঞ্চারণ করার চেষ্টা করতেন প্রফেসর সুফিয়ান। যখন রেন্টের ভেতর এলেন, তখন কিন্তু আমাদের মাথাটা অসহযোগিতা শুরু করেছিল। বাজারে দাম ওঠানামা, ‘ডিমিনিসিং মারজিনাল ইউটিলিটি’ ‘আরও সব বোঝাতে তিনার উদাহরণের ঝুলিতে থাকত খালি অরেঞ্জ। সেই থেকে অনেকের কাছে তিনি ছিলেন মিস্টার অরেঞ্জ। ছিলেন অনেক লম্বা-চওড়া আর আসতেন শেরওয়ানি পরে।
সারা দেশে টাকার পরিমাণ কীভাবে বাড়ে আর কীভাবে কমে, দেশটা গরিব থেকে কীভাবে ধনীর দিকে এগোতে পারে, এসব বিষয় আমাদের কাছে রহস্যে ঘেরা। আবরণটা পুরোপুরি মুছে ফেলেছিলেন প্রফেসর সুলতান। যেমনি নিপুণ ছিলেন বচনভঙ্গিতে আবার তেমনি কেতা দুরস্ত ছিলেন পোশাকে। আসতেন স্যুট আর জিন্নাহ ক্যাপ পরে। আমরা উৎসুক হয়ে থাকতাম কখন তিনার ক্লাসটা শুরু হয়।
টেলস অব হিউম্যান এন্ডেভার বইটা থেকে চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিককার একটা বক্তৃতা আমাদের সবাইকে পড়তে হতো। পড়িয়েছেন প্রফেসর নুরুল হক। লম্বায় চার্চিলের মতোই ছিলেন। চার্চিলের আবেগ অনেকটাই ক্লাসে আনতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলো তখনো আমাদের মনে সজীব। তাই বিষয়বস্তুটা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয়নি।
যাদের আবার ইংরেজি সাহিত্য ছিল তাদেরকে তিনি ‘এ লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প’ বইটা খুব দরদ দিয়ে পড়িয়েছিলেন।
ইংরেজি সাহিত্যের ভেতর রবার্ট লুই স্টিভেন্সনের ট্রেজার আইল্যান্ড বইটাও ছিল। বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু ইংরেজি গল্পের বই পড়া হয়ে থাকলেও এই বইটার পরিবেশের সঙ্গে আমরা ছিলাম অপরিচিত। পাইরেটদের রীতিনীতি, চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, জিনিস-পত্তর আমাদের অজানা। তবে অসাধারণ বর্ণনাশক্তি আর বইটার একটা ছবির বইয়ের সংস্করণ এনে সেই অভাবটা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম। স্টকেড, কাটলাস, গ্যালি, স্কুনার এবং আরও অজানা অনেক কিছুর সঙ্গে ভালো রকম পরিচয় হয়ে গিয়েছিল ছবির মাধ্যমে। প্রফেসর ইসলাম ছিলেন বেশ লম্বা। তাই আমরা দু-একটা চরিত্রের সঙ্গে আবার তিনাকে মিশিয়ে ফেলতাম।
সবাইকে যে ইংরেজিটা পড়তে হতো তার ভেতর জন গ্যালসওয়ার্দীর দ্য লিটল ম্যান বলে ছোট্ট একটা নাটক। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ছিল ব্রিটিশ, আমেরিকান, জার্মান আর ডাচ। এই লোকদের কালচার আর ভাষার বিভিন্নতা, কথা বলার ভঙ্গির পার্থক্যটা অনেক সময় নিয়ে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন প্রফেসর সিরাজুর রহমান। যেখানে আমেরিকানটা বলছে, উই ড্র দ্য লাইন অ্যাট নিগারস, সেখানে এসে পরের দিন ধরে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন দাসত্ব প্রথার শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত কালোদের প্রতি সাদাদের কী আচরণ আর মনোভাব। দশ বছর পরে আমেরিকাতে এলে তিনার সেই দিনের কিছু কথাকে জীবন্ত দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রফেসর ছিলেন তিনি। অনেক সাহায্য করতেন ইংরেজটাকে আয়ত্তে আনতে। থাকতেন কলেজের খুবই কাছে। প্রথমবার গেলে একটা দামি ডিকশনারি দিয়েছিলেন। সেই বইটা তিনি পেয়েছিলেন এমএতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার প্রাইজের ভেতর। পরে বার্নার্ড শয়ের পিগম্যালিয়ন বইটার নতুন জায়গা হয়েছিল আমার টেবিল। ইংরেজি সাহিত্যের কিছু অংশও ক্লাসে পড়িয়েছেন। সবচেয়ে অপূর্ব ছিল শেলির স্কাইলার্ক কবিতাটা পড়ানো। আমরা বসে থাকলেও তিনার কথার বাঁধুনিতে মনটা উড়ে বেড়াত নীল আকাশে স্কাইলার্কের সঙ্গে। ‘আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট’, এই জায়গায় এসে পুরো একটা পিরিয়ড কাটিয়েছিলেন এর ব্যাখ্যাতে। শুরু করেছিলেন জন্মের অপার আনন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়ানো বেদনার প্রলেপটাকে নিয়ে।
ছাত্রজীবন
প্রথম দিন ভর্তি আর আনুষঙ্গিক পর্ব শেষ করেই দৌড় দিলাম সাহেব বাজারের দিকে। কালো শেরওয়ানির অর্ডার দিতে। এইটা না পরে গেলে ক্লাসে ঢোকার অনুমতি পেলেও হাজিরাটা মিলত না। এই নিয়মটার প্রবর্তক ছিলেন আগেকার প্রিন্সিপাল জুবেরী। সবার একই পোশাক, শুধু যে দেখতেই ভালো লাগত তা নয়, সাম্যবাদের একটা প্রচ্ছন্ন বহিঃপ্রকাশও ছিল। একজনের দামি শার্ট আর একজনের সাধারণ জামার পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালেই থেকে যেত। সে সময় আর কোনো কলেজে পোশাকের বাধ্যবাধকতা ছিল না। পোশাকের ব্যাপারে মেয়েদের ছিল আবাধ স্বাধীনতা।
থাকার জায়গা হয়েছিল কলেজ হোস্টেলের এফ ব্লকের ২ নম্বর রুমে। চারজনের বসবাস। আসবাবপত্র বলতে চারপাশে স্ট্যান্ড লাগানো মজবুত একটা খাট, ডেস্ক লাগানো টেবিল, আর একটা চেয়ার। বিল্ডিংটাতে কোনো বাথরুম, ওয়াশ বেসিন ছিল না। ছয়টা ব্লক মিলে কলেজের পুরো হোস্টেলটা। মাঝখানের বিরাট জায়গাতে চমৎকার একটা বাগান। ভারী রোমান্টিক একটা পরিবেশ। অপূর্ব লাগত জ্যোৎস্নার রাতে।
হোস্টেলের একেকটা ব্লকে তেমন বেশি ছাত্র না থাকলেও বিচিত্রতার অভাব ছিল না। সদ্য আগমন আমাদের রুমে। আমাদের মতোই প্রথম বছরের ছাত্র। কাছেই বাড়ি, এই তো নওগাঁয়। মুখে কোনো হাসি-খুশির লেশ নেয়। সব সময়ই বিমর্ষ। জানা গেল অতিমাত্রায় হোমসিক। প্রতি রোববার বাবা, মা আর কোনো না কোনো নিকটাত্মীয় এসে সারা দিনটা কাটাতেন। কাক্সিক্ষত পরিবর্তন কিন্তু এল না। শেষমেশ মাস দুয়েক পর রাজশাহী কলেজটা অতীতের অধ্যায়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। বিজ্ঞানের ছাত্র। আমাদের উপরের ক্লাসের। চৌবাচ্চা থেকে পানি উঠিয়ে গোসলটা সেরে বদনার মুখটা মাটির দিক করে ঘোরাতে ঘোরাতে ফিরতেন। সবার চোখে পড়ত। কৌতূহল সামলাতে না পেরে একদিন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই ব্যতিক্রমটার কারণ কী। বিজ্ঞের হাসি দিয়ে বললেন, এই প্রক্রিয়াতে বদনা থেকে সব ব্যাকটেরিয়া বেরিয়ে যাবে। আমাদের অনেক সিনিয়র। কথা বলতেন না কারও সঙ্গে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সেটা নিজের প্রয়োজনের ভেতর পড়লে দু-একটা কথা বলতেন; তা না হলে নীরব থাকতেন। খালি একদিনই আমরা তিনার নিজ থেকে বলা কথা শুনতে পেরেছিলাম। যেদিন পিছলে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। সিনিয়র মানুষ। ডুবে আছেন পড়াশোনার ভেতর। গতবারের ফেলটাকে যদি কিছু মলিন করা যায় ভালো রেজাল্ট করে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আগমন এক বিকেলে। চৌধুরী, চলো কবি সিনেমাটা দেখে আসি। সম্ভব নয় রে, ভীষণ চাপ পড়ার। আরে চৌধুরী, এই সিনেমাটা মিস করলে কত বছর ধরে অপেক্ষা করতে হবে, তার কি কোনো ধারণা আছে তোমার। আর পরীক্ষা, ফেল করলে আগামী বছরই তো দিতে পারবে।
আমাদের হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ইতিহাসের প্রফেসর মিরজাহান। আমরা পেয়েছিলাম আরেকজন অভিভাবক। স্নেহ, উৎসাহ আর মৃদু শাসনÑকোনোটারই কমতি ছিল না। কেউ কোনো অন্যায় করে ফেললে সেটার কোনো রকম প্রচার হতে দিতেন না। আড়ালে রেখে শুধরানোর সুযোগ দিতেন। কোনো কিছুর ওপর একটা লেখা নিয়ে গেলে সেটাকে অনেক উঁচু মানের করে দিতেন। তিনার কাঁধের ওপর আবার আরও দুটো ব্লকের পরিচালনার ভার ছিল।
সুপারিনটেনডেন্টের কাজের চাপটা একটু হালকা হতো কিছু দায়ভার ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। পালা করে একেকজন ছাত্র এক মাসের জন্য হোস্টেলের খাওয়াদাওয়া, বাজার খরচের দায়িত্বে থাকত। খাওয়ার মেন্যুটা মোটামুটি ছকে বাঁধা ছিল। এক বেলা খাসির গোশত না হয় মুরগি, আরেক বেলা রুই মাছের টুকরো। কিছু সবজি আর অঢেল ডাল। আমাদের বাবুর্চি শরাফত আর তার সহকারী রান্নায় ছিল খুব পটু। সাধারণত মাসে একটা ফিস্ট হতো। হবে কি হবে না সেটার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে। বেশি ভোটটা সব সময় ফিস্টের পক্ষেই পড়ত। সম্মানিত অতিথি হিসেবে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব নিমন্ত্রিত হতেন।
বাবার কড়া হুকুম। মাস শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে খরচের হিসাবটা পাঠাবি। দেরি হলে টাকাটা পৌঁছাবে অনেক দেরিতে। প্রথম মাস শেষ হতেই খরচের একটা বিস্তারিত হিসাব গেল। বাবা লিখলেন : হিসাব দেখে মনে হচ্ছে এত বড় রাজশাহী শহরে কোনো সিনেমা হল নেই। এবার থেকে এদিকে ওদিকে না ঢুকিয়ে সরাসরি লিখবি। তবে মাসে একটার বেশি সিনেমা দেখবিনে।
শরীরটা খারাপ লাগলে দেখতেন কলেজের মেডিক্যাল অফিসার। কলেজের ডাক্তারের চিকিৎসায় তেমন সন্তুষ্টি না পেলে অনেকেই ছুটত বাইরের নতুন ডাক্তার সুলতানের ওখানে। কলেজের অফিস বিল্ডিংটার সামনের পুকুরটা পেরোলেই তিনার ক্লিনিক। কেউ কেউ আবার হাঁটা দিত বেশ দূরের মিশনারি হাসপাতালটিতে।
মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ সভা, মিটিং ভাঙাÑএসবের নেতৃত্ব দিতেন দুজন সিনিয়র। গোলাম আলি টিপু ছিলেন এর একজন। সার্কিট হাউসের পাশে সদ্য নির্মিত জিন্নাহ হলে মুসলিম লীগের মিটিং। সময়টা একুশে ফেব্রুয়ারির কিছু পরে। প্রধান অতিথি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ইউসুফ খটক। তিনি মাইকের কাছে আসতেই সামনের সারি থেকে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মাথার ওপর কাপড়চোপড়বিহীন ছোট ছোট বাচ্চা। শুরু হয়ে গেল লালাবী। আর কি, প্রধান অতিথিকে কোনো কথা না বলেই চলে যেতে হয়েছিল। মিটিং বানচাল করার এই অভিনব পদ্ধতিটা আমাদের নেতাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ছিল। সরকারি প্রোগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনজন ছাত্র কলেজ হোস্টেলে থাকত। আমাদের ব্লকে অবশ্য কেউ ছিল না। আলাপ হয়েছিল একজনের সঙ্গে। ওর কাছ থেকে ডন পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে দেখতাম। ওরা কিন্তু আমাদের ভেতর মিশে যেতে পারেনি। একবার ওদের একজন অনুষ্ঠানের ভেতর একটা মেয়েকে সম্বোধন করেছিল। ধরনটা ওদের কালচারে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আমাদের আচার-ব্যবহারে অশোভনীয়। দু-একজন মারমুখী হয়ে পড়েছিল। ওরা থাকত অনেকটা এলিয়েনের মতো। ওদেরকে কাছে টেনে আনার মতো মনমানসিকতা আমাদের ছিল না।
লেখক : অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, চেনি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ


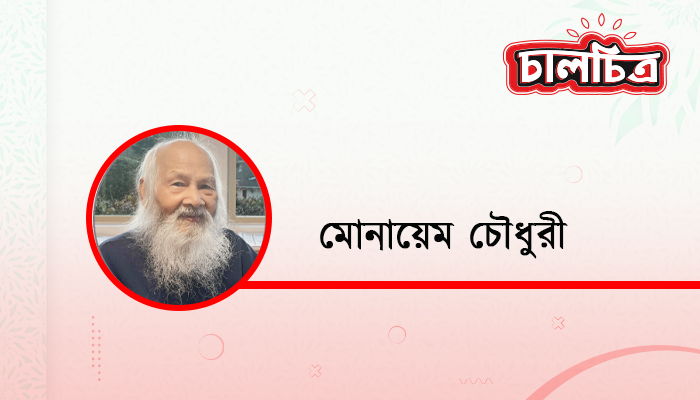 মোনায়েম চৌধুরী
মোনায়েম চৌধুরী