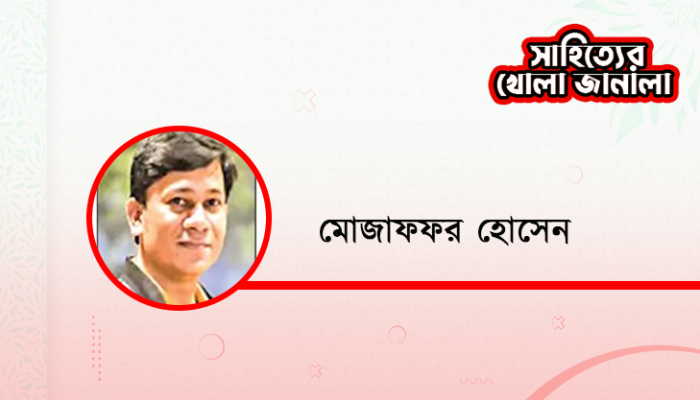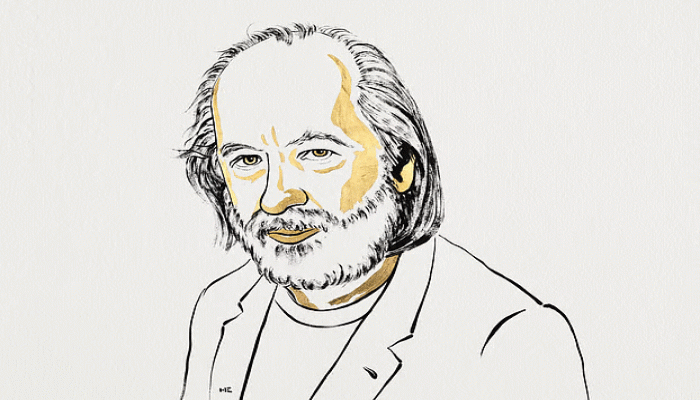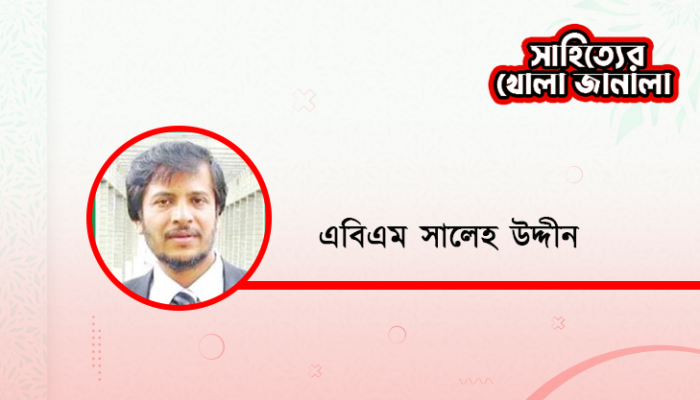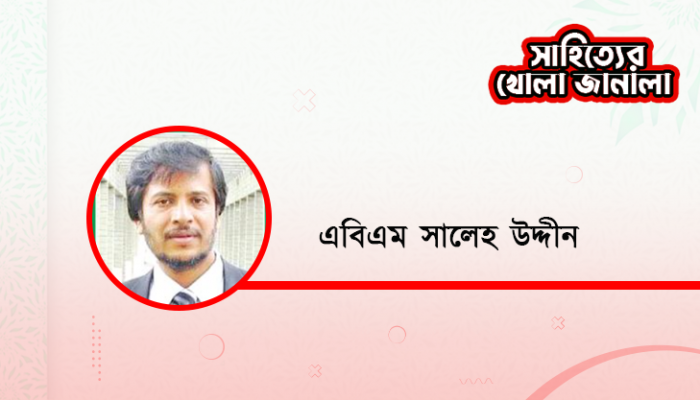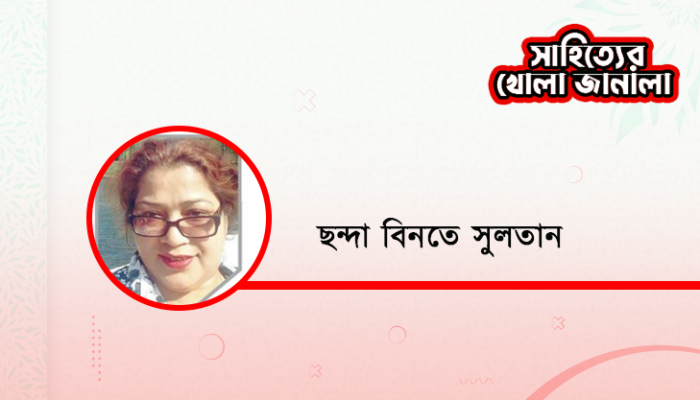কাজী মোশাররফ হোসেন
গ্রামের কবিগান, জারিগান, সারিগানের প্রতি ভালো লাগা ও ভালোবাসায় কবি সিক্ত ছিলেন শিশুকাল থেকেই। কবিগান শুনতেন, কবিগান করতেন। তাঁর কবিগানের শ্রোতা ছিল এবং তা যে খুব অল্প ছিল, এমন নয়। এই শ্রোতাদের ধারণা ছিল কবি একদিন কবিয়াল হবেন। কবির ভাষায় : ‘পাড়ার লোকেরা আমার কবিগান শুনে মন্তব্য করিত, কালে এই ছেলেটি চেষ্টা করিলে একজন কবিয়াল হইবে।’ কবি নিজেই বলেন, ‘আমি কবিয়াল হইতে পারিলাম না, হইলাম কবি জসীম উদ্দীন।’
তার মানে বাল্যকাল থেকেই জারিগান, সারিগান, কবিতার প্রতি ছিল তাঁর অদম্য আগ্রহ ও মনোযোগ।
কবিগানের ধারায় ও সুরে তার শিশুসাহিত্য বিকশিত হয়েছে। তাঁর কবিতা- ‘মামার বাড়ী’
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ী যাই।
ছোটবেলায় মামার বাড়িতে যাওয়ার সুখ এবং সেখানে মামা, নানি, খালাদের অকৃত্রিম আদর ও ভালোবাসা ফুটে ওঠে এই কবিতায়, যা এখনকার সময়ে পরিলক্ষিত হয় না বা আমাদের বাঙালি সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে এই মামাবাড়িতে যাওয়ার সুখ আছে কি না, তাতে আজকের যুগে যথেষ্ট সন্দেহ।
শিশু-কিশোরদের হাসিখেলার চিত্র তিনি একে একে চিত্রিত করেছেন তার ছড়া-কবিতায়। যেমন ‘এত হাসি কোথায় পেলে’ কবিতাÑ
এত হাসি কোথায় পেলে
এত কথার খলখলানি
কে দিয়েছে মুখটি ভরি
কোন বা গাঙের কলকলনি।
নৌকা, নদী, নদীপারের শিশু-কিশোরদের মনের গানগুলোই তিনি তুলে এনেছেন একেবারে সহজ করে-
‘পালের নাও’
পালের নাও পালের নাও
পান খেয়ে যাও
ঘরে আছে ছোট বোনটি
তারে নিয়ে যাও।
যৌবনে যে রাখাল ছেলের বা মেয়ের ভালোবাসা আঁকিবুঁকি করে, তা নিয়েও অমর কাব্যগাথা, তা-ও তার হাতেই সম্ভব। রাখালী কবিতায় তার চিত্র আমরা দেখতে পাইÑ
‘এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রানতে বসে জল আনে সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
কেমন যেন গাল দু’খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার
মাঠে ফোটা কলমি ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চলত যখন গাঙের ঘাটে
ঐ ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগত ভারী ওদের বাটে,
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস।
ঐ মেয়েটির জল-ভরনে ভাসতে ঢেউয়ে রূপের উছাস।
কবির গীতিকাব্য ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’। এখানে বাংলার, বাঙালি মায়ের গ্রামবাংলা যা দেখে তারই চিত্র ওই সুতোয় ফুটিয়ে তোলেন ধীরে ধীরে। অনেক যত্নে গড়ে তোলা সেই স্বপ্নীল কারুকার্যখচিত কাঁথা বংশ পরম্পরায় হাতবদল হতে থাকে। এখানে মা তার সেলাই করা সেই নকশি কাঁথা উপহার দেন তার মেয়ের বিয়ের পরে স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার সময়ে। মায়ের অতি আদরের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি সেই কাঁথা সন্তানের জন্য মায়ের হাতের পরশ। জসীম উদ্্দীন তাঁর এই কাব্যে বাংলা মাকে সজ্জিত করেছেন এর প্রতিটি ফুল, ফল, নদী, পাখি, মানুষের চিত্র তাঁর কলমের কালির আঁচড়ে।
নক্সী কাঁথার মাঠ
এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে
কাইজা ফ্যাসাদ করছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকও করতে পরখ ও গাঁর লোকের বল
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভালো এ-গাঁও, ও-গাঁও আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধূলায় দোলে দুখান দীঘল বাট;
দুই পাশে তার ধান কাউনের অথই রঙের মেলা
এ গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও গাঁয় যাওয়ার ভেলা
তাঁর নক্সী কাঁথার মাঠ প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। ১৯৪০ সালের মধ্যেই এটি একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়।
তিনি আমাদের আরও উপহার দিয়েছেন অমর প্রেমের ট্র্যাজিক কাব্যগ্রন্থ ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’। মিলেমিশেই ছিল শিমুল তোলা ও উড়াল খালীর হিন্দু-মুসলমান। স্বার্থান্বেষী হিন্দু ও মুসলিম জোতদাররা মুসলিম এবং নমঃ হিন্দু একে অপরকে সর্বস্বান্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। জমিজমা সব নায়েব বা জোতদারদের দখলে চলে যায়।
এই গ্রামেরই সোজন বাল্যকালের খেলার সাথি নমঃ মেয়ে দুলালীর প্রেমে পড়ে। জোতদারদের কুচক্রে তাদের বিচ্ছেদ ও সোজনের সাত বছরের কারাবাস হয়। কারাভোগের পর সোজন বের হলে সে বেদে জীবন বেছে নেয় এবং বিভিন্ন গ্রামে দুলালীকে খুঁজে বেড়ায়। অবস্থাপন্ন ঘরে দুলালীর বিয়ে হলেও সে ছিল অখুশি। দুজনের দেখা হলেও দুলালী সব কথা গোপন করে এবং স্বামীর ঘরে সুখেই আছে বলে জানায় এবং সোজনকে চলে যেতে বলে। সোজন দুঃখিত মনে চলে আসে এবং বিষপান করে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।
দুলালী বিয়ের পর কখনো সাজসজ্জা করেনি, আজ সে নিজের ইচ্ছেমতো সাজ গ্রহণ করে। তার স্বামী অবাক হয় এই সাজ দেখে। কিন্তু আজ সে পরিশ্রান্ত যেন দুলালীর সৌন্দর্য তার দেখার সময় নেই, সে শ্রান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ দুলালী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু সে স্বামীকেও তার মৃত্যুর পূর্বে হয়তো সুখী করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামী ঘুমিয়ে, সে তার সোজনকে শেষ দেখা দেওয়ার জন্য সোজনের কাছে চলে আসে, ইতিমধ্যে সে বিষ সেবন করেছে, দুজনে বিষ সেবনের মাধ্যমে তাদের জীবনাবসান ঘটায়। দুটি প্রাণ অকালে ঝরে যায়, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় তথা জোতদারদের সাম্প্রদায়িকতার দায় নিয়ে। এটি ইউনেস্কোর অনুবাদ প্রকল্পে দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে অনূদিত হয়।
কবি বড় বেশি ভালোবেসেছিলেন তাঁর গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনকে। সবাইকে তার মুগ্ধতাকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কাব্যে কবিতায় তার আকুল আবেদন তাঁর ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতায়Ñ
তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়;
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
তুমি যদি যাও-দেখিবে সেখানে মটর লতার সনে,
সীম আর সীমÑহাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেই খানে।
কবি রচনা করেছেন অসংখ্য পল্লিগীতি ও ভাটিয়ালি গান। তার মধ্যে সবগুলো ছিল জনপ্রিয়। যেমনÑ
১. আমার গহীন গাঙ্গের নাইয়া
২. আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
৩. ও আমার দরদী আগে জানলে
৪. কই গেল সেই গাঁয়ের রাখাল
৫. কোন ঘাটে লাগাব সোনার নাও
৬. আমার সোনার ময়না পাখি
কোন দোষেতে গেলে উইড়ারে
দিয়া মোরে ফাঁকি
এমন অসংখ্য গান তিনি লিখেছেন, যা হৃদয়ের রন্ধ্রে প্রবেশ করে।
কবির গানগুলো মানবমনে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে তা বাংলা রাজ্য ছেড়ে হিন্দি রাজ্যেও তার আবেদন রেখেছিল। যেমনÑ
‘রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রেÑ
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই রইলা রে।
১৯৫০ সালে প্রথম গানটি রেকর্ড হয় শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে। এ গান হিন্দি ‘দেবদাস’ সিনেমায় সংযোজিত হয়। কণ্ঠ দেন গীতা দত্ত ও মান্না দে। কিংবা
নিশিতে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা
নিশিতে যাইও ফুল বনে
এর মূল গীতিকার ছিলেন শেখ ভানু, জসীম উদ্্দীন গানটি নতুন করে লেখেন।
১৯৩৫ সালে এই গানও শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে গীত হয়।
পরবর্তী সময়ে গানটি বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী কিশোর কুমার হিন্দি সিনেমার জন্য হিন্দিতে প্লে ব্যাক করেন।
কবির কালির আঁচড়ে ফুটে উঠেছে গ্রামীণ দুঃখী চরিত্রগুলো একে একে। তাঁর একটি কবিতা দিয়ে সমগ্র চিত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমনÑ
আসমানী
আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হয়েই গড়িয়ে পড়ে পানি। ...
কবির লেখা একমাত্র উপন্যাস ‘বোবা কাহিনী’।
এক সহায়-সম্বলহীন যুবক আজহার, মজুর করে দিন আনে দিন খায়। যৌবনে বিয়ে করার সাধ হয় তার। ব্যবসা করে সংসারে উন্নতির আশায় পনেরো টাকা ঋণ নেয় শরৎ সাহার কাছ থেকে। সুদে-মূলে তা যখন ২৫ টাকায় পৌঁছে, তখন শেষ আশ্রয় বসতভিটা নিলামে ওঠে। ভিটে-মাটিহীন আজহার তার বধূ আয়েশা, ছেলে বছির এবং মেয়ে বড়ুকে নিয়ে শহরের দিকে পা বাড়ায়। ছেলে বশিরকে ডাক্তার বানানোর আশা আজহারের। প্রথম পর্বে গ্রামীণ জীবনের জোত, মৎসুদ্দির চিত্র ফুটে উঠেছে, আবার শহুরে পর্বে বিভাজন সৃষ্টিকারী রমিজ উদ্দীনদের চিহ্নিত করেছেন, চিহ্নিত করেছেন শহুরে প্রতিকূল পরিবেশ। আজহারের বুকের ভেতরের কান্না তিনি বিবৃত করেছেন। যে কথা মুখ ফুটে বলতে সক্ষম নন আজহার, তা-ই তিনি কলমের আঁচড়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।
কবি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক হিসেবে ১৯৩৮ সালে, পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগে ১৯৪৪ সালে যোগদান এবং ১৯৬২ সালে অবসরে আসেন।
১৯৬৬ সালের পরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, এখন যা বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধী দলের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। আইয়ুব খান গদিচ্যুত হন। মার্শাল ল’ আসে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সারা পাকিস্তানের একমাত্র গ্রহণযোগ্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে সমস্ত জনতা ঐক্যবদ্ধ এবং যেকোনো কাজ জনতা করত নেতার নির্দেশে। এই সময়ের চিত্র পাই আমরা কবির বঙ্গবন্ধু কবিতায়। কবিতাটি কবি লিখেছেন ঐতিহাসিক ২৬ মার্চের আগে এবং বিখ্যাত ৭ই মার্চের ভাষণের পরে। কবিতাটির অংশবিশেষ-
বঙ্গ-বন্ধু
মুজিবর রহমান
ওই নাম যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে।
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
মুজিবর রহমান।
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
আরো একদিন ধন্য হইব চির-নির্ভীকভাবে,
আমাদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চাবে,
‘কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছ বিক্রয়?’
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেইরূপ নির্ভয়।
নয় মাস যুদ্ধের ফলে বাঙালি এ দেশকে শত্রুমুক্ত করে, এক নির্ভয় জাতি ও বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে।
কবি জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর শহরের অদূরে তার মামাবাড়ি তাম্বুলখানা গ্রামে। তার বাবা ছিলেন মাস্টার আনসার উদ্্দীন মোল্লা, মা আমিনা খাতুন ওরফে রংগাছুট। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুলে। এ সময়ে খুব সংখ্যক ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো হতো। মুসলিমদের মধ্যে তার পরিমাণ ছিল শতকরা দশ ভাগেরও কম। সেদিক থেকে মোল্লা পরিবারে জন্ম নেওয়া জসীম উদ্্্দীনকে খুব ভাগ্যবানই বলা যায়। বাবা-মায়ের প্রচেষ্টা এবং নিজের প্রতিভা খাটিয়ে ১৯২১ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ পাস করেন ১৯২৪ সালে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ১৯২৯ সালে বিএ এবং ১৯৩১ সালে এমএ পাস করেন।
তাঁর অমর কবিতা ‘কবর’ যখন রচনা করেছেন, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ কবিতা মনোমুগ্ধকর এক বৃদ্ধ দাদুর জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি, যা তিনি তার নাতিকে স্বগতোক্তি আকারে বর্ণনা করেন। কবিতাটি পাঠ্যসূচিতে শ্রেণিভুক্ত করা হয় এবং কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে প্রদর্শিত হতো।
‘কবর’
এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
আমারে ছাড়িয়ে এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়।
একে একে দাদুর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি, কন্যা মারা গিয়েছে। তাদের সুখ-দুঃখের গল্প, ভালোবাসা তিনি তার নাতির সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মসজিদ থেকে আজান আসছে, কবির ভাষায়Ñ
মজিদ হইতে আযান হাঁকিছে বড় সুকরুণ সুরে
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূরে।
জোড়হাত দাদু মোনাজাত কর, আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যুব্যথিত প্রাণ।
কবি বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল লোকসাহিত্যবিশারদ দীনেশ চন্দ্রসেনের সঙ্গে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েন। তিনি ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র প্রায় ১০ হাজার গান সংগ্রহ করেন। তিনি প্রচুর ছোটদের আমুদে গল্প রচনা করেন এবং অনেকগুলো সংগ্রহ করেন। তিনি অনেকগুলোতে জারিগান, মুর্শিদি গানের সুর সংযোজন করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক। তাঁর বইয়ের মধ্য থেকে বইয়ের নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া হলো-
রাখালী (১৯২৭), নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩), রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), পদ্মাপার (১৯৫০), পল্লীবধূ (১৯৫৬), বোবাকাহিনী (১৯৬৪)।
কবি আত্মকথা লিখেছেন চারটি- ১. যাদের দেখেছি, ২. ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (১৯৬১), ৩. জীবন কথা (১৯৬৪), ৪. স্মৃতিপট (১৯৬৪)।
তিনি অনেকগুলো দেশে ভ্রমণও করেছিলেন। তা তিনি তার পাঠকদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেনÑ ১. চলে মুসাফির, ২. হলদে পরির দেশে (১৯৬৭), ৩. যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮), ৪. জার্মানীর শহর বন্দরে (১৯৭৫)।
কবি যে সময়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, সে সময়ে উপরে উঠে গেলে নিচের দিকে কেউ তাকাত না। কবি সেখানে ব্যতিক্রম। তিনি তাদের অভিব্যক্তি থেকে সরে আসেননি বরং তাতে অবগাহন করে তা থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে সমাজের মাঝে বিলিয়েছেন। তাঁর ভাষায় : ‘... দেশের অর্ধশিক্ষিত আর শিক্ষিত সমাজ আমার পাঠক-পাঠিকা। তাহাদের কাছে আমি গ্রামবাসীদের সুখদুঃখ ও শোষণ-পীড়নের কাহিনী বলিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাইতে চেষ্টা করি।’
তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনে তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেনÑ ১. প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড অব পারফরম্যান্স, পাকিস্তান (১৯৫৮), ২. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট ডিগ্রি, ভারত (১৯৬৯), ৩. ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (প্রত্যাখ্যান করেন), ৪. একুশে পদক (১৯৭৬), ৫. স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর ১৯৭৮)
এই মহান কবি ১৪ মার্চ ১৯৭৬ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাদির পাশে ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে তাঁকে চিরসমাহিত করা হয়।
ফরিদপুরের গোবিন্দপুরে জানুয়ারি মাসে ১৫ দিনব্যাপী জসীম মেলা উদ্্যাপন করা হয়। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনে হয় অনেকটা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নামে একটি আবাসিক হলের নামকরণ করেছে।
কৃতজ্ঞতা : উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া