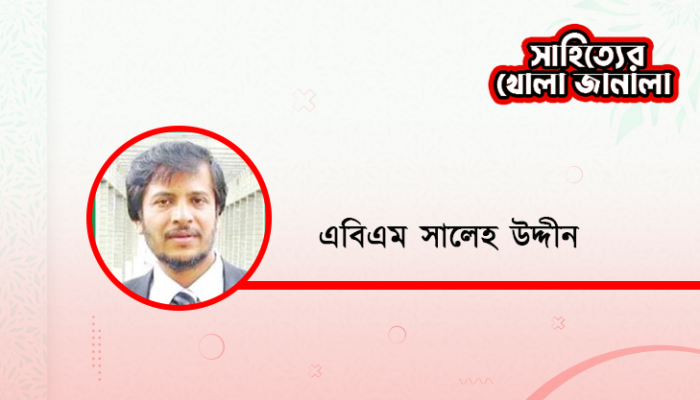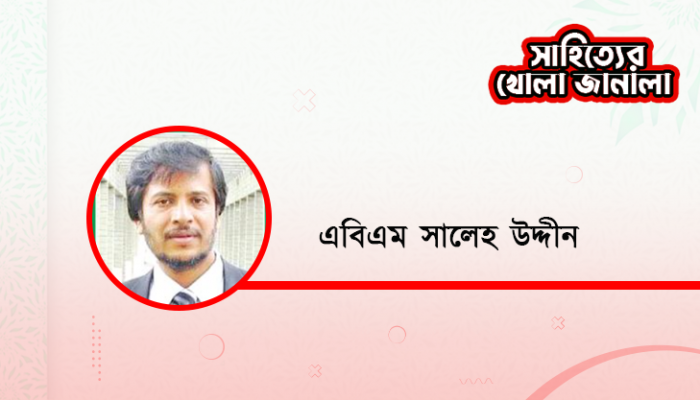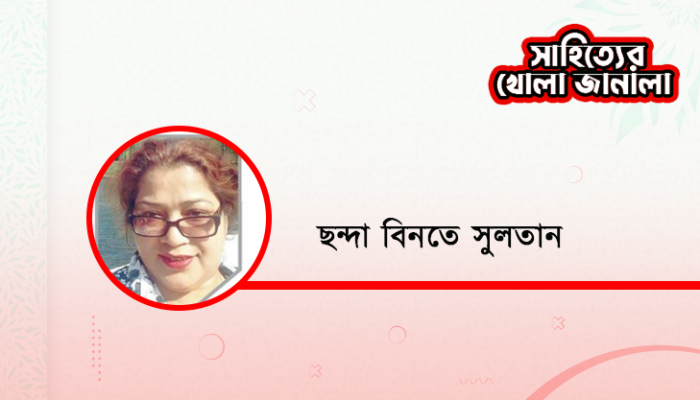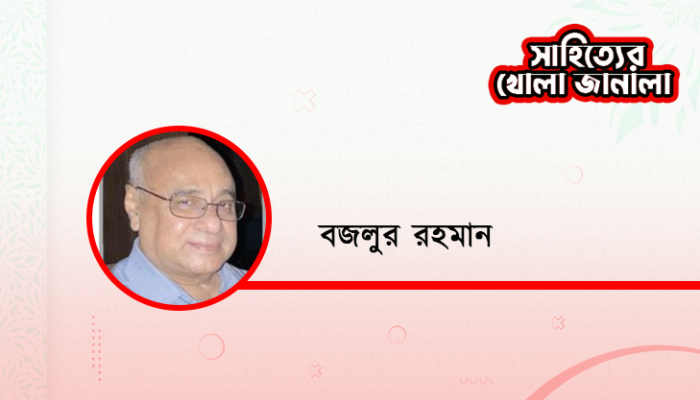কাজী নজরুল ইসলামের লেখালেখির জীবন শুরু হয় ১৯১৭ সালের পর থেকে। বিশেষ করে, তাঁর সামরিক ব্যারাকে থাকার সময়ে। তারপর ১৯২০ সালের দিকে বাঙালি পল্টনের সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন। কলকাতায় ফিরে তিনি সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ কমরেড মুজফ্ফর আহমদের আস্তানায় স্থিত হন। মুজফ্্ফর আহমদ ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। এ ছাড়া তিনি বন্ধুদের বাড়িতে থেকেছেন এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা অফিসেও কিছুদিন ছিলেন। তখন তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করতেন।
নজরুল তাঁর বন্ধু মহান কমরেড মুজফ্্ফর আহমদের সান্নিধ্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবেশ করেন পত্রিকার জগতে। এ সময়, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই শেরেবাংলা এ কে. ফজলুল হকের অর্থায়নে ও সম্পাদনায় ‘দৈনিক নবযুগ’ নামের সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশ করা হলে তার সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয় কমরেড মুজফ্্ফর আহমদ এবং কাজী নজরুল ইসলামের ওপর। পরবর্তী সময়ে নজরুলই হন নবযুগের সম্পাদক। অতঃপর নজরুলের জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে। কোথাও তিনি স্থিত হননি। তা না হলেও সর্বক্ষেত্রে নজরুলের উপস্থিতি। নবযুগ ছেড়ে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যুক্ত হন যথাক্রমে ধূমকেতু পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ শুরু করেন।
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ধূমকেতুর মাধ্যমে নজরুল সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
১৯২২ সালের আগস্ট মাসে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ধূমকেতু’। পত্রিকাটিতে যেহেতু গণমানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়ে বিখ্যাত লোকদের জ্বালাময়ী লেখা ও কবিতা থাকত, তাই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাধ সাধল নজরুল রচিত বিখ্যাত কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ বের হওয়ার পর। ব্রিটিশ সরকারের তোষামোদকারী একদল কট্টর সুবিধাবাদী চক্র নজরুলের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতিতে বিষোদ্্গার করার ফলে সরকার ‘ধূমকেতু’ পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জনকারী ধূমকেতুর সংখ্যাগুলোকে সরকার বাজেয়াপ্ত করে। নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তাঁকে ধরার জন্য পত্রিকা অফিসসহ নানান জায়গায় হানা দেয়। অবশেষে নজরুলকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। নজরুলের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সাহিত্যাঙ্গনসহ গণমানুষের মাঝে ব্যাপক প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হুলিয়া মাথায় নিয়ে ‘ধূমকেতু’ তার পরও কয়েকটি সংখ্যা বের হয়।
নজরুল সেই মামলায় এক বছর জেল খাটেন। একপর্যায়ে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, ধূমকেতু পত্রিকাটি নিয়মনিষ্ঠতার মধ্যেও স্বাধীনতাসংগ্রামীদের প্রেরণাবাহী, যার ব্যাপক কাটতির ফলে পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার ছাপা হতো।
পত্রিকার যে ৮ নভেম্বর সংখ্যায় ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি ছাপা হয়, সেটি মহররম সংখ্যা হিসেবেও গণ্য করা হয়েছিল। এই সংখ্যায় প্রচুর ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলÑছবিসমূহের একটি ছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর। এই বিশেষ সংখ্যায় নজরুলের প্রচ্ছন্ন রাজনীতি-সম্পৃক্ত কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশিত হলে ৮ নভেম্বর পত্রিকার ওই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। এ ছাড়া ধূমকেতুর দেওয়ালি সংখ্যায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুরস্কনীতি ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক নমনীয়তার কঠোর সমালোচনা করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, কাজী নজরুল ইসলামের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে এবং পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার অপরাধে ১৯২৩ সালে কারাবন্দী হন। এক বছর কারাবাসের পর তিনি বীরের বেশে জেল থেকে বের হয়ে আসেন।
কারাগারে থাকা অবস্থায়ও তিনি প্রচুর লিখেছেন। তাঁর সেসব রচনা ছাড়াও প্রতিটি রচনাই ইতিহাসের অনিবার্য অংশ হয়ে আছে। জেলমুক্ত হওয়ার পর নজরুলের সাহিত্যকর্ম আরও তীব্র ও প্রবলতর হয়ে উঠল। তিনি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যা-ই হোক, নজরুল পত্রিকার জগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেও পত্রিকা তাঁকে ছাড়ে না। কবিতা ও গান রচনার পাশাপাশি কোনো না কোনোভাবে পত্রিকার মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে যান।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর ‘লাঙল’-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। লাঙল ছিল কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা, যাকেও ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়’ পার্টির প্রকাশনা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। এই পত্রিকায় শ্রমিক শ্রেণি সম্পর্কে কবিতা এবং যুগের বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের ওপর নিবন্ধ প্রকাশ করা হতো।
সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ‘লাঙল’-এর প্রথম সংখ্যায় পাঁচ হাজার কপি ছাপানো হয়েছিল, যার সব বিক্রি হয়ে যায়। ফলে একই সপ্তাহে পুনরায় আরও কপি ছাপাতে হয়। প্রকাশনায় ‘শ্রমিক-প্রজা-সমাজ’ দলের মুখপত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলেও পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল, এর সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যেখানে নজরুল সেখানেই গণমানুষের উপচে পড়া উপস্থিতি।
উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের কৃষক-শ্রমিকদের দুরবস্থা, শোষণমূলক অবিচার থেকে মুক্তি এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করা। একটি শোষণমুক্ত দেশ ও সমৃদ্ধশীল সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে ‘লাঙল’ জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায়। কাজী নজরুল ইসলামের ‘লাঙল’ পত্রিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা ছাপা হতো। ১৯২৬ সালের ২১ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘লাঙলের’ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাতে সুভাষের জীবনী এবং তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি স্থান পায়। এই পত্রিকার উদ্যোক্তা এবং লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌম্যেন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণি সব সময় ছিল অবহেলিত। ফলে এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকেরা ব্যাপকভাবে নজরুলের প্রতি আস্থাভাজন হন এবং তাঁর প্রতি ঝুঁকে গেলেন। কেননা তখন ‘লাঙল’ পত্রিকার পাতায় গণবিপ্লব সম্পর্কে কবিতা এবং সেই যুগের বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা শুরু হয়। ধূমকেতুর মতো ‘লাঙল’ পত্রিকাও সপ্তাহে একাধিকবার প্রিন্ট করতে হয়েছিল।
নজরুলের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের পার্টিসমূহের মুখপত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। কোনো রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশের ধারণা আসে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষ থেকেই। ‘লাঙল’ পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল তাঁর সম্পাদকীয়তে দেশ-বিদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কথা তুলে ধরেন।
কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক ও শিল্পজীবন সম্পর্কে আমরা অনেকাংশে জানলেও তাঁর সাংবাদিকতা ও সম্পাদক-জীবন সম্পর্কে কম জানি। নজরুলের সম্পাদক-জীবন ও সাহিত্য-জীবনকে আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। তিনি এমন একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, একই সময়ে সবকিছুর সামাল দিতে পেরেছিলেন। যেমন তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে মুহম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত কলকাতার ‘সওগাত’ পত্রিকায়। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা ছাড়াও ভারতের কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় সমানতালে লিখেছেন।
১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর কাজী নজরুল ইসলাম, মুজফ্ফর আহমদ, শামসুদ্দীন হোসায়ন, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুব উদ্দীন আহমদ প্রমুখ মিলে ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়’ গঠন করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘লাঙল’ পত্রিকা। যার ‘নগদ মূল্য এক আনা’। এর প্রধান সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু কাজের সুবিধার্থে নজরুল সম্পাদকের দায়িত্ব দেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম থাকলেও পত্রিকার বেশির ভাগ কাজই করতে হতো নজরুলকে। তাঁর তদারকির বাইরে কোনো লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হতো না।
পত্রিকা প্রকাশে নজরুলের বিশেষ কোনো আর্থিক লাভ হয়নি। বরং একটা আদর্শগত অনুভূতির তাড়নায় অর্থকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি ‘লাঙল’ পত্রিকাটিকে পরিচালনা করতেন এবং সেটি সহসাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতৎসংক্রান্ত আরও জানা যায়, ‘লাঙল’-এর মোট ১৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
পত্রিকাটির গায়ে লেখা থাকত : ‘প্রধান পরিচালক নজরুল ইস্লাম’। প্রথম সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে বড় করে লেখা ছিল : ‘এই সংখ্যার লাঙলের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ কবি নজরুল ইসলামের কবিতা সাম্যবাদী।’ ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকায় ৮ পৃষ্ঠাজুড়ে ছিল নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের সবগুলো কবিতা। এর কারণে পত্রিকার ৫ হাজার কপি দ্রুত শেষ হয়ে যায়।
লাঙলের দ্বিতীয় সংখ্যায় ঘোষণা ছাপানো হয় : “গতবার আমরা ৫ হাজার ‘লাঙল’ ছেপেছিলামÑকয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাগজ ফুরিয়ে যাওয়াতে কলিকাতায় অনেকে কাগজ পাননি এবং মফস্বলে একবারেই কাগজ পাঠানো যায়নি। ঐ সংখ্যার প্রধান সম্পাদক বিদ্রোহী কবি নজরুলের ‘সাম্যবাদী’ গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তিকাকারে বের করা হয়, যার মূল্য নির্ধারণ করা হয় মাত্র দু’আনা।” দ্বিতীয় সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায় নজরুলের ‘কৃষাণের গান’ কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার মতো তৃতীয় সংখ্যার মাঝখানেও বর্ডার লাইন টেনে লেখা ছিল : ‘এই সংখ্যায় কবি নজরুল ইসলামের সব্যসাচী।’ বোঝাই যাচ্ছে, নজরুলের সমকালীন জনপ্রিয়তাকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সময়কার লাঙল পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পেছনে। এই সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় লেখা হয় : ‘কবি নজরুল ইসলাম এখন অসুস্থ। তাঁর শরীরটা একটু সারলেই তিনি কাউন্সিলের প্রজাদলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে প্রজা আন্দোলন উপলক্ষে মফস্বলে ঘুরবেন। যাঁরা তাঁদের চান, অনুগ্রহ করে এখনই পত্র দিবেন।’
তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পর নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া উপলক্ষে কলকাতার ঐতিহাসিক এলবার্ট হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু নজরুলের অসুস্থতার কারণে সে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হয়। এ ব্যাপারে লাঙলের চতুর্থ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : “কাজী সাহেবের বিশেষ অসুস্থতার জন্য এলবার্ট হলে ‘ভ্যারাইটি এন্টারটেনমেন্ট’ আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল। যাঁহারা টিকিট কিনিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বিক্রেতাগণের নিকট জমা দিলেই টাকা ফেরৎ পাইবেন।”
পঞ্চম সংখ্যায় নজরুলের একটি পত্র প্রকাশিত হয়, যে পত্রটি তিনি ময়মনসিংহের জেলা কৃষক সম্মেলনে অসুস্থতার কারণে অংশগ্রহণ করতে না পেরে সম্মেলন কর্তৃপক্ষের প্রতি এই পত্রিকা মারফত প্রেরণ করেছিলেন। সপ্তম সংখ্যার প্রথম তিন পৃষ্ঠাজুড়ে নজরুলের ‘অশ্বিনীকুমার’ কবিতাটি ছাপা হয়। অষ্টম সংখ্যায় নজরুলের কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘শ্রমিকের গান’। দশম ও একাদশ সংখ্যা বাদ দিয়ে দ্বাদশ সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের ‘জেলেদের গান’ কবিতা। ত্রয়োদশ সংখ্যা বাদ দিয়ে চতুর্দশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘সর্ব্বহারা’। পঞ্চদশ অর্থাৎ শেষ সংখ্যায় নজরুলের কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি।
প্রতিটি সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় নজরুলের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা চলাকালীন নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে সবগুলোর আগাম খবর ছাপা হতো।
লেখার বিষয়বস্তু : পত্রিকাটি যেহেতু ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র’ ছিল, সেহেতু বলার অপেক্ষা রাখে না, এখানে সাম্যবাদী ও বিপ্লবীদের বিষয়ই প্রধান ভূমিকায় থাকবে। প্রথম সংখ্যার দুটি লেখার শিরোনাম দেখে আমরা কিছুটা আঁচ করতে পারব। ১১ পৃষ্ঠায় ‘ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী’ এবং ১৪ পৃষ্ঠায় ‘মনিব ও কর্ম্মচারী বিদেশী কোম্পানীর নির্ম্মম ব্যবস্থা’।
পত্রিকার প্রথম থেকে অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত হেডিংয়ের ডান পাশে লেখা থাকত : “লাঙলে কী কী থাকিবে? ১. বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা, ২. ম্যাক্সিম গোর্কির জগদ্বিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস ‘মা’র ধারাবাহিক অনুবাদ, ৩. কাল মার্কসের জীবনী, ৪. প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা, ৫. গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সংকলন, ৬. প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।”
নজরুলের কোন কোন কবিতা কোন কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, সেসব আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ধারণা করা যায়, তার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ‘লাঙল’ পত্রিকা মারফত বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো অনূদিত হয়েছিল ‘মা’ উপন্যাস। প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু ধারাবাহিকভাবে নয়, মাঝখানে ছেদ পড়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চতুর্থ, পঞ্চম বাদ দিয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম, অষ্টম থেকে দশম সংখ্যায় বাদ দিয়ে একাদশ থেকে ধারাবাহিকভাবে চতুর্দশ সংখ্যায়-ভেঙে ভেঙে মোট ৯ কিস্তি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেবারের মতো অনুবাদটি অসম্পূর্ণই রয়ে যায়।
কার্ল মার্কসের জীবনী প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংখ্যায়, লিখেছেন দেবব্রত বসু। পরবর্তী সংখ্যা থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে পাঁচ কিস্তিতে লিখেছেন বিরাট কলেবরের প্রবন্ধ, ‘লেনিন ও সোভিয়েট রুশিয়া’। সপ্তম সংখ্যায় ‘কার্ল মার্কসের শিক্ষা’ নামক একটি লেখা ইংরেজি থেকে তরজমা করেছেন কুতুবুদ্দীন আহ্মদ।
১৮৫৩ সালে নিউইয়র্কের ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে যে দুটি চিঠি লিখেছিলেন, সে দুটি চিঠির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যায়। অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয়নি; সম্পাদকের দফতর থেকেই হতে পারে। সুকুমার চক্রবর্তী ও সুরেশ বিশ্বাসের যৌথ অনুবাদে প্রকাশিত হয় ‘চীনের নবজন্ম’, দুই কিস্তিতে। পঞ্চম সংখ্যার ‘লাঙল’ পত্রিকা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে করেছিল বিশেষ আয়োজন। এতে কবিতা লিখেছেন নরেন্দ্র দেব। সম্পাদকের দফতর থেকে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সুভাষচন্দ্রের ৮টি চিঠির সংকলন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যাতেও ‘সুভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্রাবলী’ শিরোনামে ৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়।
সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত : কেবল যে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের খবর আর বিপ্লবী লেখার অনুবাদ দিয়েই ‘লাঙল’ চলত তা নয়, বরং সমকালীন কলকাতার জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রও তুলে ধরা হতো। সমকালের দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে লাঙলে। স্যার আবদুর রহীম কলকাতার ‘জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ্’ এর সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘বাংলা ভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তাহলে বাঙালী মুসলমানের সর্ব্বনাশ হবে।’ এই ঘটনার প্রতিবাদে ‘লাঙল’ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, ‘স্যার আবদুর রহীম নিজে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জরিত হয়ে আছেন। সে বিষ তিনি বাঙলার সকল মুসলমানকে পান করাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মাতৃভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় সকল প্রকারের উচ্চশিক্ষা লাভ করা যে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত উপায় তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত লোক এ কথা খুব ভালো করেই জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি যে এরূপ অদ্ভুত কথা বলেছেন, তার মানে এই যে তিনি মুসলমানদের জন্য কানা গরুর পৃথক বাগান সৃষ্টি করতে চান।’ প্রকাশ থাকে যে, অন্যায়কে অন্যায়ই মনে করতেন নজরুল। যেকোনো অন্যায়ের তিনি এভাবেই প্রতিবাদমুখর ও সোচ্চার হয়ে উঠতেন। পত্রিকাটি গুরুত্বসহকারে ত্রয়োদশ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠায় ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ শিরোনামে স্যার আবদুর রহীমের সংবাদটি প্রকাশ করে এবং কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করে। কিছুদিনের মধ্যেই মিসেস এম রহমানÑনজরুল যাকে মা ডেকেছেনÑতিনি আবদুর রহীমের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে লাঙলে প্রকাশের জন্য একটি পত্র পাঠান। পঞ্চদশ সংখ্যার ৭ পৃষ্ঠায় এই প্রতিবাদপত্র ছাপা হয়। সেই প্রতিবাদপত্রের একাংশে মিসেম এম রহমান লিখেছেন : ‘আজ বাঙালী রহীম সাহেব বাঙলা ভাষার মূলোচ্ছেদ বা মাতৃজিহবা কর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! বিজ্ঞানের আকর দেশসমূহে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, হইবার নহে, বাঙলায় তাহার সূচনা কাহার অভিশাপে! শিক্ষার বূ-কাষ্ঠে বাঙালী না হয় মাতৃভাষা বলি দেবে কিন্তু মা বোনরা কোন ভাষায় পুত্র ভ্রাতাদের সহিত বাক্যালাপ করিবে, উর্দ্দু-ফার্সীতে? তাহা হইলে পুরুষদের ভাষা পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভে নারীদের জন্য প্রতি গ্রামে উচ্চ স্কুলের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যকীয়, অন্তত: কুমারীদিগকে ইরানী ইস্পাহানী গড়িয়া তুলিবার জন্য।’
বাংলা ভাষার প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের দরদ ও ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। সবার ওপর তিনি মাতৃভাষা বাংলাকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা হিসেবে মনে করতেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। ২০ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে বের হওয়া চতুর্দশ সংখ্যায় ‘কলিকাতায় দাঙ্গা’ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। খবরের একাংশে লেখা হয় : ‘এবারকার দাঙ্গার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের মন্দির ও মসজিদ কোথাও ধ্বংস করেছে এবং কোথাও-বা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। জাকারিয়া স্ট্রীটে যে মন্দিরটি ছিল সেটি মুসলমানরা নষ্ট করে দিয়েছে। আরও অন্যান্য অনেক মন্দির তারা আক্রমণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। হিন্দুরা কয়েকটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। হাওড়া পুলের নিকটবর্ত্তী জুম্মাশার দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বানারসী ঘোষ স্ট্রীট অঞ্চলেও একটি দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।’ তখনকার দাঙ্গার সময় ‘লাঙল’-এর পরবর্তী সংখ্যায় মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, ‘ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র’ নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ‘ধর্ম্ম রক্ষায় হিন্দু-মুসলমান’। ‘বিবাদ’ নামে মুজফ্ফর আহমদ দাঙ্গার ভয়াবহতা নিয়ে লিখেছেন আরও একটি লেখা। সম্পাদকের দফতর থেকে লেখা হয়েছে ‘ধর্ম্ম বিভীষিকা’।
লাঙলের চতুর্দশ সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশ হয় : ‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতেও প্রায় ৫০ জন মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য অ-বাঙালী হিন্দুগণ ঠাকুর বাড়ী ঘেরাও করেছিল। তারা বলছিল যে মুসলমানদের তাদের হাতে ছেড়ে না দিলে তারা ঠাকুর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিবে বলে হুমকি দিতে থাকে। অতঃপর কর্তৃপক্ষ পুলিশের স্মরণাপন্ন হলে পুলিশ ও কয়েকজন কনস্টেবল যখন আসে, তখন দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। আশ্রিত মুসলমানদিগকে পুলিশের হেফাজতে লালবাজার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।’ দাঙ্গার বিভীষিকাময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে মুসলমানরা যে আশ্রয় পেয়েছিল এবং তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, এ তথ্য চমকপ্রদ তো ছিলই, প্রশংসাযোগ্য ও দুর্লভ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেউ কেউ মুসলিমবিদ্বেষী প্রমাণের অপচেষ্টা করেন।
নজরুল ইসলামের বৈচিত্র্যময় জীবনের পরতে পরতে এমন বহু দুর্লভ ঘটনা রয়েছে, যা পত্রিকার পাতায় তুলে ধরা হয়েছে। নজরুলের ‘লাঙল’ পত্রিকা শতবর্ষ পার হয়েছে বহু আগে। কিন্তু তার ওপর গবেষণা করার প্রচুর উপাদান রয়েছে। বাংলা সংবাদপত্র জগতে নজরুলের অবদান বিস্ময়করভাবে দিতে পারে নতুন নতুন পথের সন্ধান। আবার লাঙলের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। লাঙল পত্রিকার প্রচ্ছদে কাঁধে লাঙলবাহী একজন কৃষকের ছবি ছাপা হতো। পত্রিকার প্রথম পাতায় মানুষের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে চণ্ডীদাসের একটি উক্তি মুদ্রিত হতো। লাঙলের প্রথম সংখ্যার আকর্ষণ ছিল ‘সাম্যবাদী’ শিরোনামে নজরুলের এগারোটি কবিতার সমাহার। কৃষক, নারী, দিনমজুর, কুলি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পীড়িত ও নির্যাতিত জীবনের বর্ণনাত্মক এ কবিতাগুলো পরবর্তীকালে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, লাঙলের বিভিন্ন সংখ্যায় নজরুলের কিছু বিখ্যাত গানের একটি অংশ আছে, কবিতা প্রকাশ করা হতো। যেমন ‘কৃষাণের গান’, সব্যসাচী’ এবং ‘সর্বহারা’। লাঙলে অন্যান্য লেখকের রচনাসমূহের বিষয়বস্তু ছিল তৎকালীন সমাজতন্ত্রী নেতা কার্ল মার্কস, লেনিন বা সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক গতিধারা, চীনের পুনর্জাগরণ এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদি। এভাবেই ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ‘লাঙলের পঞ্চদশ সংখ্যাই ছিল শেষ সংখ্যা, যা শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখনই যে অবস্থায় ছিলেন, তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং শিল্পকর্মের বিরতি ছিল না।



 এবিএম সালেহ উদ্দীন
এবিএম সালেহ উদ্দীন