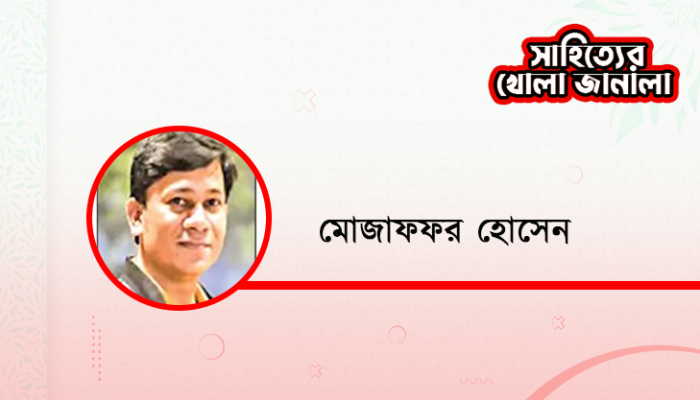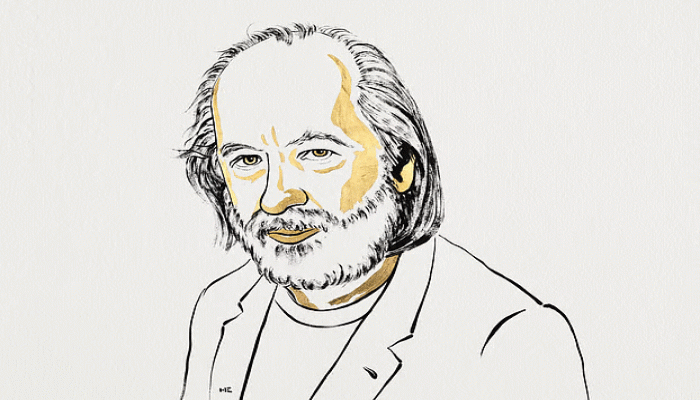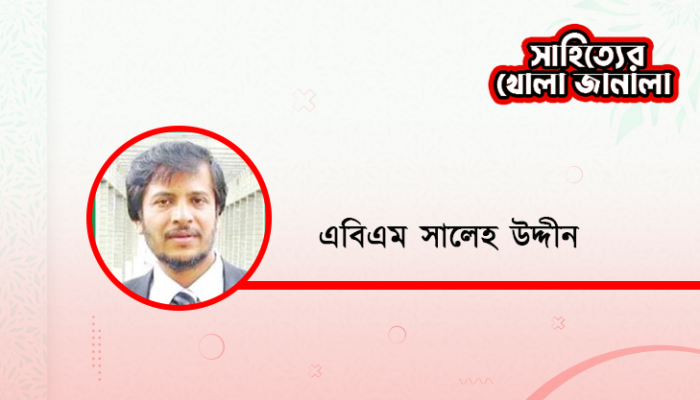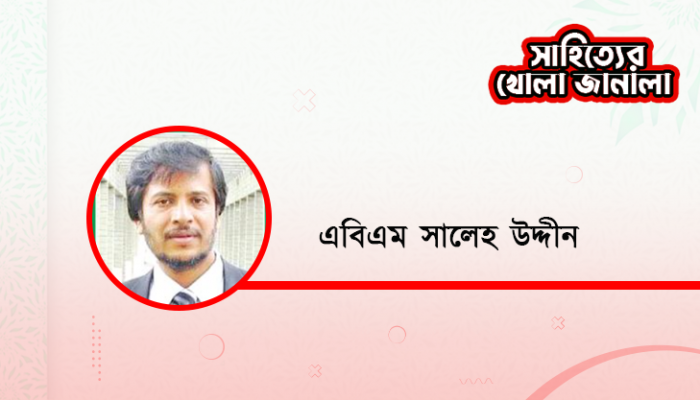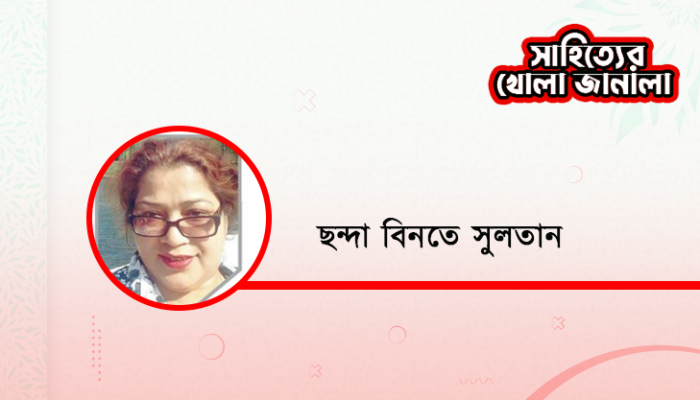২০২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই (László Krasznahorkai)। ফ্রানৎস কাফকার উত্তরসূরি হিসেবে আখ্যায়িত লাসলো ক্রাসনাহোরকাই মধ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার মহাকাব্যিক লেখক। তার লেখালেখির প্রধান বিষয় হলো সামাজিক-রাজনৈতিক অসংগতি।
মানবিক স্খলন ও বীভৎসতাকে তিনি অতিরঞ্জিত করে তোলার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এজন্য ডিসটোপিয়ান লেখক হিসেবেও তাকে পাঠ করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ইতিহাসের ঘূর্ণিতে নিষ্ঠুরতা ফিরে ফিরে আসে। এখন আমরা আবার সেই সময়েই আছি। নিষ্ঠুরতা রাস্তায় প্রকাশ্যে ঘটে চলেছে। এর প্রতিরোধ হিসেবে আমি যা করতে পারি তা হলো লেখা’।
১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের শহর জিউলালে জন্মগ্রহণকারী এই লেখক জার্মানিতে বসবাস করছেন। লেখেন প্রধানত ছোটগল্প ও উপন্যাস। প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুখ্যাতি আছে। বেশকিছু ছোটগল্প ও নভেলাসহ পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস ‘ঝধঃধহঃধহমড়’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে।
তার পাঠকপ্রিয় উপন্যাস ‘The Melancholy of Resistance’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমি মেলানকোলিক মানুষ। আমার ধারণা, মেলানকোলি মানে এমন এক বোধ, যেখানে মানুষজ্ঞানের মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজে পায়। মেলানকোলিক মানুষ সময় নেয় শুধু বসে থাকার জন্য, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বসে থাকতে পারে। ইউরোপের আগের কৃষক সমাজে মানুষ এমনই ছিল- সময়ের বাইরে, নিঃশব্দ। তলস্তয়ের একটা গল্প মনে আছে, তিনি লিখেছিলেন- ‘আমি কৃষকের কাঁধে হাত রাখার আগে, সে কোথাও ছিল না। ঠিক তেমনই মেলানকোলিক। মেলানকোলি আমাদের শুধু থাকতে দেয়- থাকা, শুধু থাকার জন্য। কোনো আকাক্সক্ষা বা প্রেরণা দেয় না।’
নিজের ছোটগল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমার ছোটগল্পগুলো আমার নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে আসে, ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে নয়। আমি অনেক সময় ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করি যেন তা একদিকে রীতিমতো ধনী, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি। শুনেছি, অনেকেই বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে না। আমি তাদের সেই দৈনন্দিন কথার ভেতরেই আমি একধরনের নতুন ছন্দ খুঁজে পাই।’
তার একাধিক বই থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন প্রখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পরিচালক বেলা তার (Béla Tarr)। সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম আধুনিক ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত ‘দ্য তুরিন হর্স (The Turin Horse)’ লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের প্রবন্ধ থেকে নির্মাণ করেন বেলা।
লাসলো ক্রাসনাহোরকাই বিশেষভাবে চিহ্নিত তার স্বতন্ত্র গদ্য ও তার দার্শনিক প্রজ্ঞার কারণে। তার লেখা খুব সহজপাঠ্য না। তিনি দীর্ঘ বাক্যে গদ্য লেখেন। কোনো কোনো বাক্য এক পৃষ্ঠা। তার ‘দ্য লাস্ট উলফ (The Last Wolf)’ বড় গল্পটি পুরো একটা বাক্যে লেখা। অন্যান্য যতিচিহ্ন থাকলেও কোথাও তিনি দাড়ি বা ফুলস্টপ ব্যবহার করেননি।
এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, “আমার উপন্যাসে দেখবেন, বাক্য কখনো শেষ হয় না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, মানুষের কোনো ভাবনা, কোনো অনুভূতির আসলে ‘শেষ’ নেই। একটি বাক্য এগিয়ে চলে সময়ের মতোÑ ক্রমাগত, অবিরাম এগিয়ে চলে। এই কারণেই আমি বিরামচিহ্ন না দিয়ে গদ্যের ধারাকে চলতে দিই; আমি চাই মানুষের মতো বাক্যটিও শ্বাস নিক”।
হাঙ্গেরির আধুনিক সাহিত্যের অসামান্য এই লেখক ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে কয়েক দশক ধরেই জনপ্রিয়। ২০১৫ সালে বুকার প্রাইজ পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক মহলেও জোরেশোরে উচ্চারিত হতে থাকে তার নাম। সাহিত্যে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা তার নোবেল প্রাপ্তিতে বিস্মিত হননি।
কয়েক বছর ধরেই নানা মহল থেকে এই পুরস্কারের দাবিদার হিসেবে তার নাম উচ্চারিত হয়ে আসছে। এ বছরও বুকিদের তালিকায় তার নাম ছিল দুই নম্বরে। ২০২৩ সালের নোবেলজয়ী লেখক ইয়োন ফসে (Jon Fosse) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তার পরে যদি কেউ ইউরোপ থেকে সাহিত্যে নোবেল পান তিনি হবেন লাসলো ক্রাসনাহোরকাই।
হাঙ্গেরি ছোট্ট একটা দেশ। মাত্র এক কোটির মতো জনসংখ্যা। এই দেশ থেকে এর আগে ২০০২ সালে ইমরে কার্তেজ (Imre Kertész) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ইউরোপীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, যুদ্ধ এবং ভাঙনের সঙ্গে হাঙ্গেরি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জনসংখ্যার বিচার দিয়ে একটি জাতির সাহিত্যিক সমৃদ্ধি বিচার করা যায় না। কিন্তু তারপরও কিছু অনিবার্য প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে।
বিশ্বসাহিত্য নিয়ে ইউরোপীয় রাজনীতির কথা মাথায় রেখেও আমরা ভাবতে থাকি বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে। প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য হাজার বছরেরও পুরনো। এই ভাষার লেখক শতবর্ষ আগেই সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন। এতকিছুর পরও কেন আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেল না বাংলা সাহিত্য?
সাহিত্যে নোবেল হয়তো পরিকল্পনা করে অর্জন করা যায় না। কিন্তু একটা দেশের সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জনে নিশ্চয় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি দুই বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বুকার পেল ভারতের হিন্দি ও কন্নড় ভাষার দুইজন লেখক।
২০২৪ সালে নোবেল পেল কোরিয়ার তুলনামূলক নবীন লেখক হান কাং (Han Kang)। নবীন বলছি এই কারণে, হান কাং ২০১৬ সালে ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান (The Vegetarian)’ দিয়ে দ্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ অর্জন করে বিশ্বে পরিচিতি পান। ২০১৫ সালে তার প্রথম উপন্যাস অনূদিত হয়, এটা দ্বিতীয়। অর্থাৎ তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি এক দশকও হয়নি। অনূদিত হয়েছে মাত্র চারটি উপন্যাস। অর্থাৎ এক দশকের পরিচিতি ও মাত্র চারটি উপন্যাস দিয়েই তিনি ৫৩ বছর বয়সে এসে নোবেল পেয়ে গেলেন।
অনুবাদক ডেবোরা স্মিথ (Deborah Smith)-এর বয়স মাত্র ৩৭। এই ব্রিটিশ লেখক অনুবাদক বছর দশেক কোরীয় ভাষা শিখে হান কাং অনুবাদে হাত দেন। তার অনুবাদে ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান (The Vegetarian)’ আমেরিকায় প্রকাশিত হলে সে বছরই পুরস্কার পেলেন হান কাং।
এখন প্রশ্ন হলো, কোরীয় লেখক হান কাংয়ের আন্তর্জাতিকতার কাছে বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতা পিছিয়ে কেন? মূল কারণ, একজন ডেবোরা স্মিথের অভাব। অর্থাৎ ইউরোপীয় বা আমেরিকান অনুবাদকদের বাংলাদেশের সাহিত্যে আকৃষ্ট করতে না পারা।
বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতায় অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই, এ কথাটা না বললেও চলে। এখন প্রশ্নটা হলো, এই অনুবাদের কাজটি কীভাবে হবে? কারা অনুবাদ করবেন? কারাই বা প্রকাশ করবে?
ইংরেজি ভাষায় বাংলাদেশের সাহিত্যের অনুবাদ হয়ে আসছে মোটামুটিভাবে সত্তরের দশক থেকেই। অনুবাদক হিসেবে আমরা দেখি, প্রথমত, বাংলাদেশের যারা অন্যান্য ভাষা জানেন এবং অনুবাদ করেন; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের প্রবাসী বা ডায়াসপোরা অনুবাদকরা। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদক প্রায় বেশির ভাগ প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা থেকে। বাংলাদেশের অনুবাদের আন্তর্জাতিক প্রকাশনা বলতে যেগুলো হয়, অধিকাংশ ভারত থেকে। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকাকেন্দ্রিক প্রকাশনা ছাড়া একটি দেশের সাহিত্যের ‘আন্তর্জাতিকতা’ প্রায় অসম্ভব। আবার ঢাকার অনুবাদকদের দ্বারা ইউরোপ-আমেরিকার মূলধারার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বই প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কাজ। তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব; কিন্তু দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন।
এক্ষেত্রে আমাদের সামনে ক্লাসিক উদাহরণ হলো রবীন্দ্রানুবাদ। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বঙ্গদেশীয়/ভারতীয় অনুবাদকের মাধ্যমে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের নির্ভরযোগ্য অনুবাদকদের ভেতর আছেন মারিনো রিগন (Marino Rigon) যিনি বাংলা থেকে সরাসরি ইতালি ভাষায় অনুবাদ করেছেন, ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন আঁদ্রে জিদে (André Gide)-এর মতো প্রখ্যাত লেখক, যিনি পরবর্তীকালে নিজেও সাহিত্যে নোবেল পান, স্পেনে আরেক নোবেলজয়ী লেখক কবি হুয়ান রামোন হিমেনেস (Juan Ramón Jiméney), আর্জেন্টিনায় ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো (Victoria Ocampo), নেদারল্যান্ডে ফ্রেডরিক ভ্যান ইডেন (Frederik Willem van Eeden), চেক ভাষায় ভিনসেনস লেসনি এবং দুসান জ্বভিতেল (Dušan Zbavitel), লাটভিয়াতে কার্লিস ইগল এবং রিচার্ডস রুডিটিস, আরবে মুহাম্মদ সুখরি আয়াদ এবং রুশ ভাষায় এ পি নাতুক-ডানিল’ চাক (A P Natuk-DanilÕChak)।
রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার জাপানি অনুবাদক কবি মাশিনো সাবুরো (Mashino Saburo)। বহুভাষী ও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়াতানাবে সোকো (Watanabe Shoko)-এর অনুবাদে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। আরবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদক সম্ভবত লেবানি কবি ওয়াদি আল-বুস্তানি (WadiÕ al-Bustani)। তানিয়াস আবদুহ-এর অনুবাদে কায়রো থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
১৯৬১ সালে কবির শতবার্ষিকীতে চীনা অনুবাদকদের প্রচেষ্টায় ১০ খণ্ডে নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ চীনা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ২০০০ সালে চীনের হ্যপেই শিক্ষা প্রকাশনা থেকে ২৪ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ২০১৬ সালে সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ রবীন্দ্র রচনাবলী চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ৩৩ খণ্ডের এ অনুবাদকর্ম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র রচনাবলী অনুসরণ করে বাংলা ভাষা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।
যদি রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে আমরা মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতি-অমিয়ভূষণদের মধ্যে থেকে দুয়েকজনকে বিশ্বে তুলে ধরতে পারতাম তাহলে বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব-ঐতিহ্য তৈরি হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোনো লেখকের রচনা বিশ্ববাজারে পৌঁছায়নি। বাংলাদেশের সাহিত্যের জনপ্রিয় বৈশ্বিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কেউ হননি। আরও দুর্ভাগ্য, সরাসরি যারা ইংরেজিতে লেখেন, তাদের মধ্য থেকেও আমরা একজন চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe) (নাইজেরিয়া), একজন অমিতাভ ঘোষ (Amitav Ghosh) (ভারত), একজন হানিফ কুরেশী (Hanif Kureishi) (পাকিস্তান) কিংবা মাইকেল ওন্দাৎজে (Michael Ondaatje) (কানাডীয় শ্রীলঙ্কান)- এদের মতো একজনও আন্তর্জাতিক লেখক পাইনি।
বাংলা ভাষায় বিশ্বমানের লেখক এখনো আছে, আমরা তাদের অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে পারিনি। এর কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে শিল্পসাহিত্যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা। বাংলাদেশ সরকার কখনো উন্নয়ন বলতে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বোঝেনি। সবসময় অবকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে।
সফট পাওয়ার তৈরিতে শিল্পসাহিত্য ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের আন্তর্জাতিকীকরণ রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুভব করেনি। এসব কারণে বাংলা সাহিত্যের যে আন্তর্জাতিক যাত্রা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে শতবর্ষ আগে শুরু হয়েছিল, সেটা গত ৫০ বছরে বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু অনেকটা কালক্ষেপণ হলেও সময় শেষ হয়ে যায়নি।
স্বাধীনতার এত বছরে এসে বিশ্বসাহিত্যের মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যূথবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে। শিল্প-সাহিত্যের আন্তর্জাতিকীকরণ ছাড়া বর্তমান বিশ্বে নিজস্ব আইডেনটিটি তৈরি করা কঠিন। জানি না রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের সেই বোধ কবে হবে! কিন্তু আশা হারাতে চাই না। আমাদের আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্য ছিল, আছে, বাকিটা যা দরকার সেটা হলো যথাযথ সমন্বিত উদ্যোগ।



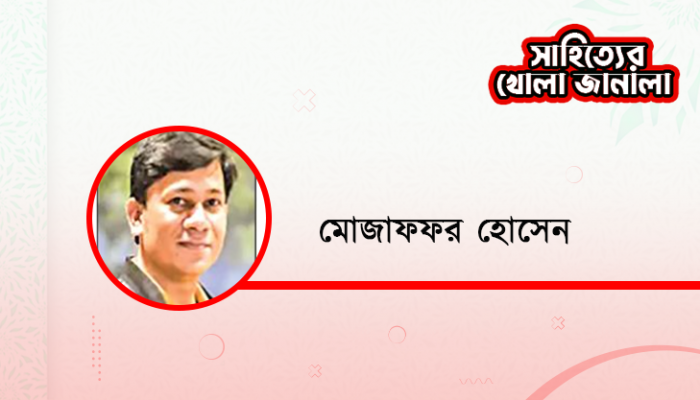 মোজাফ্ফর হোসেন
মোজাফ্ফর হোসেন