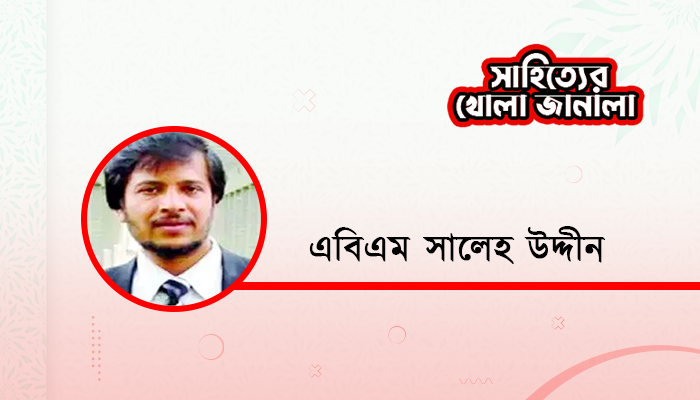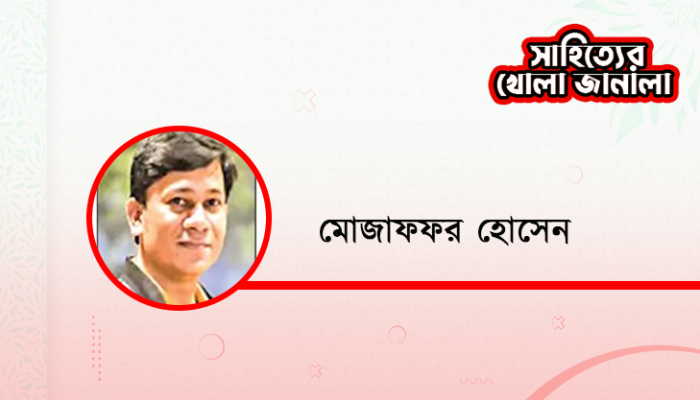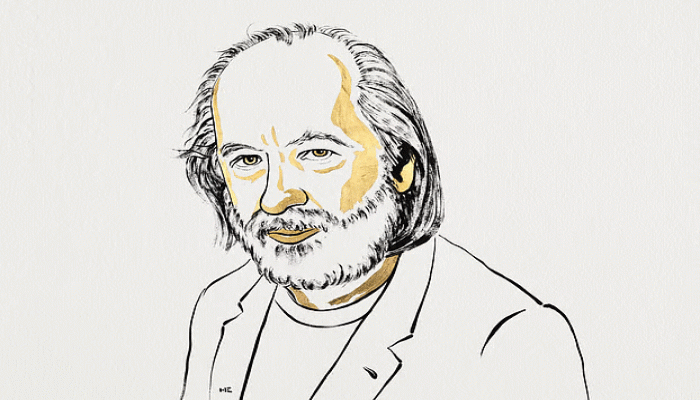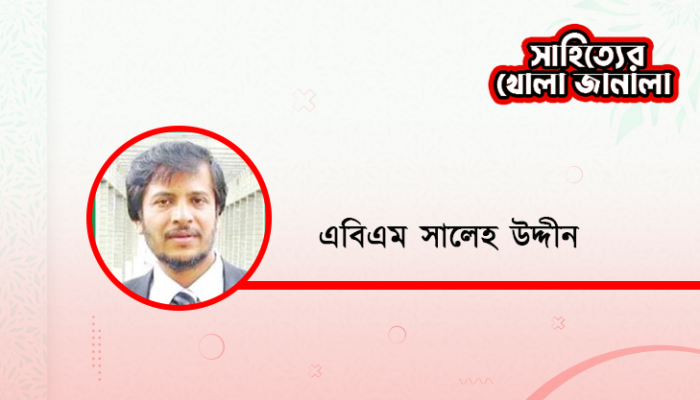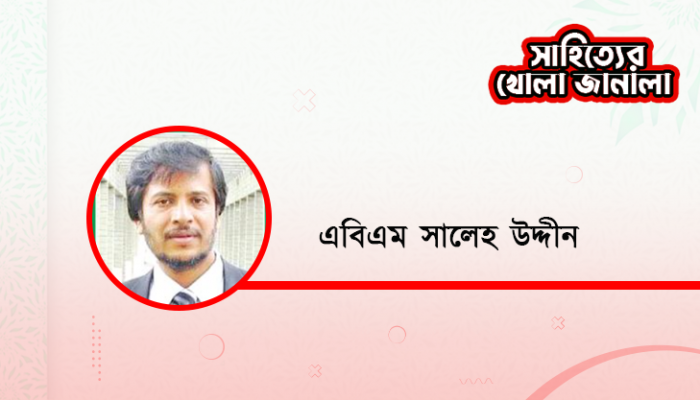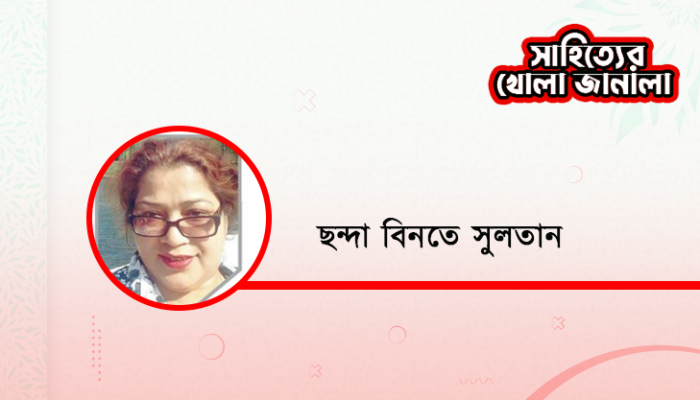এবিএম সালেহ উদ্দীন
মাহমুদ দারবিশ আরববিশ্বের স্বাধীনতা ও মানবতাবাদী কবি। কবিতার ভুবনে তাঁর প্রতিটি শব্দকণা আকাশছোঁয়া। জীবন বাস্তবতার কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়েছেন। জীবনযুদ্ধের তীব্র উত্তাপের মধ্যেই সকল ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে সয়ে তিনি মাবনতার জয়গানে ন্যস্ত ছিলেন। স্বাধীন তীব্র টান ও উত্তাপের কারণে তাঁকে প্রতিবাদী কবিও বলা হয়। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই ফিলিস্তিনকে ঘিরে আবর্তিত। শিশুকালে নিজের জন্মভূমির মায়ার পরশ থেকে ছিটকে পড়ার ফলেই সারা জীবন তাঁকে কঠিন সংকটের পাহাড় অতিক্রম এবং সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।
এই দিক থেকে পৃথিবীর অন্য অনেক কবির বেলায় সেটি ঘটেনি। তিনি নির্বাসিত জীবনে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার আকুতি প্রকাশ করেন এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাক্সক্ষায় পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন। শুধু ফিলিস্তিন নয়, গোটা আরবেই রয়েছে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি। আরববিশ্বে তাঁকে বলা হয় আধুনিক আরবি কবিতার উন্নয়ন প্রতিভূ।
পৃথিবীতে একেক কবির মেধা ও মননের প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা রয়েছে। স্থান-কাল ও সময়ের প্রয়োজনে সেটি নানান আঙ্গিকে ধরা পড়ে। তাঁর কবিতায় মানববিধ্বংসী আগ্রাসী শক্তির জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ আছে। ভাগ্যহারা ফিলিস্তিনি জনজীবনের দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারের কথা বিধৃত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির শোষণ-নিপীড়ন ও দুর্দশার করুণ বর্ণনার পাশাপাশি দারবিশ তাঁর কবিতায় ফিলিস্তিনি জনগণের হতাশা ও নিরাশা বিদূরিত করে দুঃখ-কষ্ট, বিরহ-বেদনার উদ্ভাসিত অনুভবের মধ্যেও মুক্তির প্রত্যাশায় নতুন দর্শনের পথ উন্মোচন করেছেন।
যেমন রবীন্দ্রনাথ যখন বিনিদ্র তপস্যায় জীবনসাহিত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের চিরন্তনী রূপকে নানান আঙ্গিকে, বিচিত্র বৈভবে রূপ দিয়েছেন; শিল্পসাহিত্যের মহাসমুদ্রে মানুষের জীবনের অনন্ত মায়াকে আনন্দ, বেদনা ও বিরহ-বিদ্রƒপের তুলিতে সুন্দরতম অবয়বে এঁকেছেন; অগাধ সম্পদ ও জমিদারি ঐতিহ্যের রাজসিক প্রভাবে থেকেও তিনি শিল্পসাহিত্যের আকাশকে সর্বজনীন ও সুসমৃদ্ধ করেছেন; তেমনি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর আত্মসংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে আকাশচুম্বী মেধা ও উত্তঙ্গ কাব্যবোধের দ্বারা দুর্বোধ্যতার সকল প্রাচীর চুরমার করে দিয়েছেন এবং শিল্পবোধ ও কবিতাকেই সর্বোন্নত এবং সুউজ্জ্বল করে তুলেছেন।
সেই তুলনায় মাহমুদ দারবিশের কাব্যচর্চা, সাহিত্যবোধ ভিন্ন আঙ্গিকের এবং ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে বিচার্য। তিনি ঘাতে-প্রতিঘাতে জীবনের কঠিনতম বাস্তবতার মধ্যে কাব্যরচনা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। এই কবির মানসলোকে সতত ক্রিয়াশীল স্বদেশচেতনা, স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতি, পৃথিবী, মাটি ও মানুষ।
চিরায়ত বিশ্বাসের ছায়া, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের লালিত মায়া এবং জন্মভূমির কোলে জন্ম নিলেও নিয়তি তাঁকে কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ পথে ঠেলে দিয়েছে। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, দেশছাড়া-ভূমিহারা মানুষের আর্তনাদ। ভুক্তভোগী ও একেবারে কাছে থেকে তিনি ইসরাইলি আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছেন। দেখেছেন আপন মাতৃভূমির মৃত্যুর বিভীষিকা। আগ্রাসীদের পাশবিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর করুণ দৃশ্য ও মৃতপুরীতে দস্যু-দানবের তাণ্ডব দেখার মধ্য দিয়েই তিনি জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে গেছেন। পথে-প্রান্তরের সর্বস্থান তাঁকে স্বাধীনতা, মানবতার মুক্তির লড়াইয়ে আত্মনিয়োজিত হতে বাধ্য করেছে। সময়ের সকল প্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই তিনি জীবনকে উপভোগ ও উপলক্ষ করেছেন।
মাহমুদ দারবিশ এমন এক কবি, যিনি ছিলেন নিপীড়িত ও স্বাধীনতাকামী মানুষের কণ্ঠস্বর। যাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দকণা একেকটি দুর্মর পাথরখণ্ড, যদ্দ¦ারা মানববিশ্বের কুলহারা, অধিকারবঞ্চিত মানুষের স্বাধীনতার আকুলতা ও মুক্তির পথ দেখায়। প্রগতি ও মানবিকতার প্রচলিত মিথকে ভেঙে জগৎ-পৃথিবী ও মানুষের জীবনের নবতর চেতনা, উপলব্ধি ও কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে। অযাচিত ধ্বংসযজ্ঞ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতার করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি পরদেশে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। কঠিন বাস্তবতাকে জীবনের সঙ্গী করেই নিজে বহু কষ্টে লেখাপড়া করেছেন।
কেননা, নিজের জন্মভূমি, ঘরবাড়ি, আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে শিশুকাল থেকেই অন্তরে নানান প্রশ্নের উদ্রেক হয়। সেই প্রশ্নের নিয়ত তাড়নায় তিনি কবিতার ভুবনে আবির্ভূত হন।
মাহমুদ দারবিশের জন্ম ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনের ‘আল-বিরওয়া’ গ্রামে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলি সৈন্যদের অতর্কিত হামলা ও ভয়াবহ আগ্রাসনে কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। নিশ্চিহ্ন জনপদে নেমে আসে স্বজনহারা আর্তনাদ ও শোকের ছায়া। ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াল রাতে যখন আগ্রাসী সৈন্যদের গোলাবর্ষণ শুরু হয়, শত শত ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নারী ও শিশুসহ বহু মানুষের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটে। তখন মাহমুদ দারবিশ পাঁচ বছরের শিশু। সেই ভয়াবহ রাতে আক্রান্ত দারবিশের এই ছোট্ট গ্রামটিও সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দারবিশের পরিবারটি বেঁচে যায়। বর্বর সৈন্যদের চোখে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা একটি ক্ষেতে লুকিয়ে ছিলেন।
অতঃপর নিজ জন্মভূমি থেকে পালিয়ে ঘরবাড়িছাড়া অন্যান্য অসহায় ফিলিস্তিনির সঙ্গে মাহমুদের পরিবারও শরণার্থী হয়ে লেবাননের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। এক বছর পর দারবিশ তাঁর চাচার সঙ্গে লেবাননের সীমান্ত দিয়ে তাঁর হারানো জন্মভূমিতে আবার প্রবেশ করেন। নিজের জন্মভূমিতে ঢুকে শিশু দারবিশ দেখলেন মৃত্যুর বীভৎস চিত্র ও ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপ! দেখলেন, কীভাবে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞে তাঁদের গ্রাম, শহর, উপত্যকাগুলো জনশূন্য, বিরান ও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইসরাইলি কামানের গোলার আঘাতে কীভাবে ভস্ম হয়ে গেছে তাঁদের ঘরবাড়িসহ ফিলিস্তিনি গ্রামগুলো। শিশুকালের সেই করুণ বর্ণনা দিয়ে মাহমুদ দারবিশ বলেন :
‘এক রাতে আমার চাচা এবং একজন পথপ্রদর্শকের সঙ্গে লেবাননের সীমান্ত দিয়ে আমি আবার প্রবেশ করলাম ফিলিস্তিনে। সকালে উঠে দেখি, আমি একটি ইস্পাতকঠিন দেয়ালের মুখোমুখি। জননী জন্মভূমির অভ্যন্তরে। কিন্তু কোথায় আমাদের ঘরবাড়ি? আমি আর কখনো আমার জন্মস্থান, আমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারিনি। দুঃখ-বেদনা ও প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে আমি দেখতে পেলাম, আমার গ্রামখানি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত-ভস্ম এবং ছারখার হয়ে গেছে। জনশূন্য, বিরান ও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই।’
তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় সেসব করুণ অভিজ্ঞতার কথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মাহমুদ দারবিশের কবিতা ও লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা, মানবতার মুক্তি এবং অধিকারহারা মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার নিরলস আহ্বান। যে জাতি তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করত, তাদের ওপর চালানো হয় পৈশাচিক বর্বরতা। স্বভূমিতে জন্মভূমির কোলে সহস্র বছর তাদের স্বাধীন স্বদেশের প্রেম ও ভালোবাসা বুকে ধারণ করে স্থিতিশীল ও অবস্থান করছে, সেই জাতি হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ভিটাবাড়ি হারিয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়। ফিলিস্তিনিদের সেই সব মানবেতর জীবনের করুণ বর্ণনায় তিনি তাঁর সংক্ষুব্ধতা ও বেদনাগ্রস্ত দুঃখবোধকে কবিতা ও সাহিত্যে ব্যক্ত করেন; যার সিংহভাগজুড়ে রয়েছে জনগণের পরাধীনতা ও নির্বাসনের করুণ বর্ণনা।
সেই শিশুকালেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, কেন তাঁদেরকে নিজের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করা হলো? যুগ যুগ ধরে যে ভূমিতে তাঁরা বসবাস করেন, অকস্মাৎ কেন তাঁদের এমন নির্মম ও নির্দয়ভাবে বিতাড়িত করা হলো? কেনই-বা স্বাধীন ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করে দিয়ে সেই ভূখণ্ডকে ইসরাইল নামক দস্যু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে! সারা জীবন বুকভরা ব্যথা, দুঃখ ও হতাশাদীর্ণ কষ্টবোধ তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন। তার পর থেকে প্রতিবছর ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমিতে দস্যু সৈন্যরা আগ্রাসন, নিপীড়ন চালিয়ে তাদের ভূমিকে দখল করে নিতে থাকে। যুগ যুগ ধরে পালায় পালায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি বর্বরতা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চলে আসছে। এভাবেই জীবনে বহু কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন।
মাহমুদ দারবিশ কেবল ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি নন, তিনি আরববিশ্বেরও জাতীয় মর্যাদাবান কবি। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিপুল সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মূর্ত হয়ে উঠেছেন দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার আকাক্সক্ষার প্রতীক হিসেবে। কাব্যপ্রতিভার স্বর্ণচূড়ায় তাঁর পরিচিতি ছড়ানো সমগ্র আরবে ও বিশ্বব্যাপী।
মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তিনি তাঁর নিজের এবং স্বজাতির আত্মপরিচয়ের সংকট দ্বারা সংজ্ঞায়িত ও প্রতীকায়িত করেছেন। তিনি তাঁর নির্বাসনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিতার ভাষায় বলেন, ‘অনুপস্থিতি... আমি এসে পড়েছি অনুপস্থিতির কঠিন বাস্তবাতবার শূন্য বাড়িতে।’
যখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন-তিনি কে? তখন তিনি বলেন, ‘আমি এখনো জানি না, আসলে আমি কে।’ তাঁর উত্তরকে অন্যের অনুধাবনের জন্য তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেন, ‘সম্ভবত আমার মতো আপনারও কোনো ঠিকানা নেই।’
তারপর সেই মানুষটির দুর্দশা ফুটে ওঠে আরও একরাশ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে :
‘সেই মানুষের কী দাম আছে,
যার কোনো স্বদেশভূমি নেই,
নেই কোনো পতাকা, Ñনেই কোনো ঠিকানা।
তুমি বলো, এ রকম মানুষের কী মূল্য আছে?’
ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
নিজের ফেলে যাওয়া জন্মভূমির সন্তান দারবিশ ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। ১৯৬৯ সালে ইসরাইলি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে মাহমুদ দারবিশ বলেন :
‘সেই ভয়ংকর ভয়াল একটি রাত সবাইকে শরণার্থী বানিয়ে দেয়। লেবাননে আমি যেমন উদ্বাস্তু তথা শরণার্থী ছিলাম, তেমনি আমার মাতৃভূমি ফিলিস্তিনেও আমি শরণার্থী হয়ে আছি।’
কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তিনি জানান, ইসরাইল নামক সেই রাষ্ট্রের প্রথম আদমশুমারিতে যেসব ফিলিস্তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়নি, নবগঠিত ইসরাইলি সরকার তাদেরকে কোনো পরিচয়পত্র দেয়নি। তাদের চিহ্নিত করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। ফলে তাঁর মতো অজস্র ফিলিস্তিনি নিজ জন্মভূমিতে হয়েছিলেন অবৈধ অভিবাসী।
নিজের আত্মপরিচয় গোপন করে লেবানন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ‘দাইরুল আছাদ’ নামক এলাকায়। সেখানে ইসরাইলি সরকারের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অবৈধ অভিবাসী। তিনি জানতেন যে ধরা পড়লে অবশ্যই তাঁকে সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন ‘কাফার ইয়াসিফ’ নামক গ্রামের একটি স্কুলে।
মাধ্যমিক শিক্ষা নেওয়ার পরই তিনি জড়িয়ে পড়েন নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায়। জীবন হয়ে ওঠে সাহিত্য ও সংস্কৃতিধর্মী। উদ্দেশ্য, কাব্যরচনা এবং কবিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়াই করা।
সত্যিকার অর্থে দারবিশ তখন নানা রকম বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রাম করার পথ খুঁজছিলেন। এ সময় তিনি ইসরাইলি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। অচিরেই কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি সবার প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁকেই পার্টির নিজস্ব মুখপত্র পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন।
পর্যায়ক্রমে ফিলিস্তিনিদের মুক্তিসংগ্রামের একটি শক্তিশালী অস্ত্র ও হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতা। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ‘আমছিয়া’ বা সান্ধ্যকালীন কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানসমূহে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন, যা ফিলিস্তিনিদের দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ অবস্থায় ইসরাইলি সরকার শঙ্কিত হয় এবং তার আমছিয়াগুলোর (কবিতাপাঠ) ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই সময় ইসরাইলি সৈন্যরা তাঁকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত গৃহবন্দী করে রাখত। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ইসরাইলে দারবিশের রাজনৈতিক তৎপরতা সহজ ও নির্বিঘ্ন হয়নি।
ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার দায়ে ১৯৬১, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৭ সালে তিনি তিনবার জেল খাটেন। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে চলে যান। এই সময়ের মধ্যে মাহমুদ দারবিশ কবি হিসেবে বিখ্যাত ও খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।
১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ ‘আবিরুনা ফি কালামিন আবিরিন’ ব্যাপক সাড়া জুুগিয়েছিল। এই সময় মাহমুদ দারবিশ ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হন এবং ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের দলে যোগদান করেন। এই রাজনৈতিক সংগঠনে তিনি দীর্ঘদিন ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফিলিস্তিনি সরকার গঠনের সময় আরাফাত তাঁকে ফিলিস্তিনের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু মাহমুদ দারবিশ তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার একমাত্র আকাক্সক্ষা বারুদের ধোঁয়ামুক্ত বাতাসে স্বাধীন ফিলিস্তিনে বসে কাব্যরচনা করা।’
অবশেষে ১৯৯৩ সালে ‘অসলো চুক্তির’ পর তিনি ক্ষুব্ধ হন, দল থেকে বের হয়ে যান। তারপর তিনি আরাফাতের দলের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি। তিনি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, চুক্তিটি ইসরাইলের সঙ্গে আপসকামী। এই চুক্তিতে ইনসাফ নেই, যেখানে ফিলিস্তিনি হিসেবে পরিচয়ের ন্যূনতম অনুভূতি এবং তার ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই চুক্তি ফিলিস্তিনিদের একটি যাযাবর জাতিতে পরিণত করবে। কিন্তু তিনি ইয়াসির আরাফাতকেই বেশি ভালবাসতেন। আরাফাতের মৃত্যুর পর একটি সাক্ষাৎকারে মাহমুদ দারবিশ বলেছিলেন, ‘পৃথিবীর মানুষের কানে যারা ফিলিস্তিন শব্দটি তুলেছেন ইয়াসির আরাফাত তাঁদের অন্যতম। আরাফাত তাঁর জীবনকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আরাফাত কখনো নিজের স্বার্থে, নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চাননি। সম্পূর্ণ জীবন-যৌবন ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থেই দান করে গেছেন। আমি চাই, আমার অনুভব ও স্মৃতিতে আরাফাতের সেই সব চিত্র জেগে থাকুক। আমরা তাঁকে খুব মিস করি। কিন্তু অন্য কোনো আরাফাত চাই না।’
নানা দেশ ঘুরে ১৯৯৪ সালে মাহমুদ দারবিশ অবশেষে ফিলিস্তিনের রামাল্লায় ফিরে আসেন। সেখানে ইসরাইলি সৈন্যরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রকাশ থাকে যে, সেই দীর্ঘ অবরোধকালে মাহমুদ দারবিশ ইসরাইলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং তাঁর ভাষা ও কবিতা দিয়ে বিরামহীনভাবে নিরন্তর লিখেছেন। কবিতার শব্দঝংকারের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত রেখেছেন। ২০০২ সালের মার্চে আরব এবং বিশ্বের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের একটি দল গৃহবন্দী কবি মাহমুদ দারবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রামাল্লায় গিয়েছিলেন। কবিতা প্রসঙ্গে এবং নিজের জীবনের প্রতিবন্ধকতা ও কঠিনতম সময় নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওরা তা চায়নি; অথচ আমি হয়েছি তা-ই, যেটি আমি হতে চেয়েছি। আমি নির্দ্বিধায় বলি-এটাই আমার স্বাধীনতা।’
সাহিত্যকর্ম
কবি মাহমুদ দারবিশ ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মাঠে ছিলেন। তবে তিনি লড়েছেন ভাষা, সাহিত্য ও আধুনিক ধারার কবিতার প্রচলন ঘটিয়ে। এই সময় দারবিশের কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁর কবিতায় আরবি কাব্যভুবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে রচিত কবিতাসমূহে যেসব কাব্যিক জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা ছিল, তা লাঘব করা হয়। সব পাঠকের উপযোগী, সহজ ও সাবলীলতায় কাব্যরচনা করেন। তিনি দেখতে পান, তাঁর আগেকার কবিতা সাধারণ মানুষ ও যোদ্ধারা বুঝতে পারে না। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন সহজ ও সরল ভাষায়; যা সহজেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। আত্মপ্রত্যয়ী চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে পারেন সকল পর্যায়ের মুক্তিকামী সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা। এই সংকলনের চৌদ্দটি কবিতার তেরোটিই এই সময়, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থাকাকালীন।
মাহমুদ দারবিশ শৈশবেই কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে তাঁর মনন-চেতনায় কবিতাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। স্কুলজীবনে তিনি সিলেবাসের আরবি কবিতা এবং অন্যদের কবিতার আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেন। স্কুলজীবনে প্রথম কবিতা পাঠ করেন নতুন ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যাপন অনুষ্ঠানে। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে দারবিশ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সেখানেই জীবনের প্রথম বারের মতো আমি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার যে কবিতা পাঠ করি, সেটি ছিল একজন ইহুদি বালকের প্রতি আরেকজন দুর্দশাগ্রস্ত ফিলিস্তিনি বালকের আর্তনাদপূর্ণ অভিব্যক্ত আহ্বান।’
মাহমুদ দারবিশের কবিতায় যেমন দ্রোহ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংক্ষুব্ধতা আছে; তেমনি তিনি প্রচুর প্রেম-বিরহ, রোমান্টিক ও প্রেমের কবিতা
লিখেছেন। যেমন তাঁর রোমান্টিক কবিতায় উঠে আসে :
‘তোমার ভালোবাসাকে যখন হৃদয়ে ধারণ করি; তারপর প্রবাহিত করে দিই আমার শিরা-উপশিরায়।’
‘তোমার সুগন্ধির প্রতি দুর্বলতাহেতু; তোমার গোপনীয় বিষয়গুলো সর্পদষ্ট-ক্ষতের মতো খুঁজে পাই/ মাঝে মাঝে শরতের উদাসী বাতাসে তোমার চুলকে তাঁবু বলে আমার ভুল হয়ে যায়।’
রোমান্টিক প্রেমানুভূতি নিয়ে ব্যক্ত করেন, ‘প্রেমিকা যখন আমায় জিজ্ঞেস করে, Ñআকাশের সাথে আমার পার্থক্যটি কীভাবে তুমি দেখো? আমি তাকে বলি; পার্থক্য এটাই যে, তুমি যখন হাসো/ আমি তখন আকাশের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাই।’
মাহমুদ দারবিশের সাহিত্যাদর্শ ও কবিতার একটি নিজস্ব স্টাইল লক্ষণীয়। তিনি মনে করতেন, আরবি ভাষাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। যার রয়েছে সহস্র বছরের ঐতিহ্য। তিনি সর্বদা সাহিত্যকর্মে গৌরবান্বিত আরবি ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে গৌরববোধ করতেন।
অসংখ্য কবিতায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলি আগ্রাসন ও অমানবিক আচরণে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে কাব্য রচনা করেন। নিজের জীবনকাব্য সম্পর্কে তিনি বলেন :
‘এই রাস্তায় আমার সঙ্গে যদি অন্য কেউ থাকত; তাহলে আমি আমার আবেগ ও অনুভূতিকে বাক্সবন্দী করে রাখতাম। যদি তা হতো; আমার কবিতা হয়ে উঠত বিমূর্ত ও জলের মতো স্বচ্ছ।’
স্বাধীনতার জন্য আকুতিভরা তাঁর অনেক কবিতা আছে। তাঁর মধ্যে নিজের স্বদেশভূমিকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করার দীপ্ত প্রয়াস ছিল। স্বাধীনতার যোজন দূরত্বকে তিনি সর্বদাই বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছেন। স্বাধীনতার সৌন্দর্যের প্রত্যাশায় দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন।
কবিতায় প্রবল দেশপ্রেম ও প্রেমিকার সৌন্দর্যকে তিনি চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেন, ‘চাঁদ অনেক সুন্দর, প্রধান কারণ হলো তার দূরত্ব।’
মাহমুদ দারবিশের ধর্মবোধ ছিল, আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাস ছিল। আমাদের জীবন হওয়া উচিত আমাদের ইচ্ছের মতো। ছোট্ট একটা জীবন দিয়ে ঈশ্বর বলেন, ‘এমনভাবে যাপন করো, যেন পুনরুত্থানের (কিয়ামতের) দিনে সম্মানের সঙ্গে উঠতে পারো।’
নিজের মাতৃভূমি নিয়ে অনেক কবিতায় তাঁর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন ‘জেরুজালেম’ নামক দীর্ঘ কবিতায় তিনি বলেন :
‘কোনো স্মৃতি ছাড়াই একটি প্রাচীন দেয়ালকে
আড়াল করে,
যুগ যুগ ধরে আমি হেঁটে যাই জেরুজালেমের দিকে...
আমি হাঁটি অন্য কেউ হয়ে। নিভৃতে একটি ঐশ্বরিক সাদা গোলাপের ক্ষত আমার হাত দুটো জোড়া কবুতর হয়ে ক্রুশের ওপর ঝুলে থাকেÑঅনন্তকাল এই পৃথিবীর ভার বয়ে...
আমি তখন আর হাঁটি নাÑআমি ভেসে বেড়াই অন্য কেউ হয়ে
বহুরূপে আমার প্রকাশ ঘটে... আমার কোনো দেশ নেই, কাল নেই।
তাহলে আমি কে-? আসলে আমি কেউ নই, একটি অনাহূত উপস্থিতি মাত্র। কিন্তু আমি যখন নিজেকে নিয়ে একাকী ভাবি,
তখন বুঝতে পারি
নবী মুহাম্মদ যে ভাষায় কথা বলতেন; সেটি আমার ভাষা, আমারই মাতৃভাষা... তুমি আর কী জানতে চাইবে? অতঃপর, একজন নারী সৈনিক চিৎকার করে বলল, তুমি আবার এসেছ? তোমাকে না হত্যা করলাম? আমি বললাম,
তুমি আমাকে খুন করেছিলে... এবং আমি ভুলে গেছি,
আসলে,
তোমার মতো, আমি মৃত্যুকে মনে রাখিনি।’
নিজের জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা বুকে নিয়ে মাহমুদ দারবিশ লেখেন :
‘হে আমার জন্মভূমি!
তোমার কোলে জন্মেই দেখেছি ক্ষত-বিক্ষত
হয়ে আছ তুমি
তোমার ক্ষেতের ফসল ও বৃক্ষের কত ফল খেয়েছি
আমি সাক্ষী হয়েছি তোমার প্রতিটি সকালের
হে নিস্তেজ বন্দী ঈগল,
হে আকাক্সিক্ষত মৃত্যু হে...
তোমার জ্বলজ্বলে ক্ষত ডুবে আছে আমারই চোখের গভীরে...’
(ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশের ৯ আগস্ট মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধটি নিবেদিত)
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক