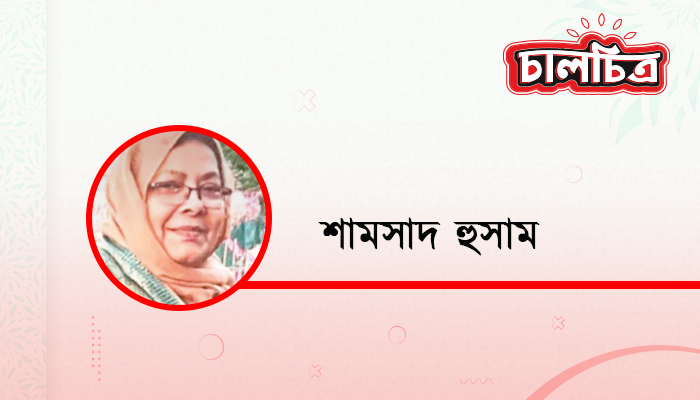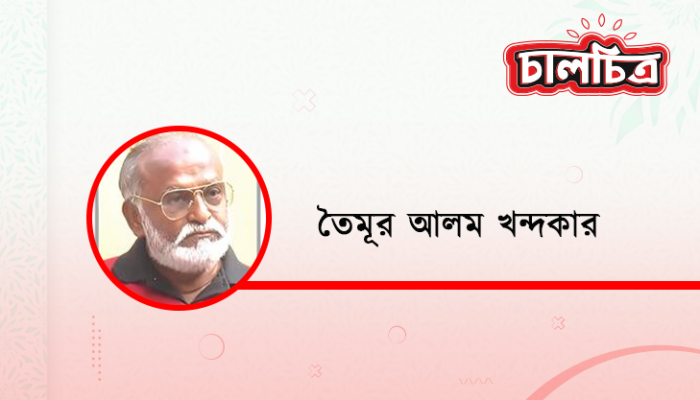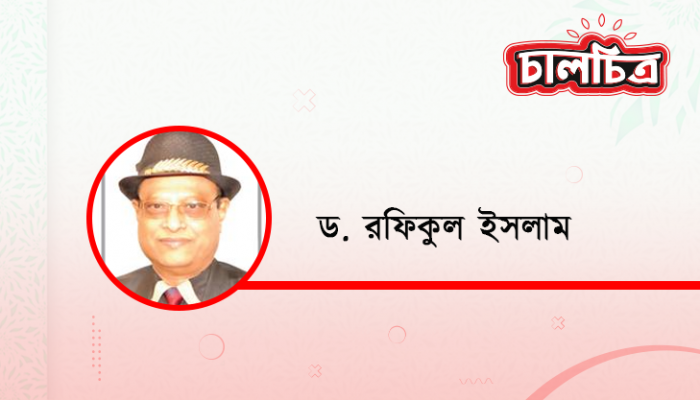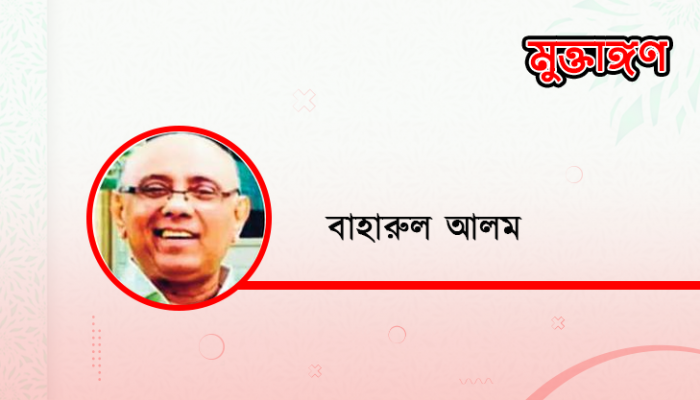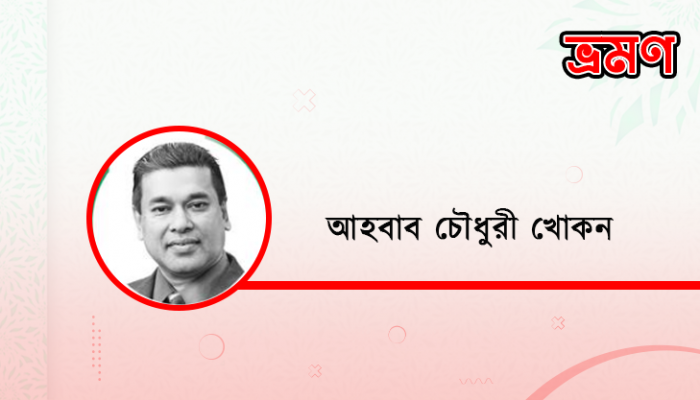বাড়ির কাছে আরশি নগর, সেথায় এক পড়শি বসত করে-এই এক গান কতভাবে যে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, তার কোনো হিসাব নেই। সারা দিন পড়ার টেবিলে মুখ গুঁজে থাকা এক মানুষ এই আমারও মাঝেমধ্যে টেবিল ছেড়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়ার তাগিদ থেকেই একদিন ঘর ছেড়ে অচেনা নগরের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিলাম। একবার নয়, দু-দুবারের মতো। আসামের করিমগঞ্জ নগর-আয়তনের দিক দিয়ে ছোট হলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার ওজন নেহাত কম নয়। এই করিমগঞ্জের প্রতি অন্য ধরনের টান থেকেই সেই মেঠো পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। প্রথমবার গেলাম ২০০৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার গেলাম ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে। শেষবার গিয়েছিলাম ‘ভাষা সংস্কৃতি আকাদেমি অসম’ এর আমন্ত্রণে তিন দিনব্যাপী তাদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে। এই দুবার আসাম ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল শিলচরের জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক মিলন উদ্দিন লস্কর ভাইয়ের সৌজন্যে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় এক সাহিত্য সংগঠনের নাম ‘নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র’। ওই সংগঠনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিলচরে। সেই সুবাদে আসাম অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে শুধু সিলেট নয়, ঢাকার জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্যিকদের মধ্যেও একটা আন্তরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। নন্দিনীর প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক সুলতানা রাজিয়া তার অনুগামী লেখকদের নিয়ে বার কয়েক শিলচর ঘুরে এসেছেন এবং আসামের বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকও ঘুরে গেছেন সিলেটে। সেই কারণে শিলচরের সাহিত্য পরিমণ্ডল সম্পর্কে আমাদেরও একটা কৌতূহল রয়েছে, বিশেষ করে একসময় আমাদের সিলেট অঞ্চলটিও ছিল আসামের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরের একটা অংশ হয়েই। সে কারণেও ওই অঞ্চলের প্রতি অন্য ধরনের একটা টান অনুভব করি।
ওই করিমগঞ্জ শহরে একসময় আমার পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল। আমার প্রপিতামহ আব্দুল আহাদ চৌধুরী ব্রিটিশ শাসনামলে করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। শুনেছি শহরে অনেকগুলো বাড়ি ছিল আমার পরিবারের। সাতচল্লিশের দেশভাগে আমার পরিবারের ওপর একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছিল, অন্য আর সবার মতো তারাও এক দিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেরত এসেছিলেন বাহাদুরপুরে। আমার আপন নানার বাড়িও ছিল করিমগঞ্জ অঞ্চলের আলীনগর গ্রামে। ২০০৩ সালে প্রথম যেবার করিমগঞ্জের শিলচর ঘুরে এলাম, ফেরত আসার পরে আমার মা অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কী করে আলীনগর যাওয়ার কথা একবারের জন্যও মনে হলো না আমার? তাহলে অন্তত আমার চোখ দিয়ে হলেও নিজের মাতৃভূমির খবরটা জানতে পারতেন উনি। আসলে ওই হলো আমার বাড়ির কাছের আরশি নগর! অচেনা এই নগরটি আপনার মতো করে কাছের হয়ে উঠল একসময়। কত প্রিয়জনের বসবাস ওই অঞ্চলেÑসদ্য প্রয়াত ইমাদউদ্দিন বুলবুল ভাই, কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য, কবি লেখক অনুরূপা বিশ্বাস, লেখক চন্দ্রিমা দি, প্রয়াত তুষার কান্তি নাথ দাদা, তার স্ত্রী স্মৃতিকণা নাথ, জাহিদ তফাদার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রেজাউল হোসেন খানÑকতজনের কথা বলব? যাদের নাম লিখলাম, তাদের ভেতরেই তো কতজন এখন ‘নাই’ এর তালিকায়। কিন্তু সেই দুবারের ভ্রমণ আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিকে এতটাই সমৃদ্ধ করেছিল, আমি তখন এসব মানুষের একান্তই আপনজন হয়ে উঠলাম। মিলন উদ্দিন ভাই আমাকে একদিন ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকায় দাওয়াত দিলেন। যথারীতি একপর্যায়ে শিলচর প্রেসক্লাবের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও হলো। আমি নিজে একজন সংবাদকর্মী, সিলেটের প্রাচীনতম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক (পরে দৈনিক) যুগভেরীর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম বিধায় শিলচর প্রেসক্লাবের দাওয়াতটা আমার কাছে একটা সম্মানীয় বিষয় বলেই গণ্য হয়েছিল।
করিমগঞ্জ ও শিলচর পাশাপাশি শহর হলেও শিলচরের সার্বিক অবস্থা করিমগঞ্জের তুলনায় অনেকটাই উন্নত। ওই সময়ে এক অনন্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল আসামের বাংলাভাষী মানুষেরা, যখন সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তির পরে আসাম অঞ্চলে পাশের দেশগুলো থেকে প্রচুর বাঙালি অভিবাসী সম্প্রদায়ের ঢল নামে। সেই কারণকে সামনে রেখে একসময় ‘বাঙ্গাল খেদাও’ আন্দোলনটা আসামজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়ালে তার উত্তরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভেতরে রাষ্ট্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে অসমীয় ভাষার পাশাপাশি বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তারা গড়ে তুলেছিলেন জোরালোভাবে। যে আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিলেন ১১ জন বঙ্গসন্তান। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ওই রক্তাক্ত আন্দোলনের কারণে শেষ পর্যন্ত আসাম সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে রাজি হয়েছিল।
আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই একষট্টি সালের ১৯ মের অভ্যুদয়। ওই এক কারণেও শিলচরের প্রতি আমার অন্য ধরনের আবেগ কাজ করেছিল। ওই ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী দাদা পরিতোষ পাল চৌধুরীর অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর শিলচরের গান্ধীবাগের ঈশান কোণে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ বইমেলায়ও যাওয়ার সুযোগ হলো আমার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথিদের সঙ্গে আমাকেও মঞ্চে ডাকলেন তারা। বেশ রাত করে হোটেলে ফিরেছি। সকালে ঘুম ভাঙল দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে। দরজা খুলতেই সৌম্যদর্শন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে হলো। অনুমান করছি, কিন্তু নিশ্চিত নই। তার আগেই হাত তুলে সালাম দিলেন তিনি। খুব মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি তৈমুর রাজা চৌধুরী, ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকার সম্পাদক। কোথায় বসাই? অগোছালো বিছানা। মাত্র ঘুম ভেঙে উঠেছি। সকাল আটটা বাজছে তখন। কিন্তু তিনি বিনয় নিয়ে বললেন, আজ বসব না, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলাম আজ সন্ধ্যার সময় আমার পত্রিকা অফিসে আপনাকে আসতে হবে। সামান্য আয়োজন করেছি। পরিচয় হবে সবার সাথে আপনারও। একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নিজে এসেছেন আমাকে দাওয়াত দিতে? সীমাহীন কুণ্ঠা আমার, মনে মনে বলছি। এতটা বিনয় না দেখালেই পারতেন। বললাম, কিন্তু মিলন উদ্দিন লস্কর ভাই তো আগেই বলে রেখেছেন, আপনি এত সকালে এসেছেন কষ্ট করে, খুশি হতাম যদি আমাদের সাথে এক কাপ চা খেয়ে যেতেন। চা খেতে রাজি হলেন না তৈমুর রাজা চৌধুরী। সন্ধ্যার সময় তার পত্রিকা অফিসে যাওয়ার জন্য আবারও অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন।
সন্ধ্যায় যোগ দিলাম ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত সুধী সমাবেশে। বেশ বড় মাপের আয়োজন ছিল। সংবাদকর্মীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। একপর্যায়ে তারা দাবি জানালেন, যেন প্রতি মাসে একটা হলেও ‘সিলেটের চিঠি’ শিরোনামে লেখা দিই। দেশে ফেরত এসে ওয়াদাটা পূরণের চেষ্টা করেছি। হয়তো রেগুলার লেখা দেওয়া সম্ভব হয়নি; কিন্তু বাদ দিইনি একেবারে। কিন্তু তৈমুর রাজা চৌধুরী রাজার মতো কাজ করলেন, তিনি তার দৈনিক পত্রিকাটা প্রতিদিন ডাক মারফত আমাকে পাঠাতে শুরু করলেন। প্রায় দুই বছর বিনা মূল্যে পাঠালেন। তারপর নিউইয়র্কে চলে আসায় বন্ধ হয়েছিল। এ যে কত বড় স্বীকৃতি! কত বড় উদারতা! মানুষ নিজেকে কত বড় মাপের জায়গায় তুলে ধরলে এ ধরনের কাজ করতে পারে-তার প্রমাণ দিলেন তিনি। একজন মৃদুভাষী মানুষ হিসেবে পরিচিত মানুষটি সর্বজনীন মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনের চিন্তা ও চেতনাকে ব্যয় করে দিয়ে হয়ে উঠেছেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র, ভালোবাসার পাত্র। আগামী ২৬ মে তিনি ৭৩ বছরে পা রাখবেন। সেই দিনকে স্মরণে রেখেই বলতে ইচ্ছে করছে : ‘এই দিন শুধু দিন নয়, আরও দিন আছে-’। -নিউইয়র্ক




 শামসাদ হুসাম
শামসাদ হুসাম