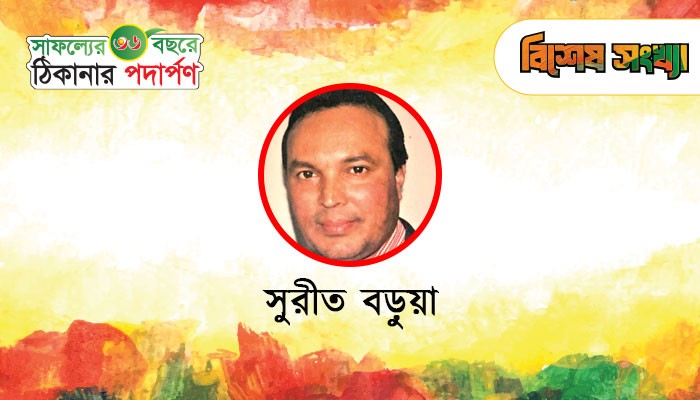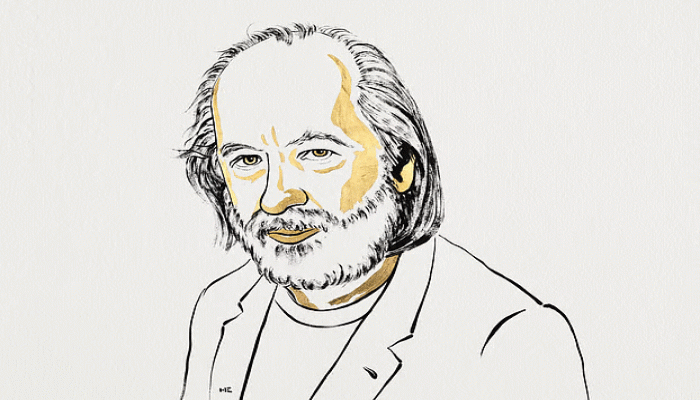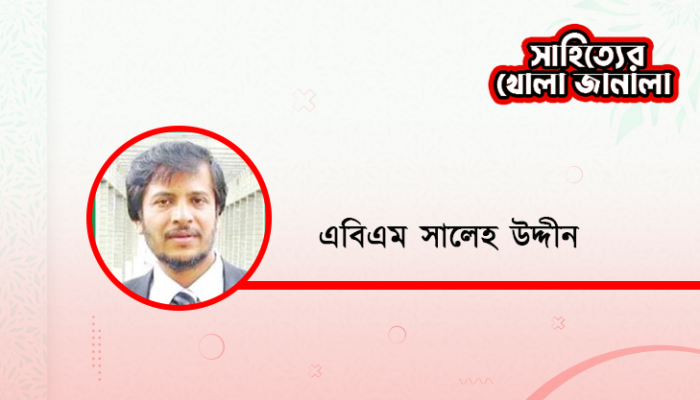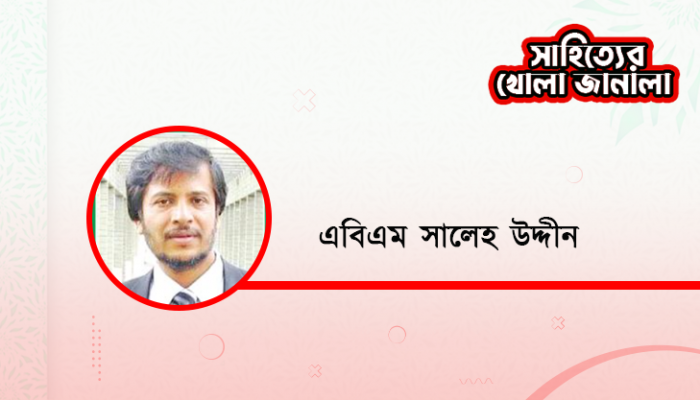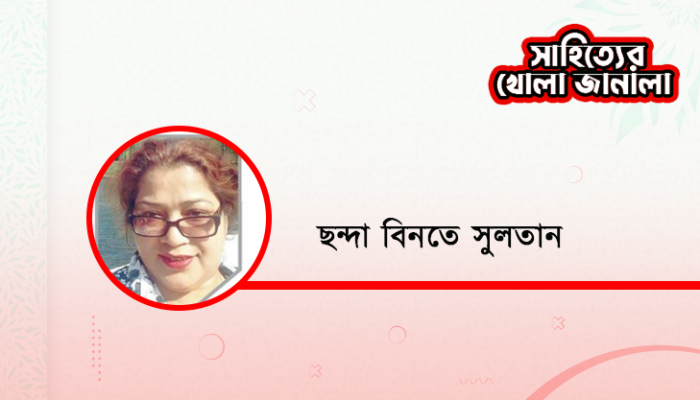প্রিয় বন্ধু বারি আলিগের উৎসাহে সাংবাদিকতা শুরু করলেও প্রথাগত জীবিকা অর্জন করা মান্টোর পক্ষে ছিল অসম্ভব। অস্থিরচেতন এই মানুষটি ছিলেন নিঃশঙ্ক, নির্ভীক। জাগতিক নিয়মের দাসত্বে আবদ্ধ না থেকে সৃষ্টির উন্মাদনায় নিজেকে সমর্পণ করাই ছিল জীবনের ব্রত। তাঁর সাহিত্য বাস্তববাদী হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্মুখী বা আত্মকেন্দ্রিক নয়, বরং সাহিত্যকে ছাপিয়ে গিয়ে জীবনকে ছুঁতে চাওয়াই ছিল প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ বুঝতে হলে ফিরে যেতে হয় তাঁর অবিস্মরণীয় ছোটগল্পগুলোতে। একদিকে গঠনশৈলী, অন্যদিকে চরিত্রায়ণের আশ্চর্য ক্ষমতা, এই দুইয়ের সহাবস্থানে রচনাগুলো আজও প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব চেতনের গভীরে প্রোত্থিত। এসবের সঙ্গে যোগ করতে হয় মান্টোর রসিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যেন সমাজের অন্ধকার অলিন্দে বিচরণকারী এক দুর্দমনীয় অভিযাত্রী, ঘাত-প্রতিঘাত, বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে সদর্পে এগিয়ে চলা এক গল্পনেশা পর্যটক। সমাজের ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত মানুষের হাহাকার-বঞ্চনার করুণ ইতিহাস মূর্ত হয়ে ধরা দেয় মান্টোর গল্প বলার ভাঁজে ভাঁজে। তাঁর অবিস্মরণীয় ছোটগল্পের মধ্যে ‘ঠান্ডা গোস্ত’, ‘কালো সালোয়ার’, ‘বাবু গোপীনাথ’, ‘শরিফন’, ‘তোবা টেক সিং’, ‘খোল দো’, ‘নয়া কানুন’, ‘বু’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মান্টো ছিলেন ঘোর সংসারবিমুখ, প্রকৃত অর্থেই তাঁর ছিল অনুসন্ধানী দৃষ্টি। নিষিদ্ধ পল্লিতে ছিল অবাধ আনাগোনা, সেখানকার বর্ণময় চরিত্ররাই বারবার এসে পড়েছে তাঁর রচনায়। অপরদিকে সুরাপায়ীদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। মৃত্যুশয্যায় জলের বদলে চেয়েছিলেন কয়েক ফোঁটা হুইস্কি। কিছুদিন পান করতে না পারলে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তেন, সাহিত্যসৃষ্টি হতো ব্যাহত। লেখার আগে মগজের খোরাক হিসেবে মান্টোর কাছে মদ্যপান করা ছিল অপরিহার্য।
এই আত্মঘাতী নেশার একটি অন্য সহজবোধ্য কারণও হয়তো ছিল। ১৯৪৭-পূর্ব অবিভক্ত ভারতে মান্টোর কদর ছিল ক্রমবর্ধমান, স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পর তিনিই হয়ে গেলেন ব্রাত্য। প্রথমে ফিলিস্তান স্টুডিওওয়ালাদের সঙ্গে মনোমালিন্য, তারপর অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় কাজ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে মান্টো চলে যান পাকিস্তানে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন বুকভরা অভিমান আর তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনার রসদ।
মান্টোর মতো ক্ষুরধার ধীশক্তিসম্পন্ন লেখকের রচনাকে একমাত্রিক বিবরণে ফেলতে চাইলে ঠকে যেতে হয়। কারণ একই পরিসরে তাঁর রচনায় অধিষ্ঠান করে নানাবিধ স্তর। ‘খোল দো’ বা ‘ঠান্ডা গোস্ত’, বিশেষত ‘গোস্ত’ কথাটির মধ্যে নিহিত আছে অনেকগুলো চিত্রকল্প- রাস্তার ধারে ঝুলন্ত খণ্ড-বিখণ্ড পশুদেহ, ‘ঈশ্বর সিং’ ভোগ করার উদ্দেশ্যে লুট করে নিয়ে যাওয়া মেয়েটির নির্জীব হিমশীতল দেহ এবং পরে স্ত্রী কুলবন্ত কাউরের সান্নিধ্যে এসে যৌন চাহিদার উষ্ণতা হারিয়ে নিজের মধ্যে সৃষ্ট এক অপরাধবোধের গ্লানি- এই দুইয়ের মধ্যে অনুশোচনা ও বিবেকের তাড়ানা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ‘খোল দো’ গল্পে একাধারে রাষ্ট্রনীতি, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, যৌনতা, প্রেম, ভয় ও ঘৃণার মতো বিচিত্র ও বহুমুখী আবেগ চলে আসে। ‘কালো সালোয়ারে’ও হেনরির ‘দ্য গিফট’ কাহিনির ছোঁয়া আছে। তবে মান্টোর গল্পের প্রধান চরিত্ররা-নারী ও পুরুষ উভয়ই যেহেতু শরীর-ব্যবসায় সিদ্ধহস্ত, তাই এটি নির্ভেজাল প্রেমের উপাখ্যান নয়, এটি অন্য রকম এক জটিল মানবিক চাহিদার গল্প। দেশভাগ-প্রসূত হিংসা ও বর্বরতা যে মানুষের গভীর অন্ধকার প্রদেশ থেকেই উঠে আসে, মান্টো তা জানেন। তাই তাঁর গল্পে কোনো আশাবাদ দেখা যায় না। ‘শরিফন’ গল্পের কাসেম, শত্রুপক্ষের হাতে তার নিহত কন্যা শরিফনকে নগ্ন অবস্থায় দেখে, এক হিন্দুকন্যা বিমলাকে যেভাবে হত্যা করে, তার পেছনে কোনো মতাদর্শ নেই, আছে শুধু অন্ধ প্রবৃত্তি আর প্রতিশোধস্পৃহা। রাজনৈতিক উন্মাদনার সময়ে মানুষের প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ কেমন করে ফেটে পড়ে, মান্টো দেশভাগের গল্পে তারই নানা রকম ছবি লেখার বৈচিত্র্যশৈলীতে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।
একদিকে বহির্বিশ্বে চলতে থাকা তাণ্ডবলীলা, অন্যদিকে মান্টোর দৃষ্টি ঘনবদ্ধ হয় অন্তঃপুরের গোপন পারিবারিক নাটকের ওপর। বয়ঃসন্ধির কথা চলে আসে ‘ধুঁয়া’-তে, ‘বু’ গল্পের যুবকটির বিয়ের প্রথম রাতে মনে পড়ে যায় একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে উষ্ণ রাত্রি যাপনের কথা, সেই অপরিচিতার শরীরের পাগলপারা গন্ধের স্মৃতি বিছানায় শায়িতা সুন্দরী নববধূর আশা-আকাক্সক্ষাকে ম্লান করে দেয়।
মান্টোর বিখ্যাত গল্প ‘বু’ (গন্ধ) ১৯৪৪ সালে ‘অদব-এ-লতিফ’-এর বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক ‘প্রভাত’-এ লেখা হয়েছিল, এ ধরনের গল্প কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মন নোংরা করে দেয় এবং জনরুচিকে দূষিত করে। এমনকি পত্রিকার সম্পাদক মান্টোকে তিন বছর জেলবন্দী করার দাবি তোলেন। এই সময় ‘খোল দো’ গল্পকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান সরকার। এমনকি ‘নকুশ’ নামে যে পত্রিকা গল্পটি ছেপেছিল, সেটিকেও ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। এরপর ‘ঠান্ডা গোস্ত’ গল্পের কপালেও জুটল অশ্লীলতার অভিযোগ। এই সময় মান্টো ও তাঁর গল্প নিয়ে কেউ সুস্থির থাকতে পারছেন না, এমনকি ফয়েজের মতো কবিও নন। কারও চোখে মান্টো কমিউনিস্ট, কেউ তাঁকে মনে করেন প্রতিক্রিয়াশীল। একটি ঘটনা তো আরও আশ্চর্যের। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বোম্বে থেকে প্রকাশিত ‘কওমি জঙ্গ’-এর এক নিবন্ধে আলি সর্দার জাফরি ‘বু’ গল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরই সেই মুক্তমনা জাফরি সাহেব একই গল্পকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আক্রমণ করলেন। এর পেছনে কী দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল, তা জানা যায়নি। শুধু বুঝতে পারি, গল্পলেখক মান্টো দিনে দিনে অসহায় হয়ে পড়ছেন, তাঁর কোনো বর্ম নেই, যা দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়। আমলাদের দাবি, তাঁর গল্প পাকিস্তানের জাতীয় শান্তি বিঘ্নিত করছে। অন্যদিকে তাঁকে শুধু পাকিস্তান নয়, এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের শিরোপা দেওয়া হচ্ছে। এহেন চড়াই-উতরায়ের মধ্যে মান্টো ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠেন।
অপরদিকে বন্ধু-লেখক আহমদ নাদিম কাসিমিকে মান্টো লিখেছিলেন, ‘চিন্তার স্তরে আমি এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি, যেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, এই সব এখন অর্থহীন। যেখানে হয়তো কিছু বুঝতে পারছি, আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেক সময় মনে হয়, সারা পৃথিবী আমার হাতের তালুতে, আবার অনেক সময় নিজেকে এত ফালতু মনে হয়, যেন একটা পিঁপড়ে হাতির শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’
লেখকের অস্তিত্বের এই যে অনির্ণেয় অবস্থা এবং তা থেকে জন্ম নেয় যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা তার মর্মমূলকে অনুভব না করলে মান্টোর সাহিত্যকে আমরা নানা খোপে আটকে ফেলব। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মান্টো উর্দু ভাষার সাহিত্যে একজন নোমাড, একজন অভিবাসী, একজন জিপসি। এভাবেই তিনি তাঁর সমসাময়িক রাজিন্দর সিং, কৃষণ চন্দর, আহমদ নাদিম কাসিমি, ইসমত চুঘতাইদের থেকে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য সত্তায় অনন্য।
এসব জাল সরিয়ে আজ আমরা একজন পরিপূর্ণ মান্টো ও তাঁর গল্পের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। সাহিত্যের বিষয় কী? এই মৌলিক প্রশ্ন মান্টো তোলেন এবং উত্তরও দেন। মানুষের জীবনে দুটি আদি ও অকৃত্রিম ক্ষিদের সঙ্গে সাহিত্যের বিষয়কে জুড়ে দেন তিনি। ‘খাদ্য ও যৌনতা’। মান্টো মনে করেন, সব মানুষের দুটি মৌলিক কাজ ক্ষিদে এবং সেই ক্ষিদে থেকে জন্ম নেওয়া দুটি সম্পর্কের মধ্যে ধরা যায় খাদ্য আর মানুষ ও মানুষীর সম্পর্ক। মান্টো লেখেন, ‘যেসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত সমস্যা আজ আমাদের ঘিরে আছে, তাদের সবকিছুর গভীরে রয়ে গেছে এই দুই “ক্ষিদে”। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের মুখের ওপর থেকে ওড়না সরালে মৃতদেহের পাহাড়ের পেছনে আসলে জাতীয়তাবাদের “ক্ষিদে” ছাড়া আর কিছুই নেই।’ মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে এভাবেই দেশ-কাল-ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দেন মান্টো।
তিনি মহিমাকীর্তনে বিশ্বাস করতেন না। মানুষ মহান- এমন কোনো ধারণাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যে তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর, এই উপলব্ধি মান্টোর লেখা আড়াইশর বেশি গল্পে ছড়িয়ে আছে। মানুষের আত্মোপলব্ধিবোধের সঙ্গে মহিমার কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে মান্টোর মতো লেখককে সব মতাদর্শের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। কেন গল্প লেখেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর প্রতিরোধহীন উচ্চারণ, ‘লেখকের অনুভূতি যখন আহত হয়, তখনই সে কলম তুলে নেয়। লেখকের মনন-চেতনার ক্ষত থেকে একেকটি গল্পের জন্ম। যে মহিলা সারা দিন শস্য পিষে রাতে ভালোভাবে ঘুমোতে পারে, সে গল্পের নায়িকা হতে পারে না। বরং যে বেশ্যা সারা রাত জেগে থাকে, আর দিনে ঘুমানোর সময় হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে, তার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে তারই বয়স্ক প্রতিমূর্তি, সেই “রেন্ডি”ই মান্টোর গল্পের নায়িকা।’
এসব গল্প যেন অনেক উদ্্ভ্রান্ত আত্মার অনিশ্চিত যাত্রাপথের খণ্ডচিত্র। মান্টোর প্রায় সব গল্পের চরিত্রই তো পরিত্যক্ত পোড়খাওয়া মানুষ-মানুষী। তারা কেউ এই সমাজের মূল স্রোতে নেই। হয় তারা দেশচ্যুত, উদ্বাস্তু নয়তো বেশ্যা, দালাল আর এই আদিম মাংস-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তথাকথিত মুখোশধারী ভদ্র মানুষজন। প্রশ্ন ওঠে, তাঁর গল্পে এত বেশ্যা কেন? মাহমুদাবাদের রাজা সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে মান্টো বলেন, ‘রেন্ডিদের কথা বলা যদি অশ্লীল হয়, তবে তাদের অস্তিত্বও অশ্লীল। তাদের কথা বলা যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে তাদের পোশাকও নিষিদ্ধ করা উচিত। রেন্ডিদের মুছে দিন, তাদের কথাও আমার কলমে আর আসবে না।’ সমাজের ভাগ্যবিড়ম্বিত নিম্নশ্রেণির মানুষ এবং বেশ্যাদের নিয়ে কোনো গল্পেই মান্টো ভাবাবেগে ডুবে যান না, অন্যদিকে তাদের ওপর মহত্ত্ব আরোপও করেন না। শুধু চিত্রকরের ছবির মতো কালি-কলমের আঁচড়ে তাদের জীবনের বঞ্চনার কথা, মর্মাঘাতের কথা পাঠকের কাছে তুলে ধরেন।
মনে হয় তাঁর সৃষ্ট গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন। তাদের যাপিত জীবনের চালচিত্রে, সংলাপে তিনি মুখর হয়ে ওঠেন। একইভাবে কথা বলেন এই উপমহাদেশের ভাগ্যহত বৃন্তচ্যুত, গৃহচ্যুত মানুষদের সঙ্গেও। আর অভিযোগের পর অভিযোগ উঠতে থাকে মান্টোর বিরুদ্ধে- মান্টো সবকিছু নগ্ন করে দিচ্ছেন। মান্টোর উত্তর, ‘এই সমাজের চোলি আমি কেন খুলতে যাব, সে তো আগের মতোই নগ্ন। তবে আমি তা ঢাকতেও চাই না, কেননা কাজটা দর্জির, লেখকের নয়।’ মান্টোর গল্পগুলো আদতে সোমনাথ হোর-এর ‘ক্ষত’ সিরিজের সব ছবি। এসব ক্ষত আসলে মান্টো নামের একজন লেখকের আত্মার নানা মুহূর্তের আর্তনাদ। দেশভাগ-পরবর্তী প্রতিদিনের বাস্তবতা, যার ধারাবাহিকতা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক আতঙ্ক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ছাপিয়ে আমাদের আজকের চেতনায়ও সমানভাবে হানা দেয়। নিকট অতীতে রামুতে পোড়া বৌদ্ধ মন্দিরে ছাইয়ের মধ্যে স্মিত হাসির বুদ্ধ, গুজরাটের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা, পাকিস্তানের শিয়া মহল্লায় নির্বিচারে আগুন বা খ্রিষ্টানদের প্রার্থনার সময় গুলিবর্ষণ- এই সবকিছুর মধ্যে মান্টোর লেখনীশক্তি আমাদের বারবার সেই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানেই তিনি সার্থক রূপকার, এখানেই তিনি উর্দু সাহিত্যের একজন বিস্ময়কর ট্র্যাজিক হিরো। ভাগ্যবিড়ম্বিত মান্টো একসময় পাকিস্তানে চলে যান। সেখানেও মানসিক ও আর্থিকভাবে থিতু হতে পারেননি। নিদারুণ অর্থকষ্টে ভুগে পাকিস্তানের লাহোর শহরে ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই ক্ষণজন্মা লেখক মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা নিজের এপিটাফে বলে গেছেন, ‘এখানে সমাধিতলে শুয়ে আছে মান্টো আর তার বুকে সমাহিত হয়ে আছে গল্পবলার সব কৌশল আর রহস্য।’ -নিউইয়র্ক



 সুরীত বড়ুয়া
সুরীত বড়ুয়া