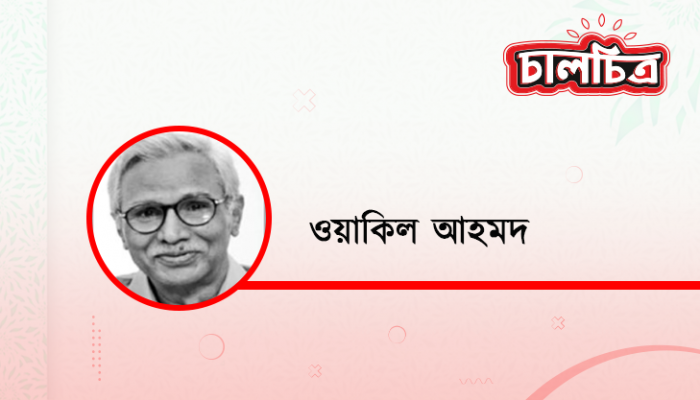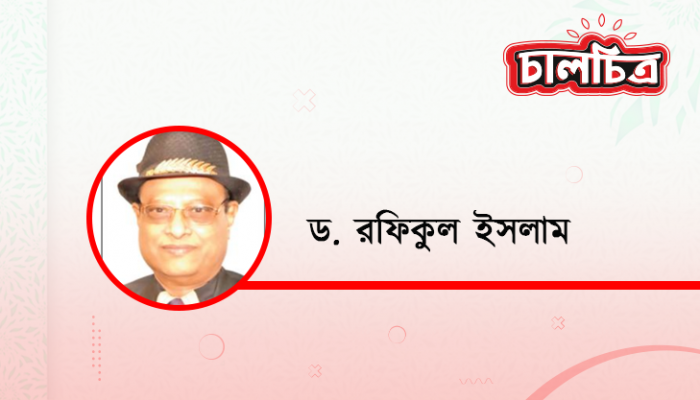(গত সংখ্যার পরের অংশ)
এক বীরাঙ্গনা নারীর উক্তি ছিল, ‘পাকিস্তানি সেনারা যখন আমাদের পেয়েছে, তখন আমরা রাজাকারদের উচ্ছিষ্ট।’ বাঙালির কুলাঙ্গারদের একাংশের নাম হলো ‘রাজাকার’। এই রাজাকার শব্দটি এসেছে আরবি শব্দভান্ডার থেকে, যার অর্থ ‘স্বেচ্ছাসেবী’। একইভাবে যুদ্ধের নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটি বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। যেমন আলবদর, আলশামস ইত্যাদি।
ওইসব বাহিনী গঠনের পেছনে জামায়াতের আমির (তৎকালীন) অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূমিকা ছিল মুখ্য। এ ছাড়া ছিলেন তৎকালীন ছাত্রসংঘের কর্ণধার মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং আব্দুল কাদের মোল্লা এবং এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজি।
তৎকালীন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ছাড়াও এসব বাহিনী গঠনের পেছনে তৎকালীন মুসলিম লীগপন্থী নেতাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখ করার মতো। এসব কিছুর পেছনে তখন একটাই উদ্দেশ্য কাজ করেছে, আর তা ছিল যেকোনো মূল্যে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করে দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৯৬ জন জামায়াত সদস্য এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে খুলনার আনসার ও ভিডিপি ক্যাম্পে সর্বপ্রথম ‘রাজাকার বাহিনী’ গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের মে মাসে। তার আগেই এপ্রিল মাসে জন্ম হয়েছিল আলবদর বাহিনীর। এই বাহিনীর কাজ ছিল যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাসদস্যদের সার্বিকভাবে সহায়তা দেওয়া।
রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে বদর বাহিনীর কিছুটা পার্থক্য ছিল। রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতাকারী হিসেবে চিহ্নিত হলেও বদর বাহিনীর লক্ষ্য ছিল-সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক হত্যার মাধ্যমে নিরীহ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া। বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তাদের প্রথম এবং প্রধান টার্গেট।
আধা সামরিক আরও একটি বাহিনীর নাম ছিল ‘আলশামস’। এ শব্দটাও এসেছে আরবি থেকে, যার অর্থ ‘সূর্য’। আলশামস বাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। মূলত আধা সামরিক এই তিনটি বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আর তা হলো যেকোনো মূল্যে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করা এবং এ জন্য পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়নে যা যা করা দরকার, নিষ্ঠার সঙ্গে তা সম্পন্ন করা।
রাজাকার বাহিনী প্রধান টার্গেট হিসেবে প্রথমেই দেশের সাধারণ নারীসমাজের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের হোলি উৎসব শুরু করেছিল। প্রথমে নিজেরা নারীর শরীর ভোগ করার পর সেই নারীকে দ্বিতীয়বারের মতো সেনা ক্যাম্পে পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে তুলে দিত তারা। সেনা ক্যাম্পে বন্দী সেসব নারীর মর্মান্তিক জীবনকাহিনি ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়।
সীমাহীন অত্যাচার শেষে ওইসব নির্যাতিত নারীর উলঙ্গ শরীরকে ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে দিনভর ঝুলিয়ে রাখা হতো। এই মহিলারা প্রায় সবাই পরবর্তী সময়ে গনোরিয়া ও সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন। অনেক গর্ভবতী নারী অনাকাক্সিক্ষত সন্তান জন্মদানে অনাগ্রহতা দেখাতে গিয়ে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যারা সেটাও পারেননি, তারা সন্তান জন্মের পরে সেসব সন্তানকে আর গ্রহণে রাজি হননি। ফলে বিপুলসংখ্যক অবৈধ সন্তানের জন্ম নবপ্রতিষ্ঠিত একটি দেশের জন্য একধরনের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
কানাডিয়ান ইউনিসেফের চেয়ারম্যান সুমান ব্রাউন মিলার যুদ্ধকালীন একবার এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আরও একবার, মোট দুবার বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তার সেসব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে একটি বই লিখেছিলেন ÔAgainst our will Men, Women and Rape।
তার সেই বইতে উল্লেখ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন ২৫ হাজারের মতো নারী গর্ভধারণ করেছিলেন বলে তিনি মনে করেন। তবে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন ১০ হাজারের মতো। বাকিদের ভাগ্যে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ হয়নি। অধিকাংশ সন্তানের ভাগ্য গর্ভপাতের কারণে অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। এমন অভিমত অবশ্য অনেক ইতিহাসবিদেরও।
এসব নির্যাতিত নারীদের কথা প্রথম লোকচক্ষুর সামনে আসে, যখন হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ‘স্বাধীনতার ইতিহাস : দলিলপত্র’ শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর আর অনেক দিন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে সে রকমভাবে কেউ আর নাড়াচাড়া করেননি।
বলা যায়, যখন সর্বপ্রথম ভাস্কর এবং যুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো নারী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী সাহসিকতার সঙ্গে কলম ধরেছিলেন। তার জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ ‘নিন্দিত নন্দন’-এ তিনি এতটাই সাহস দেখাতে পারলেন, যেন তার কলমের আগা দিয়ে সেই কথাটিই তিনি বলতে চাইলেন, ‘আমাদেরকে যারা রক্ষা করতে পারেনি, এ লজ্জা তাদের। এ লজ্জা দেশের। তাদের কলঙ্কের বোঝা আমরা কেন বহন করব?’
পরে ২০০১ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রকাশ করে ‘৭১ ও যুদ্ধ-পরবর্তী কথ্যকাহিনি’। গ্রন্থটিতে পাঁচজন বীরাঙ্গনা নারীর সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা স্থান পেয়েছিল। ২০০২ সালে ডা. এমএ হাসান ৪২টি জেলার ৮৫টি থানার মাঠপর্যায়ের ২৬৭ জন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন ‘যুদ্ধ ও নারী’। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল ‘ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি’।
তবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. নীলিমা ইব্রাহীমের বই ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’। বইটিতে সাতজন বীরাঙ্গনা নারীর করুণ কাহিনি স্থান পেয়েছিল। যাদের মধ্যে যেমন ছিলেন কৃষক পরিবারের রমণী, একইভাবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূর কাহিনিও উঠে এসেছে। এ বইটি সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তিনি আবার প্রত্যক্ষভাবে ওই মহিলাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য ‘জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদ’ নামে একটি সংস্থার জন্ম হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় নারী পুনর্বাসন বোর্ডেরও জন্ম হয়েছে।
বীরাঙ্গনা নারীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ক্লিনিকে রাখা হয়েছিল। নারী পুনর্বাসন বোর্ড বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি হওয়া বীরাঙ্গনা নারীদের ক্রমান্বয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে একটি ইতিহাসের অধ্যায় রচনার চেষ্টা করছিল। ওই তথ্য সংগ্রহকালে ভিকটিমদের নামধাম, বয়স, পরিবারের সদস্যসংখ্যা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ নিয়ে আলোচনার অবতারণা করলেও স্থায়ী ঠিকানা নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়নি এবং জানার সুযোগ তৈরির জন্য ঠিকানা রাখলেও লিখিত ডুকমেন্টে সেই ঠিকানা রাখলেও কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এটি করার কারণ ছিল। তালিকাটি ঠিক রাখার জন্য সংখ্যাতত্ত্ব বহাল রেখে যেন ভিকটিমের পরিবার কোনো না কোনোভাবে বিপদ কিংবা অপমানের মুখে না পড়ে। দুঃখজনক বিষয় হলো, যখন কাজটি অনেকখানি এগিয়ে গেছে, বেশ বড় মাপের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে নারী পুনর্বাসন বোর্ড কর্তৃপক্ষের, সেই রকম এক সময়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ওই সমস্ত নথিপত্র তারা পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন। ওই সব বিষয় প্রকাশ্যে এলে ভিকটিম মহিলাটি ছাড়াও তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই সরকার চায় না ধর্ষণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসুক। বঙ্গবন্ধু অনেক সময় আবেগতাড়িত কথাবার্তা বলতেন, সে রকম এক বক্তব্য ছিল তার, ‘এদের ঠিকানা নাই, তো কী হলো, বলে দাও এখন থেকে তাদের ঠিকানা হবে ৩২ নম্বর ধানমন্ডি।’
বঙ্গবন্ধুর এই মন্তব্য ওই নির্যাতিতা নারীদের ঠিকানা খুঁজে নিতে কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি। বরং নারী পুনর্বাসন বোর্ডের কার্যক্রমকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল এবং জাতির জনকের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে ২০১৭ সালে ‘চলো যাই’ শিরোনামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। খালেদ মাহমুদ তূর্যের চিত্রনাট্য নিয়ে নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মাসুম রহমান তানি। নির্মাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, কয়েকজন তরুণ-তরুণীর দিশা খুঁজে পাওয়ার গল্প হচ্ছে ‘চলো যাই’। এ ছাড়া নির্যাতিতা ওই নারীদের নিয়ে একটি ব্রিটিশ একাঙ্কিকা (নাটক) নির্মিত হয়েছিল ‘উইমেন অব ওয়ার’ শিরোনামে। ওই নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল এক গ্রাম্য কিশোরী মরিয়মকে নিয়ে। যে পরে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। ৬০ মিনিটের ওই নাটকের রচয়িতা ছিলেন লিসা গাজী নামের এক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখিকা এবং তিনি নিজেই মরিয়মের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তার জন্ম ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিতান্তই এক শিশু ছিলেন।
তার বক্তব্য অনুযায়ী, সতেরো বছর বয়সে তার পিতার মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন লিসা। সেই সময়ে তার পিতা তাকে বলেছিলেন, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের ঠিক পরের একদিন তিনি এক রাস্তা ধরে হাঁটতে গিয়ে দেখতে পেলেন, অনেকগুলো ট্রাকে বোঝাই করে বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা এসব নির্যাতিত নারীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই নারীদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারেননি। কিংবা তাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, সে বিষয়েও তার কাছে কোনো তথ্য ছিল না।
ব্রিটিশ-বাংলাদেশি তরুণী লিসা গাজী শুধু পিতার মুখ থেকে শোনা এই তথ্যকে সম্বল করেই ‘উইমেন অব ওয়ার’ নামে নাটক লিখে মঞ্চায়িত করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ওই নাটকটি লন্ডনভিত্তিক মর্যাদাপূর্ণ থিয়েটার পুরস্কার হিসেবে চিহ্নিত ‘অফি পুরস্কারের’ জন্য মনোনয়ন পেয়েছিল।
ধীরে ধীরে এসব নারীর জীবনকাহিনি দিনের আলো ফোটার মতো করে প্রকাশ্যে আশা শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এদের নিয়ে অনেক লেখক-সাংবাদিক নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে কালি-কলমের আগায় তুলে আনছেন নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র।
বৃহত্তর সিলেটের তরুণ লেখক ও সাংবাদিক অপূর্ব শর্মারও রয়েছে এ-সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ ‘বীরাঙ্গনা কথা’। সিলেটের আঞ্চলিক পর্যায়ের মোট ১২ জন বীরাঙ্গনা নারীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ওই বই একটি সময়ের দলিল।
এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক লেখালেখির জন্য আরও একজন কৃতিমান লেখক তাজুল মোহাম্মদের নাম খুব সহজেই সামনে আসে। তিনি ১৯৭২ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক লেখালেখির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। একজন গবেষক হিসেবে ওই ধরনের সাহিত্যে তার নানামুখী ভূমিকার কারণে নিজেই এক ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েছেন। এ পর্যন্ত তার লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও অধিক। সিলেটে গণহত্যা এবং বীরাঙ্গনাদের নিয়ে তার কাজ সবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিশেষ করে, ব্রিটেনের টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশনের উদ্যোগে এবং তাজুল মোহাম্মদের সক্রিয় সহযোগিতায় নয় মাসের তার অক্লান্ত শ্রমে আর ঘামে ‘দ্য ওয়ার ক্রাইম ফাইল’ নামক প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণের কারণে একসময় মৌলবাদী ও যুদ্ধাপরাধীদের হুমকির জন্য তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। বর্তমান নিবাস তার কানাডায় হলেও তার কলমের কাজ থেমে নেই। নিরন্তর দেশ এবং দেশের যুদ্ধসংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ-সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম ‘একাত্তরের বীরাঙ্গনা কথা’। এসব গবেষণামূলক লেখালেখির জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পদক।
এ ধরনের আরও কিছু বইয়ের মধ্যে রয়েছে মাসুদ রানার ‘একাত্তরের বীরাঙ্গনা ও নির্যাতিত নারী’; শেখ আবদুল হক চাষী রচিত ‘একাত্তরের বীরাঙ্গনা ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ’।
তবে ইতিহাসবিদ ও প্রখ্যাত লেখক মুনতাসীর মামুনের নাম এসব বিষয়ে সবার আগে আসে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং নির্যাতিত নারী বিষয়ে এত বেশি তথ্যবহুল লেখালেখি করেছেন, যা কালের পরীক্ষায় একদিন অন্য মাত্রা পাবে, তাতে সন্দেহ নেই।
তপন কুমার দে লিখিত ‘বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ’ এ সংক্রান্ত আরও একটি গ্রন্থ। বিশিষ্ট নারীনেত্রী মালেকা বেগমেরও রয়েছে ওই সংক্রান্ত গ্রন্থ।
এ ছাড়া বীরাঙ্গনা রমণী রমা চৌধুরীর লেখা ‘একাত্তরের জননী’ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনিও ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মতো সাহস করে বইটিতে নিজের জীবনের করুণ সেই অধ্যায়কে কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একাত্তর সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তারপর পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেও একে একে তার তিন শিশুপুত্রকে হারিয়ে চূড়ান্ত মাত্রায় অসহায় জীবনের হাতে নিজেকে সমর্পিত করলেও পরাজয় স্বীকার করেননি। একে একে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার লেখা ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পায়ে হেঁটে হেঁটে সে বইগুলো বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ সামান্য টাকা দিয়ে নিজের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে একসময় কক্সবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্ব পালন করে গেলেও একাত্তর সালের ওই ঘটনা তার জীবনের মোড় পাল্টে দিয়েছিল। একাত্তর সালের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি আর পায়ে কোনো জুতো পরতেন না। ২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হলে চট্টগ্রাম পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার দিয়ে সম্মানিত করেছিল এবং সরকার তাকে মরণোত্তর রোকেয়া পদকে ভূষিত করেছিল।
তবে এ পর্যন্ত বীরাঙ্গনা নারীদের নিয়ে যিনি সবচেয়ে বড় মাপের কাজ করেছেন, তার নাম সুরমা জাহিদ। তার জন্মসাল ১৯৭০। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এতটাই শিশু ছিলেন যে পরবর্তী সময়ে এ বিষয় নিয়ে কৌতূহলের জন্ম হওয়ার কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তার অন্তরে নিজের শিকড়ের সন্ধান তাকে এতটাই আকুল করে তুলেছিল বিষয়টি এককথায় অবিশ্বাস্য। অথচ সেই অবিশ্বাস্য বিষয়টিকেই তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুললেন কলম দিয়ে। একে একে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করলেন, যার বেশির ভাগই মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের নিয়ে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘বীরাঙ্গনা সমগ্র এক’, ‘বীরাঙ্গনা সমগ্র দুই’, ‘বীরাঙ্গনা সমগ্র তিন’ এবং ‘বীরাঙ্গনা সমগ্র চার’। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তার রয়েছে এ বিষয়ের ওপর লেখা ‘বীরাঙ্গনাদের কথা’, ‘একাত্তরের নির্যাতিত নারীদের ইতিহাস’, ’৭১-এর সম্ভ্রম হারানো নারীদের করুণ কাহিনী’, ‘এই সংগ্রামে আমি ও আদিবাসী বীরাঙ্গনা’, ‘সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বদেশ’, ‘একাত্তরের বীর মাতাদের অজানা কথা’ ইত্যাদি।
বীরাঙ্গনাদের তথ্য সংগ্রহ করতে তার সময় লেগেছে সুদীর্ঘ ১১ বছরের মতো। ২০১০ থেকে ২০১৮Ñএই সময়ের মধ্যে তার আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে শুধু বীরাঙ্গনা নারীদের ওপর। লেখক ৩৬১ জন নির্যাতিত মহিলার সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে যে আটটি বই লিখেছিলেন, তাদের একত্রিত করে সুরমা জাহিদ ‘বীরাঙ্গনা সমগ্র’ হিসেবে চার খণ্ডে তা পাঠকের হাতে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে এর আগে আর এত বড় কাজ কেউ করেননি। সুরমা জাহিদকে ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি পদক এবং ২০২৩ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়েছে।
এ-সংক্রান্ত আনোয়ার পাশার আরও একটি গ্রন্থ রয়েছে : ‘রাইফেল, রোটি, আওরত’।
যুদ্ধশিশু : একাত্তরের নয় মাস চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন নারীরা। তাদের সংখ্যা কত ছিল-এর সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও সরকারি নথিপত্রে দুই লাখ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সেই দুই লাখ নারী, যারা ২৫ মার্চের পর থেকে এবং তাদের কুলাঙ্গার বাঙালি সহযোগীদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। তাদের দ্বারা জন্ম নেওয়া শিশুরাই ‘যুদ্ধশিশু’। লন্ডনভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের হিসাব অনুযায়ী, নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা দুই লাখই ঠিক আছে।
কিন্তু ওই সময়ের যুদ্ধশিশু ও তাদের জন্মদাত্রী মায়েদের নিয়ে কাজ করছিলেন এমন এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ডা. জিওফ্রে ডেবিনের অভিমত ছিল, সংখ্যাটা ছিল দুই লাখেরও ওপরে।
যুদ্ধ-পরবর্তী স্থানীয় বাঙালি চিকিৎসকদের সহায়তায় ব্রিটিশ, আমেরিকান ও অস্ট্রেলীয় চিকিৎসকদের একটি দল ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রায় ২৩ হাজার নির্যাতিত গর্ভবতী মায়ের গর্ভপাত ঘটানোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকায় ওই মহিলাদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সেবা সদন নামে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ওইসব সেবা সদনে তিন থেকে চার শয়ের মতো শিশুর জন্ম হয়েছিল। সেই হিসাবে ইউনিসেফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওইসব যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের মতো।
এত বিপুলসংখ্যক যুদ্ধশিশু নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চূড়ান্তভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজকর্মী ড. নীলিমা ইব্রাহীম, যিনি একসময় নারী পুনর্বাসন বোর্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনি এ সমস্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে, বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক মন্তব্য ছিল, ‘আমি এসব নষ্ট রক্ত দেশে রাখতে চাই না। প্লিজ, আপনারা এদেরকে বিদেশে পাঠাতে চেষ্টা করুন।’ এ বক্তব্যের পরে জেনেভাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিল। এবং এ লক্ষ্যে যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশে পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধান) আদেশ ১৯৭২ নামে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত একটি আদেশ জারির মধ্য দিয়ে ওইসব শিশুকে বিদেশে পাঠানোর প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন দুটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-ঢাকাভিত্তিক বাংলাদেশ সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি যৌথভাবে এ প্রকল্পে সহায়তা দিতে কাজ করেছিল। প্রথম দিকে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কানাডীয় দুটি সংগঠন ওইসব শিশুকে দত্তক গ্রহণে এগিয়ে আসে। ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই ১৫ জন যুদ্ধশিশুর প্রথম চালানটি গ্রহণ করেছিল কানাডীয় কর্তৃপক্ষ। ওই দত্তক গ্রহণের সঙ্গে কানাডীয় দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল ‘মন্ট্রিল ফ্যামিলিজি ফর চিলড্রেন’ এবং অন্যটি ছিল টরেন্টোভিত্তিক ‘কুয়ান ইন ফাউন্ডেশন’।
পরে কানাডা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়াতে আরও বেশ কিছু যুদ্ধশিশুকে দত্তক কোঠায় পাঠানো হয়েছিল। তবে সঠিক সংখ্যাটি কত, সে সম্পর্কে রাষ্ট্রের কাছে কোনো তথ্য নেই। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি যাতে মানুষের সামনে না আসে, সেই চেষ্টাই করতে বলতেন সবাইকে।
তবে অনুমান করা হয়, সংখ্যাটি কয়েক হাজার ছিল। দেশের প্রথম যুদ্ধশিশুর নাম ছিল ‘জয়’। একাত্তরের ১৬ মার্চ শিশুটির বয়স ছিল মাত্র ১০ দিন। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসারত ওই শিশুকে দেখতে পেয়েছিলেন সুইডেনের এক সাংবাদিক সভেন স্টমবার্গ। তিনিই তাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সম্প্রতি ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি দেশের প্রথম যুদ্ধশিশুর স্বীকৃতি পেয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশের মেরিনা খাতুন।
২০২২ সালের ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৮২তম বৈঠকে যুদ্ধশিশুদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তবলে তারা পিতার নাম ব্যবহার করা ছাড়া রাষ্ট্রের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার লাভ করল। তবে এ অধিকার দেওয়ার কথা এমন এক সময়ে উত্থাপিত হলো, যখন এরা কেউই আর শিশুর বয়সসীমার মধ্যে নেই। এমনকি কে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করছে, রাষ্ট্রের কাছে সেই হিসাবও আর নেই। একসময় দত্তক আইনের বদৌলতে যারা বিদেশে গিয়েছিল, মাত্র কয়েকজন ছাড়া বাদবাকি প্রায় সবাই ভালো আছেন। কিন্তু যারা যাওয়ার তালিকায় ছিলেন, তাদের নিয়ে দেশে এক অন্য ধরনের বিতর্কের জন্ম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সরকার সেই যাওয়ার পথটাও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। বিতর্কের সূত্রপাত ধর্ম নিয়ে হয়েছিল। বলা হয়েছে, যেহেতু ওই যুদ্ধশিশুরা মুসলিম দেশের জননীর সন্তান, কিন্তু প্রতিপালন হবে বিদেশের খ্রিষ্টান সমাজে, এটা এক অনভিপ্রেত বিষয়। এসব যুদ্ধশিশু নিয়ে (কানাডা) মুস্তাফা চৌধুরীর লেখা ‘৭১-এর যুদ্ধশিশু : অবিদিত ইতিহাস’ এক প্রামাণ্য দলিল। যদিও শুধু কানাডা নিয়ে লেখা। কিন্তু অন্য দেশসমূহে এদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আর কোনো তথ্য নেই আমাদের হাতে।


 শামসাদ হুসাম
শামসাদ হুসাম