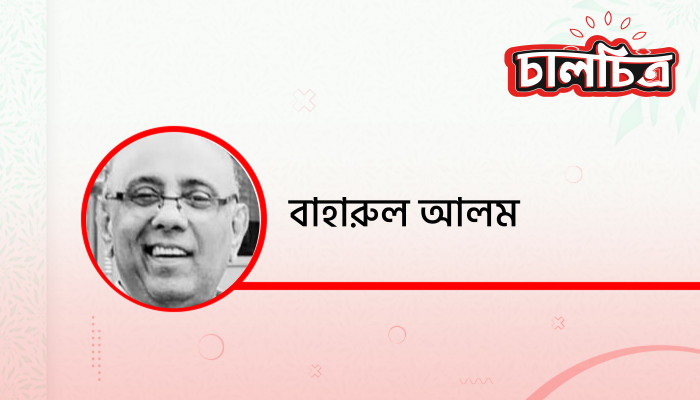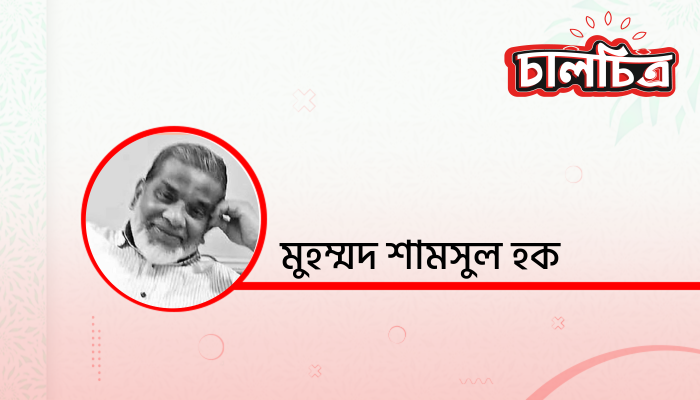ড. এবিএম এনায়েত হোসেন
বাবার ইন্তেকালের পর থেকে আমার উচ্চ শিক্ষার মাসিক ভাতা বহন করার ভার পড়ল ছবি ভাই (দাদা) ও বাচ্চা ভাই (ছোট দাদা) এর উপর। একেক জন ৫০.০০ টাকা করে মোট ১০০.০০ টাকা পাঠাতেন প্রতি মাসে।
মেজ ভাইয়ের শারিরীক অসুস্থতা এবং কাঠের ব্যবসায়ে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিযোগিতার ফলে তখন তাঁর ব্যবসায় মন্দা চলছে। তাছাড়া ‘জাহিদ’ ভাই ও মেঝ ভাইয়ের শ্যালক মিলে তাস-জুয়া খেলা ও মদাশক্তির ফলে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহের ঘাটতি দেখা দেয়।
এ সময় স্নাতাকোত্তর পর্যায়ে প্রথম শ্রেণি পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম আমি। যে পেপারটাতে উত্তর দিয়ে হতাশ হয়েছিলাম একথা ভেবে যে, হয়তো বা প্রথম শ্রেণি পাব না। একপর্যায়ে ইয়ার ড্রপ দেব বলে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু বন্ধু শাহজাহান আমাকে বছর ড্রপ দেয়া থেকে বিরত রাখলো। বললো-
‘এনায়েত! ইয়ার ড্রপ দেয়ার মতো ভুল সিদ্ধান্ত কখনো নিও না। তোমার ১ম পেপার একটু খারাপ হলে কী হবে? ২য় পেপার দিয়ে তুমি দেখো এটা পুষিয়ে নিতে পারবে।’
স্নাতকোত্তর শ্রেণির ফলাফল তেমনটিই হলো। এ সময় হঠাৎ একদিন শাহজাহান এসে আমার হাতে মধ্যে কী যেন একটা ভাঁজ করা বস্তু গুঁজে দিয়ে বললো-
‘আশরাফুন তোমার জন্য কী যেনো একটা পাঠিয়েছ, এনায়েত। তুমি খুলে দেখ।’
আমি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়েই কাগজের ভাঁজটা খুললাম, দেখি ভিতরে কাঁচা হাতের লেখা একটা চিরকুট এবং একখানা হাতে সেলাই করা রুমাল। রুমালের এক কোণায় সূচীকর্মে লেখা ‘ভালোবাসি’। চিরকুটে কাঁচা হাতে আবেগপূর্ণ কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। এসব মাত্র একবার কোনোমতে পড়েই ছিড়ে কুচি কুচি করে কামরার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলাম। কারণ, বন্ধুর আপন ছোট বোনের প্রতি আমার কোনোরকম মোহ ও ভাললাগা জন্মায়নি। তাকে নিজের ছোট বোনের মতই মনে করতাম।
ইতোমধ্যে সাভার, ডেমরা, ভুলতা বাজার মুড়াপাড়া ও মাঝিনা নদীর পারে অবস্থিত শাহজাহানদের আদি নিবাসে প্রায়ই আমাকে শাহজাহান তাদের সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতে শুরু করলো। কখনো রিকশায়, কখনো বাসে আবার কখনো নৌকায় যাতায়াত। মুড়াপাড়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমত্র বর্ষ্টীল স্কুল (কিশোর অপরাধীদের সংশোধনী প্রতিষ্ঠান) ছিল। এটা দেখার নাম করে শাহজাহান সেখানকার ভুঁইয়া পাটকলের মালিক তার আপন খালুর বাড়িতে দুপুর বেলায় ভুঁড়িভোজের ব্যবস্থা করেছিল।
এখানে শাহজাহানের খালাত বোন যে, তাকে পছন্দ করতো সেকথাটা জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইশারা ছিল না। কারণ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শাহজাহান তার সহকর্মীর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেয় আর ঐ সময়েই দুজনের মধ্যে মন দেয়া-নেয়ার শুরু হয়ে যায়। শেষ পরিণতি ‘শাদী-ই-কবুল’।
১৯৬৬ সনে আমাদের এমএসসি শেষ পর্বের ফলাফল বের হয়। এবার চাকরির জন্য অপেক্ষা।
শাহজাহানের মায়ের কুলখানিতে স্বাভাবিকভাবেই আমি আমন্ত্রিত। ওদের গ্রামের বাড়িতে সব আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে কুলখানির খাওয়া-দাওয়া এবং দোয়া-মাহফিল সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হলো। এবার ঢাকা শহরে ফেরার পালা। বিকেল বেলায় হঠাৎ শাহজাহান আমাকে জানালো যে-
‘এনায়েত। তোমাকে ডেমরার ডা. দুলা ভাই উঠানে গিয়ে তার সাথে একটু দেখা করতে বলছে। কী যেন কথা তোমাকে একান্তে বলতে চান।’
আমি মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। একটা নাজুক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেব তা নিয়ে সংশয় দানা বাঁধালো মনে। যাহোক, বুক র্দুর্দু করা নিয়ে আমি উঠানের এককোণে ডাক্তার সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে সালাম জানালাম।
‘আস সালামু আলাইকুম, ডাক্তার ভাই। আপনি আমাকে ডেকেছেন, কিছু বলবেন নাকি?’
-‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হ্যাঁ ভাই, আসেন আসেন। আসলে আশরাফুন ও ফাতেমা আপনার সাথে দেখা করতে চায়। ওরা যেন কী আপনাকে বলতে চায়।’
এ সময় ওদের দোতলা দালানবাড়ি থেকে সালোয়ার কামিজ পরা দুবোন মাথায় ওড়না দিয়ে ঢেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে আবেগ ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে সালাম জানালো।
-‘আমরা তো এতিম হয়ে গেলাম, ভাইয়া। মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা আমরা কোথায় পাব? একথা বলে প্রথম আশরাফুন এবং দেখাদেখি পরে ফাতেমাও ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলো। আমার হল সমূহ বিপদ। কীভাবে ওদেরকে সান্ত্বনা দেব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিশেষ করে ওদের মুরব্বি দুলাভাইকে সামনে দাঁড়িয়ে রেখে! বিষয়টি মনে হয় জ্ঞানী ডাক্তার সাহেব কিছুটা আঁচ করতে পরলেন। উনি কী যেন একটা উছিলা করে ঘরের মধ্যে চলে এলেন। আমি তখন কান্নারত দুবোনের মাথায় আলতো করে হাতটা রেখে বললাম-
-‘মা-বাবা কারও চিরকাল বেঁচে থাকে না রে বোন। এই দেখো না, গেল বছরের ডিসেম্বর মাসেই তো আমি আমার বাবাকে হারালাম। তাই বলে আমি কী আমার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি? তোমাদেরকেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে।
এসময় ওদের দুলাভাই আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্যামিকাদের কী যেন ইঙ্গিত করে বললেন। তখন তারা ঘরে ঢুকে গেল। দুলাভাই আমাকে বললেন-
-‘ভাই এনায়েত। আপনাকে একটা বিষয়ে খোলামেলাভাবেই বলতে চাই। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সাথে আমার শ্যালিকা আশরাফুনের একটা সম্পর্ক করার ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছেন হাসপাতালে থাকতেই। আশরাফুনেরও আপনাকে খুব পছন্দ। এ ব্যাপারে আপনার মতামতটা কী জানতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।’
-‘দুলাভাই, আপনি হয়ত জানেন যে, আমার গার্ডিয়ান এখন মেঝ ভাই আব্দুস ছালাম (তখন খুলনায়) এবং মেঝ দুলাভাই আলতাফ উদ্দিন আহমেদ (তখন চট্টগ্রাম)। তাদের মতামত ছাড়া আমি এ ব্যাপারে এক পা-ও এগুতে পারবো না।’
বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় আপাততঃ। বন্ধু শাহজাহানের অন্তরের খবর জানি না। আসন্ন শীতকালীন ও দুর্গাপূজার ছুটিতে ও প্রস্তাব দিলÑ
‘চল এনায়েত। এই ছুটিতে চাঁটগায় বেড়ায়ে আসি?
তোমার আপা-দুলাভাইকেও দেখে আসবে আর আমি একটু সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চাই। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতেও যাবার আকাক্সক্ষা আমার অনেকদিনের।’
-‘বেশ তো, শাহজাহান। আমি রাজি আছি। তোমার সাথে সাথে আমারও এক এ দুটো জায়গা দেখা হয়ে যাবে। অথচ দ্যাখো দু বছর চাটগায় মেঝ বুর বাসায় থেকে পড়াশুনা করে গেছি, কিন্তু কোনোদিন চন্দ্রনাথ পাড়েও উঠিনি, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতেও গোসল করিনি।’
আমরা দু’বন্ধু বেশ উৎসাহ উদ্যম নিয়েই একদিন চাঁটগার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে রওনা দিলাম। চট্টগ্রামে পৌঁছে রাত কাটলাম হাসনাবাগে মেঝ-বুর বাসায়। পরদিন সকালের নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়লাম চন্দ্রনাথ মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে। ট্রেনে চেপে কুমিরা স্টেশনে নামতে হলো। কারণ, সীতাকুণ্ডে অবস্থিত চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যেতে হলে এখান থেকেই রিকশা বা বেবিট্যাক্সি ভাড়া করে কিংবা হেটেই আড়াই থেকে তিন মাইল পথ যেতে হয়। বন্ধু শাহজাহানের জন্য চট্টগ্রামে এটাই তার প্রথম ভ্রমণ। ফলে কৌতুহলও তার অনেক বেশি। কুমিরা স্টেশনে নেমে বাইরের দিকে তাকালেই একটি পাহাড়ি টিলার উপর সুদৃশ্য লাল ইটের নির্মিত একতলা বাংলো টাইপের মতো একটা ইমারত চোখে পড়বে। এটিই তখন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) একমাত্র স্যানিটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে পরিচিত ছিল। শাহজাহান স্থাপনাটি দেখেই জিজ্ঞেস করল-
‘এনায়েত! পাহাড়ের উপরে ঐ যে লাল রঙের বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, ওটা আসলে কী?’
-‘ওটা একটা স্বাস্থ্যনিবাস।’ আমি উত্তরে জানালাম। শাহজাহান এ কথাটা শুনেই বায়না ধরলো- ‘চল না এনায়েত, স্যানিটোরিয়ামটা ঘুরে দেখে আসি?’
আমি বললাম- ‘না বন্ধু! এখন কুমিরার টিলায় গিয়ে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ওখানে দেখার মতো তেমন কিছু একটা নেই-ও! একটা হাসপাতাল আর এর চারপাশে পাহাড়ের উপর কিছু সংখ্যক নিম গাছ দেখতে পাবে, আর কি?’
আমার কথায় শাহজাহান কিছুটা দমে গেল! অতঃপর অনেকটা নিমরাজি হয়েই দুজনেই মিলে একটা রিকশা ভাড়া করে দুই-আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত সীতাকুন্ড পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম।
ওখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করতেই চন্দ্রনাথ মন্দির ও চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠবার পথের অবস্থাটা জেনে নিলাম। চন্দ্রনাথ মন্দিরটি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১০২০ ফুট এবং পাহাড়টি সীতাকুন্ড বাজার থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে দৃশ্যমান। পাহাড়ের চূড়ায় উঠবার জন্য দুটি পথ বর্তমান। ডানদিকে ঝরণা ধারা বরাবর বাঁধানো খাড়া সিড়ি পথ। ঝরণার বামদিকে পার্বত্য উঁচু নিচু পায়ে চলা পথ। এ পথে মাঝে মধ্যে দু একটা বড় পাথর ও ভাঙা সিড়ি চোখে পড়বে।
আমরা ঝরণার লাগোয়া খাড়া সিড়িপথ দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠব বলে মনস্থ করলাম। ঝরণার পানি উঁচু পাহাড় থেকে ঝরে পড়ার স্থানটিতে ছোট-খাট একটা অগভীর কুয়া সৃষ্ট হয়েছে। আমরা প্রথমে কুয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে আজলা ভরে পানি নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। কিন্তু মজার বিষয় হলো, ঝরণার পানি বেশ ঈষদুষ্ণ পানিই পান করে গলাটা ভিজিয়ে নেই। ফিরে এসে আবার সেই সিড়ি ভেঙে উপরে ওঠা। কিছু দূর উপরে উঠে একটা প্রশস্থ চাতাল। এখানে উঠে মনে হলো ক্ষিদে পেয়েছে। একটা ব্যাগে করে কয়েক খণ্ড পাউরুটি আর দুটো পাকা সাগর কলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই ভোর বেলায় ভাগনি হাসি। বলেছিল মামা! পাহাড়ে চড়তে চড়তে ক্ষিদে পেলে খাবে কি?
সামান্য নাস্তা দিয়ে দিলাম সঙ্গে। ক্ষিদে পেলে দুজনে খেয়ে নিও।
হাসির কথাগুলো মনে করতে করতে পাউরুটি আর কলা খেয়ে শরীরে যেন নতুন করে শক্তি পেলাম। সূর্য তখন প্রখরতর হয়ে ঝলমলে রশ্মি বিলানো শুরু করেছে। তবে সামুদ্রিক বাতাসের গতি তীব্রতর থাকায় সূর্যের প্রখরতা তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারছিল না। যাহোক, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মন্দিরটি তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু একদিকে উচ্চতা এবং অন্যদিকে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা এর কোনোটিই আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ছিল না। সুতরাং কিছুটা পথ পাড়ি দেবার পর আমি হাফিয়ে উঠলাম। বন্ধু শাহজাহানকে বলতে বাধ্য হলাম।
-‘শাহজাহান। না ভাই আমার পক্ষে এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠা সম্ভব নয়।’
-‘এনায়েত। চন্দ্রনাথ মন্দির দেখবার নিয়ত করে যহন আইছি, তহন মাছপথ থাহি ফিরে যাইবা?’
-‘আমার শরীর আর চলছে না, শাহাজাহন। না হয় তুমি একলাই চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাও। আমি এখানেই তোমার ফেরত আসার জন্য অপেক্ষা করি।’
-‘না বন্ধু, তা হয় না। বরং এমনটা করলে কেমন হয়? উপরের মাত্র কয়েকটা সিড়ি উঠলেই আমরা বীরুপক্ষ এর মন্দির চত্বরে উঠে যাব। ঐ পর্যন্ত কোনো মতে উঠ এনায়েত, তারপর না হয় নামা যাবে!’
প্রস্তাবটা মেনে নিলাম আমি। বীরুপক্ষ বা ভোলানাথ মন্দির হিসেবে পরিচিত এ পীঠস্থান থেকে চন্দ্রনাথ মন্দির আরও ১০০-১৫০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অবশেষে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় না উঠেই আমরা দুজন সিড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরেই।
ফেরার পথে আবার উষ্ণ প্রস্রবণের পানির আধাবেরর কাছে পৌছে হাত মুখ ধুয়ে ঈষদুষ্ণ পানি পান করেই তৃষ্ণা মেটালাম। এরপর সীতাকুন্ডু রেল স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনের অপেক্ষা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহাদুরাবাদ মেইল ট্রেনটি দ্রুতগতিতে এসে স্টেশনে থামলো। আমাদের টিকেট কাটা হয়েছিল আগেই। আমরা অপেক্ষাকৃত হালকা পাতলা ভিড়যুক্ত একটা বগি দেখে ট্রেনে চাপলাম। আধা ঘণ্টার মধ্যেই চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পৌঁছে একটা রিকশায় চেপে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠবার অভিজ্ঞতা থাকলো পারা না পারার বেদনায় ম্লান হয়ে।
পরদিন কক্সবাজার সৈকত ভ্রমণ। চট্টগ্রাম শহর থেকে মুড়ির টিন নামের সরাসরি কক্সবাজার-টেকনাফ রুটের বাসযাত্রা। সকাল বেলায় দু’বন্ধু কিছু চা নাস্তা শেষ করেই রওনা দিলাম বাস স্টেশনে। টিকেট কেটে দুজন তরুণ সামান্য হালকা কিছু প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ও দৈনিক ব্যবহার্য টুকিটাকি দ্রব্যাদি একটা ভ্রমণ ব্যাগে ভরে বাসে চড়ে চললাম কক্সবাজার সৈকতের উদ্দেশ্যে।
গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দিনের আলো গড়িয়ে এল। দেড় দুই মাইল থাকতেই সাগরের ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পেলাম। কক্সবাজার শহরে নেমে একটা রিকশা ভাড়া করে পর্যটনের মোটেল প্রাঙ্গণে পৌঁছালাম।
স্বপ্নের সমুদ্র সৈকতের দিকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখি অসীম জলরাশি। যেন ফুলে ফুসে তীরের দিকে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। বেলাভূমির স্বল্প গভীরতায় কতিপয় দূরন্ত দামাল ছেলে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে লুটোপুটিতে ব্যস্ত। তখনো বিশ্বের দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদচারণা শুরু হয়নি। সৈকত ঘেষে বেলাভূমির কিছুটা উঁচুতে একের পর এক ছোট ছোট ছাপড়া ঘরের একটা সারিবদ্ধ উপস্থিতি চোখে পড়ল। এছাড়া চারদিকটা শুন-শান। শুধু বাতাসের শব্দ আর সামুদ্রিক ঢেউয়ের গর্জন কানে আসছিল।
পর্যটনের বহুতল মোটেলগুলো সমুদ্রতটের কাছেই অবস্থিত। মোটেলে তেমন ভিড় নেই। আমরা দু’বন্ধু মিলে অভ্যর্থনা ডেস্কে গিয়ে আমাদের নাম ঠিকানা সব লিখে দিলাম একটা মোটা খাতায়। দক্ষিণ পশ্চিম দিকের একটা ডবল বেড ওয়ালা কক্ষ একদিন একরাতের জন্য ভাড়া নিয়ে আমাদের হ্যান্ডব্যাগ দুটো রুমের মধ্যে রেখেই ছুটলাম সমুদ্রতীরে। বিকেলের সূর্য তখন অস্তাচলে যাবার পথে। আমরা সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির সীমান্তে সূর্য ডোবার অপূর্ব দৃশ্য চাক্ষুষ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে সাগর তীরে খালি পায়ে পানির মধ্যে হাঁটতে থাকলাম। খুব শিগগির সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এল। দেখলাম পশ্চিম আকাশের অস্তাচলে সমুদ্রের অসীম জলরাশির সীমানায় একটা বিশাল গোলাকৃতির অগ্নিকুণ্ডের থালা। দিনের বেলায় আলোক-ছড়ানো মহাপ্রতাপশালী সূর্যের এরূপ নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মান ঠান্ডা প্রতিকৃতি সত্যিই বিস্ময়কর। সূর্যের এ অস্ত যাবার দৃশ্য অবলোকন করছে সৈকতে ছুটোছুটিরত বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় ছেলেমেয়ে আর আমাদের মতো আরও মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক পর্যটক।
পরদিন খুব ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমরা দুজন আবার ছুটে গেলাম সাগর সৈকতে। বেলাভুমিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমুদ্র তীরবর্তী বালুকাময় বিস্তীর্ণ চত্বরে হাজায় হাজার লাল রঙের কাঁকড়াকে দল বেধে বেড়াতে দেখা গেল। কিছুটা কাছে গিয়ে দেখব বলে এগিয়ে যেতেই আমাদের পায়ের শব্দে কাঁকড়ারা এদিক-ওদিক দৌঁড়াতে শুরু করলো। তারপর এক সময় সবাই যেন চোখের পলকে হয়ে পড়ল অদৃশ্য। কাছে গিয়ে দেখলাম যে, ছোট আকারের এসব কাকড়াদের লুকিয়ে থাকার জন্য বেলাভূমি বালুচরগুলোতে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত। প্রকৃতির কী অপরূপ নিরাপদ আশ্রয় এদের জন্য।
বেলা বাড়ার সাথে সাথে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং মোটেলে আগত দু-চারজন পর্যটক সমুদ্র তীরে এসে সাগরের ঢেউয়ের পানিতে পা ভেজাতে কিংবা তীরে আসা নানারকম ঝিনুক কুড়াতে লাগলো। আমরা সমুদ্রের পানিতে নেমে গোসল করব ফলে তৈরি হয়ে এসেছিলাম। বেলা ১০-১১ টার দিকে আমরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সফেন, ঘোলা পানিতে ঢেউয়ের মাঝে নেমে পড়লাম জীবনের প্রথম সমুদ্র স্নানে। এ রোমাঞ্চ যেন ভুলবার নয়। তবে অনেকের পরামর্শ মোতাবেক অধিকতর গভীর পানিতে না গিয়ে তীরের কাছাকাছি জায়গাতেই সাঁতরিয়ে বেড়ালাম। ঢেউ আসার সময় পানির উপর ভেসে থাকলে ঢেউয়ের ধাক্কাতেই তীরে এনে ছুঁড়ে ফেলে। এ সত্যিই উপভোগ্য।
স্থানীয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অবশ্য উপকূলের বেশ গভীরে গিয়েই সাঁতার কাটছিল। কিন্তু আমরা দুজন যুবক সাঁতার জানা সত্ত্বেও সৈকতের গভীর পানিতে যেতে একটা অজানা ভয়ে ভিত ছিলাম। কারণ, সামুদ্রিক ঢেউগুলো তীরে এসে আছড়ে পড়ে সমুদ্রে ফিরে যাবার সময়ে সাতারুদেরও টেনে নিতে পারে।
সমুদ্রের পানি নাকি লবণাক্ত হয়। এ কথার সত্যতা আজ যাচাই করে দেখলাম মুখে পানি নিয়ে কুলি করার মাধ্যমে। ঘণ্টা খানেক সমুদ্রের পানিতে ডুব দিয়ে কিংবা ঢেউয়ের সাথে খেলা করে সময়টা কাটলো। একসময় আমরা দু বন্ধু সমুদ্রস্নান শেষ করে মোটেলে ফিরে এলাম।
বিকেলে সৈকতের সারিবদ্ধ ছাপড়া দোকানগুলো থেকে টুকিটাকি উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন কেনার পালা। কিন্তু বন্ধুবর শাহজাহানের ভ্রমণ পিপাসা তখনো সম্ভবত: মেটেনি। তা না হলে সে দোকানীদের কাছে এমনটি প্রশ্ন করতো না।
-‘আচ্ছা ভাই! এখান থেকে হিমছড়ি যাওয়ার কী কোনো ব্যবস্থা আছে? দূরত্বই বা কতটুকু?’
কিছুটা মধ্যবয়সী দোকান মালিকের কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। অল্প বয়স্ক কর্মচারী বা বিক্রেতাদের অধিকাংশেরই জানা নাই বলে উত্তর দিল।
-‘এহানোথ যন হিমছড়ি ঝরণার যাইতে বেবিট্যাক্সি লইতে পারন। আরবার ঘোড়ায় সত্তয়ার কইরেও যাইত পারন। বিশ মাইলের লাহান দূর হইত পারে।’
উত্তরটা শুনে শাহজাহানের উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়তে দেখলাম। আমি ওকে থামানোর জন্য বললামÑ
‘শাহজাহান! হিমছড়ি গিয়ে কাজ নাই ভাই। কারণ, সম্পূর্ণ পথটা আমাদের অজানা! আর তাছাড়া ওখানে তেমন লোকজনও যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।’ বন্ধুকে শান্ত করে পরদিন দুপুর বারোটার আগেই আমরা মোটেল থেকে বিদায় নিয়ে কক্সবাজার শহরের বাস স্টেশনে এলাম রিকশায় চড়ে। তারপর চট্টলার পথে দুটি টিকেট কিনে বাসে করে ফিরে এলাম মেঝ-বুর বাসায় হাসনাবাগে। এভাবেই শেষ হলো আমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড় ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ।