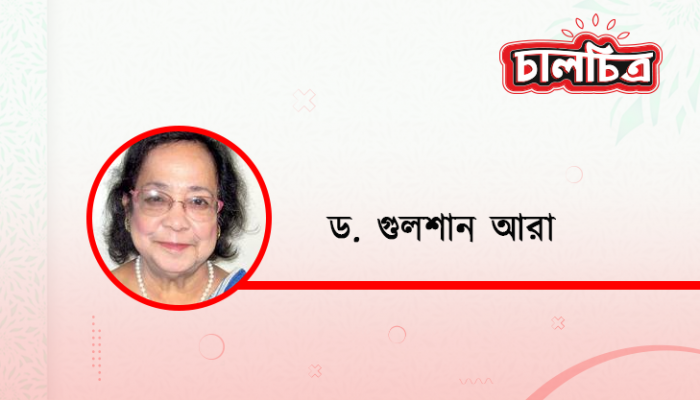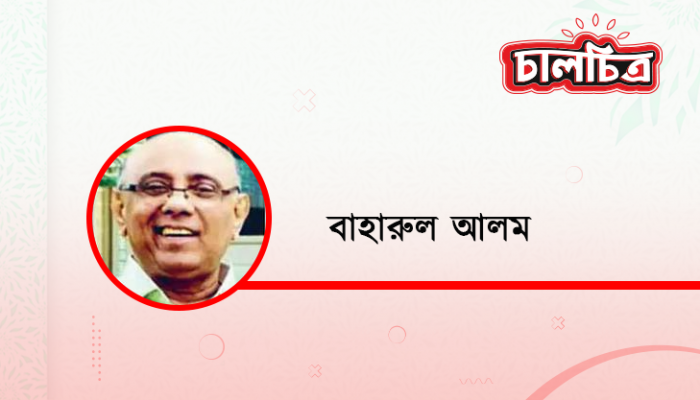ড. এবিএম এনায়েত হোসেন
দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন সময় থেকেই রুমমেট মোহাম্মদ শাহজাহান-এর সাথে সখ্যতা ও মেলামেশা আরো গাঢ় হতে থাকলো। হঠাৎ একদিন, শুক্রবার, ছুটির দিনেও আমাকে বললো
-চলো এনায়েত, সাভার থেকে বেড়িয়ে আসি।
-সাভারের যাবো? কিন্তু দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবো? আমি কিছুটা সংশয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম।
-খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমার আব্বাতো এখন সাভার সরকারি ডিসপেনসারির ডাক্তার। আমরা যাবো শুনে ওখানকার পুকুর থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা করেছেন।
আমি আর কথা বাড়ালাম না। শাহজাহানের সাথে মিরপুর-গাবতলী থেকে সাভার-নয়ারহাট রুটের মুড়ির টিনের মত দেখতে কাঠ-বডিওয়ালা বাসে চড়ে সাভার থানা রোডে গিয়ে নামলাম। প্রায় দুুপুর নাগাদ পৌঁছে প্রথমে চা-নাস্তার পর্ব সেরে মধ্যাহ্ন ভোজে কয়েক পদের তাজা মাছের তরকারি, সবজি, মুরগি ভুনা এবং খাসির রেজালা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া হলো।
বিকেলে বিদায় নেবার আগে উঠানের এক কোণায় পাটি পেতে শাহজাহানের দুটি বোন ও একজন ছোট ভাই গোল হয়ে বসে আমাকে ডেকে আনলো শাহাজানকে দিয়ে।
শাহজাহান বসার ঘরে এসে আমাকে বললো
-এনায়েত। তুমি একটু আমার ছোট ভাই-বোনদেরকে গল্প শোনাও। ওরা তোমার সাথে পরিচিত হতে চায়।
আমার কোনো ছোট ভাই-বোন না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ছোটদের প্রতি আমার আজন্মকালের প্রীতি ও আকর্ষণ। আর এ শূন্যতা পূরণ করেছে বরাবরের মত আমার ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নিরা। উঠোনে এসে দেখতে পেলাম, শাহজাহানের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত কিশোরী বোন আশরাফুলনেছা, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ফাতেমা বেগম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত সবচেয়ে ছোট ভাই মোজাম্মেল হক মোল্লা।
পরিচয়-পর্ব শেষে রোগা-পাতলা ছিপছিপে গড়নের গৌরবর্ণের ফাতেমা আবদার ধরলো
-ভাইয়া। আমাদেরকে একটা মজার গল্প শোনাতে হবে।
গল্প শোনানোটা আমার জন্য নতুন নয়। কারণ মেঝবু ও ছোটবুর ছেলেমেয়েদেরকে অজস্র গল্প শুনিয়েছি। কখনও বা রাজা-রাজড়া, রাজপুত্র-রাজকন্যাÑ আবার কখনোবা ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানবের গল্প। সুতরাং, শাহজাহানের ছোট ভাই-বোনদেরকে প্রভাবিত করার মত মজার একটা গল্প শুনিয়ে দিলাম ওদেরকে।
সন্ধ্যা হয়ে আসছিল বিধায় আমরা সালাম বিনিময় করে আবার ঢাকার দিকে রওয়ানা দিলাম।
এর কয়েক মাস পরেই খবর এলো যে, শাহজাহানের মা স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যাশায়ী। হল থেকে আমি আর শাহজাহান গেলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে। দেখলাম একজন শীর্ণদেহী পর্দানশীল মহিলা শুয়ে আছেন হাসপাতালের বেডে। আমাকে দেখে মাথার ঘোমটাটা আরো সামনের দিকে টেনে একটু জড়সর বোধ করতে লাগলেন। আমি বেড়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলাম।
- আসসালামু আলায়কুম চাচি আম্মা! আপনার শরীর এখন কেমন?
-আলায়কুম আসসালাম, বাবা। আমি অহন কিছুডা সুস্থ আছি। বাকি আল্লাহ ভরসা।
গলার স্বরটা এতই নিচু যে, প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।
চাচি আম্মার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন শাহজাহানের আব্বা ডা. ইউসুফ আলী মোল্লা। আমি তাঁকেও সালাম জানালাম। গেট থেকে কিছু কমলা কিনে এনেছিলাম সঙ্গে করে। ঠোঙাটা শাহজাহানকে দিয়ে বললাম তার আব্বার হাতে দিতে।
আধাঘণ্টা-একঘণ্টা যাবৎ রোগির শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে আসার সময়ে বললাম
-চাচাজান। কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছি চাচিজানের সুস্থতার জন্য। যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ডাকবেন, আমি হাজির হবো।
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার খবর এলো যে, শাহজাহানের মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী। জরায়ু অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। জরুরিভাবে গ্রুপ-বি রক্ত লাগবে দু’বোতল।
আমি আগ্রহী হয়ে বললাম, আমার রক্তের গ্রুপ বি। আমি একবোতল রক্ত দিতে প্রস্তুত।
এ কথা শুনে শাহজাহানের আব্বা-মা দু’জনেই যেনো কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। যথাসময়ে আমি রক্ত দিয়ে হলে ফিরলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো সম্ভবত অন্যরকম। ডাক্তারের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শাহজাহানের মা ইন্তেকাল করলেন। পরে জানতে পেরেছি যে, ভদ্রমহিলা ডাক্তার সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। প্রথম পক্ষের শুধু একজন কন্যা সন্তান জীবিত আছে। শাহজাহানের বড় এবং বিবাহিত। আপন চাচাতো ভাই, পেশায় একজন ডাক্তার, তার সাথে বিয়ে হয়ে স্বামী ও ছেলেমেয়েসহ ডেমরার বসবাস করে। গ্রাম্য এমবিবিএস ডাক্তার হয়েও তাঁর পসার ও নামডাক অনেক।
একদিন শাহজাহান আমাকে ডেমরাতেও বেড়াতে নিয়ে গেলো। সেখানে ডাক্তার সাহেব ও তার স্ত্রীর অষ্টপদ ব্যঞ্জনের আয়োজন আমাকে কিছুটা বিস্মিতই করেছিলো।
যাহোক, দেখতে দেখতে তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যে যার সিঙ্গেল রুম পেয়ে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কিন্তু একই ফ্লোরে হওয়ার পূর্বের বন্ধুত্ব ও মেলামেশা অটুট রইলো। এর মধ্যে আমাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তখন ১৯৬৫ সাল। অনার্স পরীক্ষা দেবার সাথে সাথেই আমাদেরকে চার সিটওয়ালা রুম বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়। একক রুমে থাকা অবস্থায় একদিন আমার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই কাজী গোলাম মোস্তফা (ওরফে মটু) হঠাৎ করেই বেডিং-বোচকা নিয়ে আমার শরণাপন্ন হলো। ও থাকতো মতিঝিল সরকারি কর্মচারীদের ফ্লাট বাড়িতে, মটুর একমাত্র আপা-দুলাভাইয়ের কাছে। তাদের সংসার বেশ বড়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। অথচ, সরকারি ফ্লাট বাড়িগুলোতে কেবলমাত্র দুটি শোবার ঘর, একটি বসার ঘর, আর একটি রান্নাঘর। মটুর দুলাভাই ঢাকা কেন্দ্রীয় ডাকঘরে ক্লারিক্যাল পদে ছোটখাটো একটা চাকরি করতেন।
আমি মটুকে না করতে পারলাম না। কারণ, শৈশবে ওকে আমিই প্রথম হাত ধরে পাঠশালায় নিয়ে গিয়েছি। যখন ওর বাবা শহর থেকে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলো।
মটু বললো- আমার বিএসসি পরীক্ষা শেষ হলেই আমি চলে যাবো। আমি ফ্লোরিং করেই কাটাতে পারবো।
একদিন সকালের নাস্তা শেষ করে সবে বেরিয়েছি। দেখি মটুর দুলাভাই, শিকদার সাহেব, হলের গেটের বাইরে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বললেন- এনায়েত। একটু এদিকে আসবে, ভাই। তোমার সাথে আমার একটা পরামর্শ করার আছে।
আমি শাহজাহানকে বললাম- তুমি এগোতে থাকো শাহজাহান। আমি উনার সঙ্গে কিছু আলাপ করে আসছি।
শাহজাহান গেট দিয়ে হলের মধ্যে ঢুকে যাবার পর আমি শিকদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম
-আসসালামু আলায়কুম। কী দুলাভাই? কি বিষয়ে পরামর্শ করতে চান?
-আমি খুব বিপদে পড়েছি ভাই! মটুর পরীক্ষার ফি দিতে হবে ৩৫ টাকা। অথচ, আমার হাত একদম খালি। সময়মত ফি জমা দিতি না পারলি মটুতো পরীক্ষা দিতি পারবে না নে। তুমি কী ভাই আমারে ৩৫ টাকা দিয়ে আমার মুখ রক্ষা করতি পারবা।
-ঠিক আছে দুলাভাই। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে আমার বৃত্তির টাকা থেকে ৩৫ টাকা এনে দিচ্ছি।
আমি হলরুমে গিয়ে টাকা এনে শিকদার সাহেবের হাতে দিলাম।
-আল্লাহ তোমার অশেষ ভালো করুক। কিন্তু ভাই, একটা বিশেষ অনুরোধ, ব্যাপারটা যেনো অন্য কেউ না জানতে পারে। এমনকি আমার শালা গোলাম মোস্তফাও না!
আমি কথা রেখেছিলাম।
১৯৬৫ সাল। আমাদের ৩য় বর্ষ সম্মান পরীক্ষার থিওরি পেপারগুলো সবে শেষ হয়েছে। ব্যবহারিক পরীক্ষার রুটিন মোতাবেক রাত পোহালেই, সকাল ১০টা থেকে, শুরু হবে। একক রুম থেকে শিফট করে সবেমাত্র অন্য দু’জন অপরিচিত ছাত্রের সঙ্গে আমি আর শাহজাহান আবার একত্রিত হয়েছি। আমাদের অপর দু’জন হলমেটের একজন কলা ও মানবিকী অনুষদের এবং অপরজন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র। এরা দু’জনই নির্ভার, নিশ্চিন্তে এবং ফুরফুরে মেজাজে ঘোরাফেরা ও রুমে আসা-যাওয়া করছে। কারণ, এদের কারোরই ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয় না। আমি প্রমাদ গুনছি অসংখ্য উদ্ভিদ নমুনাগুলোকে জমা দেবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় শেষ ধাপের কাজগুলো শেষ করতে। কারণ, সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই দীর্ঘ (৭ দিনব্যাপী) ফিল্ড ট্রিপ থেকে জড় করা, এগুলোকে সঠিকভাবে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে রেখে চাপযন্ত্র দিয়ে চাপা দেবার মাধ্যমে এবং মাঝেমধ্যে রৌদ্রতাপ দিয়ে শুকিয়ে পরে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করা ছিল। এখন শুধু নমুনাগুলোকে আঠা লাগিয়ে হারবেরিয়াম শিটের উপর আটকানো বাকি। সেই সাথে নমুনার সংখ্যা, আহরণের স্থান, ফুল ও ফল সম্পর্কে কোনো তথ্য, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি ফিল্ড নোটবুকে লিখে দিতে হবে। কারণ, সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনা ও ফিল্ডনোট বুক উভয়ের জন্য পৃথক নম্বর বরাদ্দ আছে। মনে মনে প্ল্যান ছিলো যে, রাত জেগে এসব টুকটাক কাজগুলো সম্পন্ন করে ফেলবো। কিন্তু বিধিবাম! ১৯৬৫ সালে হঠাৎ করেই পাকিস্তান-ইন্ডিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যদিও যুদ্ধের তান্ডব চলছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে, কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় শুরু হলো ব্লাক-আউট। সারা শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন। মাঝেমধ্যে আকাশে যুদ্ধ বিমানের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এনএসএফ-এর নেতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র-নামধারী গুন্ডারা সারা হলে পায়চারি করছে। কোথায়ও কোনো জটলা হচ্ছে কিনা কিংবা কোনো রুমে আলো বা হ্যারিকেন জ্বলছে কি না, নজরদারী করছে। আমি পাগলের মত হয়ে কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করছিলাম। তাও একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে। হঠাৎ দু-তিনজন এনএসএফ নেতা আমাদের ঘরে ঢুকে হুঁঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো- কার এতো সাহস যে, রুমে আলো জ্বালিয়ে কাজ করছে?
আমি মুখটা কাঁচুমাচু করে ওদেরকে অনুরোধ করলাম
-মোমবাতির আলো তো বাইরে যাবে না, ভাই। আমার ৩য় বর্ষ সম্মান পরীক্ষার আগামীকাল ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে। আমাকে দয়া করে ঘন্টা-দু’য়েক সময়ের জন্য কাজ করতে দিন না।
-না, না! কেউই কোনোরকম বাতি বা আলো জ্বালাতে পারবে না।
এ কথা বলে নেতারা নিজেরাই মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেলো। আমি কিছুই করতে পারলাম না। শুধু চোখ দুটো অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠলো।
আমার হতাশাগ্রস্থ অবস্থা দেখে রুমমেট পেয়ারা (ইংরেজী বিষয়ের ছাত্র) এবং অর্থনীতির ছাত্র ওয়জিউল্লাহ বললো
-রুমমেট! চিন্তা করবেন না। আপনি সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন। ভোরে উঠে আমরা সবাই মিলে আপনার বাকি কাজগুলো শেষ করে দেবো।
আমি যেন অথৈ পনিতে একটা কূল-কিনারা দেখতে পেলাম। সময়ও পানির স্রোতকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারে না। জীবন ধারাও প্রবাহিত হয়ে চলে। তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে প্রথম স্থান দখল করেই এসএম হলের দোতলায় পশ্চিম কোণে একটা চার সিট ওয়ালা রুমে আমরা শিফট হয়েছি সাবেমাত্র। এসময় বিভাগে যেনো ছাত্রছাত্রীদের বন্যা এলো। বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েটেড ডিগ্রি কলেজ থেকে পাশ করে কমপক্ষে ২০-২৫ জন ছাত্রছাত্রী এমএসসি প্রিলিমিনারিতে ভর্তি হলো। ফাইনাল ইয়ারে আমরা এক সাথেই ক্লাশ করা শুরু করলাম। মজার বিষয় এই যে, আমাদের সবাইকেই থিসিস বা প্রোজেক্ট ওয়ার্ক নিতে হলো বিভাগের বিভিন্ন শাখায়। প্ল্যান্ট ট্যাক্সেনমিতে সদ্য যুক্তরাজ্য ফেরৎ ড. মো. সালার খান-এর তত্ত্বাবধানে আমরা মোট ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা কাজ করছি। তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. মজিদ আহমেদ-এর জেনিটিক্স ও ব্রিডিং শাখাতেও প্রায় ৮ জন ছাত্রছাত্রী। ড. কাজী আব্দুল ফাত্তাহর উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানে ৫/৩জন ছাত্রছাত্রী। ড. মো. নরুল ইসলামের অধীনে ৪/৫ জন। আর বাকি কয়েকজন তরুণ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এক বা দুজন ছাত্রছাত্রী থিসিস নিয়ে কাজকর্ম শুরু করেছে।
তখনকার সমাজ-সংস্কৃতি যুবক-যুবতীদের খোলামেলা মেলামেলা ও প্রেম নিবেদনকে খোলা মন নিয়ে গ্রহণ করেনি। ধর্মীয় বাধা-নিষেধ ছাড়াও এসব কর্মকান্ডকে সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। তথাপি আমাদের সতীর্থদের মধ্যেই কমপক্ষে তিন-চার জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা এবং প্রেমালাপ চলতে দেখেছি। এদের মধ্যে রুবি-মতিউর এবং মীরা-লাইচ জুটি অন্যতম। প্রথম জুটি আমারই শাখার এবং দ্বিতীয় জুটি উদ্ভিদ শারীর বিজ্ঞান শাখায় পাঠরত।
সপ্তাহে দু’দিন সময় পেতাম থিসিসের কাজ করার জন্য। উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত (চাপন যন্ত্র দিয়ে ফোল্ডারের পর ফোল্ডার সাজিয়ে চাপ ও তাপ দিয়ে শুষ্ক করা) এবং ফিল্ড নোটবুকে প্রত্যেকটি নমুনার টুকিটাকি তথ্যাবলী রেকর্ড করতে হতো। ট্যাক্সেনমি ল্যাবে ছুটির দিনে এবং অন্যান্য ক্লাশ-চলার দিনগুলোতে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত কাজ করার সুবিধা পাবার জন্য আমরা প্রত্যেকে একটা করে ডুপ্লিকেট চাবি পেয়েছিলাম। সচরাচর আমি বেশ দূরে অবস্থিত এসএম হলে থাকার কারণে ছুটির দিনগুলোতে ল্যাবে এসে কাজ করতাম না। কিন্তু একদিন সংগৃহীত নমুনাগুলোকে ফোল্ডার পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিন তিনতলায় অবস্থিত ল্যাবে উপস্থিত হয়ে দেখলাম দরজার কপাট দুটো আলতো করে লাগনো! কড়াতে বড় তালাটা বদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে। আমি দরজার কপাট দুটো খুলে সবেমাত্র ভিতরে পা রেখেছি, তখনই মতিউর, দেখতে সুঠামদেহী এবং কালা পাহাড়ের মত, বৃন্দাবন কলেজ হবিগঞ্জের স্নাতক ছাত্র কটাক্ষ করে বলে উঠলো
-এনায়েত। তুমি ছুটির দিনেও ল্যাবে এসেছো কাজ করতে? তোমার ফাস্ট ক্লাশতো বাঁধাই আছে। তাহলে আর আমাদেরকে বিরক্ত করা কেনো? ছুটির দিনে নিরিবিলি আমরা দু’জন একটু আলাপ-সালাপ করবো, তাও করতে দেবে না!
-মতিউর, স্যরি ভাই! আমি তো সাধারণত ছুটির দিনে ল্যাবে কাজ করি না। কিন্তু গত শুক্রবারে স্থানীয়ভাবে কিছু সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করে চাপন যন্ত্রে রেখে গিয়েছিলাম। এগুলোর ফোল্ডার কাগজগুলো আজ না পাল্টালে সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এসেছি ঘণ্টাখানেকের জন্য তোমাদের দু’জনকে বিরক্ত করতে। কিছু মনে করো না মতিউর। ফোল্ডার কাগজগুলো পাল্টিয়েই আমি চলে যাবো।
রুবি একটু লজ্জিত হয়ে মতিউরকে আর কথা না বাড়াতে বারণ করলো। ব্যাপারটির এখানেই ইতি। কপোত-কপোতীর বক-বকুম করায় সাময়িক ছেদ পড়লো।