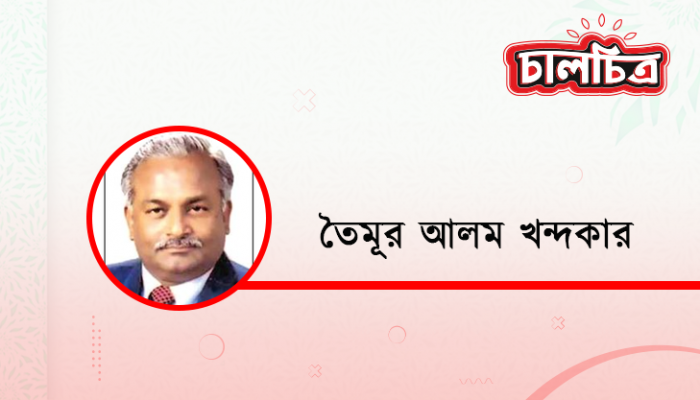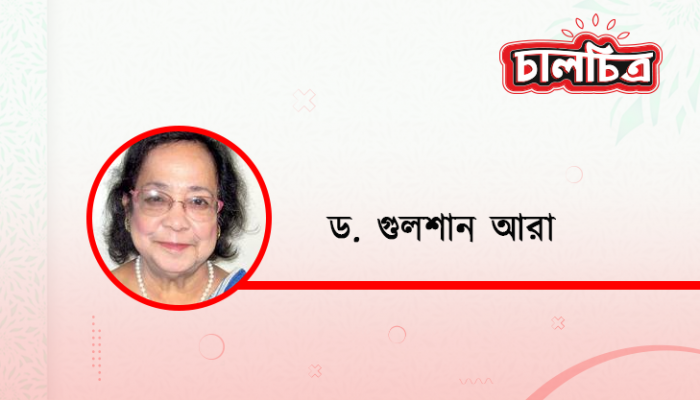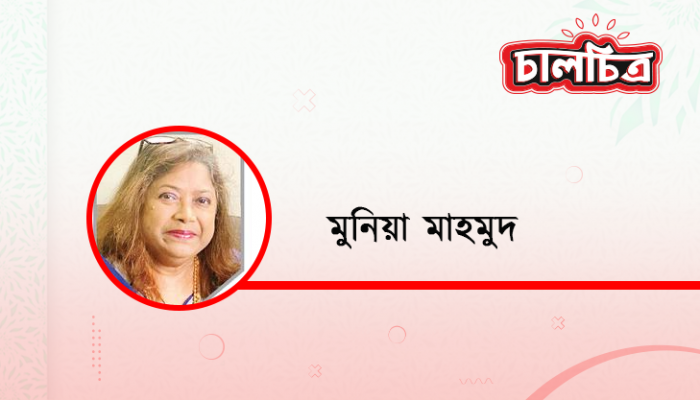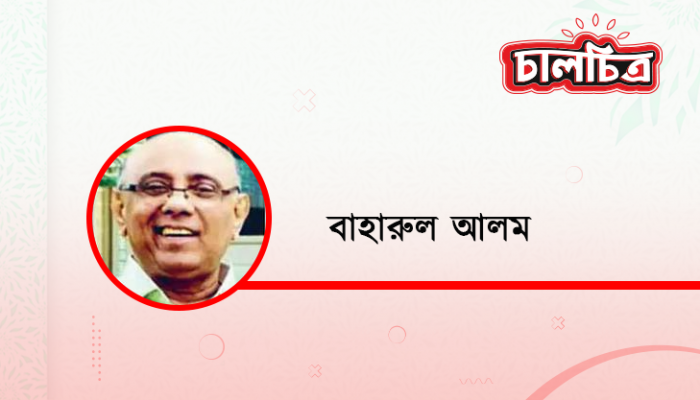লোকে বলে ‘আদালতই’ অসহায় নিপীড়িত নির্যাতিত আশ্রয়হীন মানুষের শেষ আশ্রয়। অন্যদিকে চলার পথে রাস্তা- ঘাটে, বাসে-ট্রেনে বিভিন্ন জায়গায় ‘বিবেকই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদালত’ লেখাগুলো চলার পথে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, মানুষ কি তার বিবেক দ্বারা চালিত?ৎ
‘আদালত’ শব্দটির সাথে ‘আইন’ শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসাবে যেমন সম্পর্কিত, ঠিক তেমনি আইন প্রয়োগ যদি বিবেকসম্পন্ন না হয়, তবে সে বিষয়টি ইতিহাসে কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করে।
আদালতের দায়িত্ব কী? আদালতের মূল দায়িত্ব হলো- অপরাধীকে চিহ্নিত করে আইন মোতাবেক শাস্তি নির্ধারণ করা। তবে বিচারের সাথে ‘ন্যায়’ শব্দটি সম্পৃক্ত, অন্যথায় ‘ন্যায়’ বিহীন ‘বিচার’ হবে অবিচারেরই নামান্তর।
এখন প্রশ্ন হলো- অপরাধ কি? কি করলে বা না করলে অপরাধ হয়? সংজ্ঞা বলে ‘Breaking of law is offence’, অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করার নামই অপরাধ। কোনো কাজ করে বা না করেও (Commission or Omission) আইন ভঙ্গ হয়। অপরাধী চিহ্নিত করা বা পরিমাপের স্কেল হলো ‘আইন’।
এখন প্রশ্ন হলো- আইন কি? আইন কিভাবে প্রণীত হয়? আইনের সৃষ্টিকর্তা কে? উল্লেখ্য, আইন প্রণয়ন বা সৃষ্টি করার অধিকারী শাসক গোষ্ঠী। বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসক গোষ্ঠীর আইন সৃষ্টির পদ্ধতি ভিন্ন রকম। রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে ‘জোর যার মুল্লক তার’ পদ্ধতিই ছিল আইন সৃষ্টির ব্যাকরণ, বা Juries prudence। বাহুবল, অস্ত্রবল বা জনবলে যে শক্তিশালী, সেই হতো সংশ্লিষ্ট গোত্রের সর্দার এবং তার ইচ্ছাই ছিল আইনের উৎস। তখন মানুষ বনে-জঙ্গলে-গুহায় বাস করতো। পাথর ঘসে আগুন জ্বালিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করতো।
সভ্যতার ক্রমবিকাশে পাহাড়ের গুহা বা ঝোঁপ-জঙ্গল থেকে মানব জাতি চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র বিজয় করে এখন অন্য গ্রহে যাওয়ার গবেষণায় লিপ্ত। পৃথিবীর কোটি কোটি জনগোষ্ঠী গৃহহীন, বাস্তহারা হয়ে নিজ দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে শরণার্থী (রিফিউজি) হয়ে খোলা আকাশের নিচে বা তাঁবু টাঙিয়ে রাস্তার পাশে ময়লার ভাগাড়ে অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটানোর ছবি প্রায়ই মিডিয়াতে আসছে। এ রকম দৃশ্য আমেরিকাসহ পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায়। খাদ্যান্বেষণে কাঠের নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিতে সলিল সমাধি হওয়ার খবরও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইসরাইলি আগ্রাসনে গাজায় শিশুহত্যা এখন প্রতিদিনের ঘটনা।
অন্যদিকে খাদ্যহীন ছিন্নমূল মানুষকে পূণর্বাসনের পরিবর্তে প্রাণঘাতী অস্ত্রসহ পরমাণু বোমা তৈরিতে মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার খরচে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষের কোলে, বাড়িতে, বিছানায় কুকুর/বিড়ালের স্থান হচ্ছে, অথচ অনাহারে এখনো ঘুমাতে যায় কোটি-কোটি মানুষ। তারপরও মানুষ সভ্যতার উচ্চ শিখরে পৌছার দাবিদার!
মানুষ যখন পাহাড়ে/জঙ্গলে বাস করতো, তখন যেমন ‘জোর যার, মুল্লক তার’ সংস্কৃতি চালু ছিল; সভ্যতার এ যুগেও ঐ নীতিমালার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মানবতার লংঘনকারীই মানবতা রক্ষায় অভিভাবকের দ্বায়িত্ব নিচ্ছে। খুনি নিজেই নেতৃত্ব দেয় শোক মিছিলের!
শাসনকর্তা আইন প্রণয়ন করে। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এক কথা নয়। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ উভয়ই শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। আইন প্রণয়নের সময় বলা হয় জনস্বার্থে করা হচ্ছে। কিন্তু আইন কি কোনদিন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয়? আইন প্রয়োগের level playing filed কোথাও নেই, বিশেষ করে বাংলাদেশেতো আনুষ্ঠানিকভাবেই নেই। বাংলাদেশে যার টাকা ও ক্ষমতা আছে, তার পায়ের নিচে আইন গড়াগড়ি খায়। আইন প্রয়োগকারীরা সেই সমাজপতিকে কুর্নিস করে এবং এভাবেই ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় সমাজে সৃষ্টি হয় শোষক শ্রেণি আর সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জন্ম নেয় শোষক শ্রেণির সেই কারখানা থেকে।
আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন ‘আইন অন্ধ’- কথাটি সম্পূর্ণ অসত্য। আইনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রয়োগকারী। আইন প্রয়োগকারী যখন বিবেকের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেন, তখনই শুরু হয় আইনের অপপ্রয়োগ।
শাসকের শোষণ-অত্যাচার, নির্যাতন-অবিচার থেকে বাঁচার জন্য যুগ যুগ আন্দোলনের পর বিচার বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। বিচারের জন্য আদালতের কেনো প্রয়োজন ছিল- এটাও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রাচীনকাল থেকেই রাজা বা শাসনকর্তা বা গোত্র প্রধানদের সিদ্ধান্তই ছিল আইন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রজা বা নাগরিকদের অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার জন্যই বিচার বিভাগের সৃষ্টি।
এজন্য Megna Carta, Bill of Right, Right to Petition আন্দোলনের অবদান রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেই শাসন বিভাগের পাশাপাশি পৃথক বিচার বিভাগ রয়েছে। পূর্বে বিচার ব্যবস্থার সাথে বর্তমান ব্যবস্থার ব্যতিক্রম রয়েছে। বৃটিশ বিচার ব্যবস্থায় দেখা যায়, বিচারের শাস্তি নির্ধারণ করার প্রশ্নে বিচারকের স্বাধীনতা ছিল, যা থেকে Common Law বিচারিক পদ্ধতির সৃষ্টি।
Customary Law অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণি গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা প্রথা বা নিয়ম-কানুনের ভিত্তি ছিল Common Law-এর উৎস। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শাসক গোষ্ঠী সময়ে সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারকের হাতকে সংকুচিত করে দেয়।
আইনে নির্ধারিত হয় অপরাধের সংজ্ঞা, পদ্ধতি এবং শান্তির পরিমাণ। যেমন- আইনে সাজার পরিমাণ সবোর্চ্চ ও সর্বনিম্ন নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিচারিক সিদ্ধান্তে সাজার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আইনই পথ নির্দেশক, বিচারক নয়।
এখন প্রশ্ন হলো- ‘ন্যায়’ কি বা ‘ন্যায়’ বলতে কি বোঝায়? ন্যায়পরায়ণতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Equity. রোমান শব্দ Acquitas থেকে Equity শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা শব্দার্থ হলো- সমকক্ষ, সমান। কিন্তু বাংলার এই Equity-এর চেতনাকে ধারণ করে না। বরং একজন অপরাধীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অপরাধ সংগঠনের Background তথা অপরাধী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদানে অপরাধীর সক্ষমতা ছাড়াও ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কারণে সামাজিক প্রতিফলন, Balance of Convenience and Inconvenience ন্যায়বিচার করার উপাদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। যা শুধু আইনভিত্তিক হওয়া সমীচীন নয়।
২৫০ বৎসর আগে ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Cesare Bonenana DI Beccaria-এর প্রণীত ‘On Crimes and Punishments’ বইতে বলেছেন- ‘ক্ষেত্র বিশেষে আইন ও আদালত নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।’
আইন নির্ধারিত বিচার ব্যবস্থার পরও অনানুষ্ঠানিক একটি বিচারিক প্রক্রিয়া পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই চালু হচ্ছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে যা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নামে ব্যাপক পরিচিত। পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়ভিত্তিক বিচারিক সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পায়। আপোষ-নিষ্পত্তিমূলক সামাজিক বিচার ব্যবস্থার Update সংস্করণ পদ্ধতি হলো- মেডিয়েশন (Mediation), যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে শান্তিপূর্ণ ও দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। সাধারণত বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর আইনের ছকে বাঁধা। প্রচলিত আইনি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করতে অনেক দেরি হয়। ফলে মামলায় জড়িতদের ওপর একদিকে যেমন মানসিক চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির Concept চালু হয়েছে।
এ পদ্ধতি পশ্চিমা বিশ্বে Restorative Justice (R.J) এবং বাংলাদেশে Alternative Dispute Resolution (ADR বলে পরিচিতি। আইনগত কিছু উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়াও ঈ.ঔ বা অউজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণে বিরাট অবদান রাখছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বন্ধনও সুদৃঢ় হয়। পঞ্চায়েত বিচার ব্যবস্থার আদলে বর্তমান বিশ্বে Victomology and Mediation বা মধ্যস্থতা তথা আপোষ-মিমাংসার মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টাতে সমাজ হিতৈষী মহলের চেষ্টা এখন অব্যহত রয়েছে।
এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আইন ও ন্যায় যদি পরস্পর সাংর্ঘষিক হয়, তখন বিচারক কোনটিকে প্রাধ্যন্য দেবেন? আইনতো পরিবর্তনযোগ্য। রাজা আসে রাজা যায়, সরকার আসে সরকার যায়, আইন নিজেও পরিবর্তন হয়। এমন কি নিজের করা আইন নিজেরাই পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন, স্থগিত, বিলুপ্ত প্রভৃতি আইন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন বা ইচ্ছা মাফিক করা হয়। কিন্তু ‘ন্যায়’ কি পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংযোজন বা সংশোধন যোগ্য?
বিচারক যদি ‘আইনের’ কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে ‘ন্যায়ের’ প্রতি দায়বদ্ধ কেনো নয়?
আইন ও ন্যায়পরায়ণতা (law and equity) সম্পর্কে বিভিন্ন আইন, Jurist Black Stone বলেছেন, ‘ন্যায়পরায়ণতা অন্যান্য আইনের আত্মা ও শক্তি’।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Plato-এর মতে, ‘ন্যায়পরায়ণতা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের সেই অংশ, যা সাধারণ আইনের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো পরিপূর্ণ করে।’
ন্যায়পরায়ণতা হলো মানুষের সুবিবেচনা, সততা, নিরপেক্ষতা, যা একজন বিচারককে ন্যায়বিচারে উৎসাহী করার কথা।
পবিত্র কোরআনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাক বলেছেন, ‘বলো- আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন।’ (সুরা আরাফ-২৯)। ‘আর আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা সঠিক পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে।’ (সুরা আরাফ- ১৮)।
জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলতেন, ‘বাংলাদেশে হাওয়া বুঝে মামলার রায় হয়।’ বিচার বিভাগের ওপর জনগণের আস্থা কতটুকু আছে, তা তারাই (বিচার বিভাগ) ভালো বলতে পারবেন। শুধু জনগুরুত্বপূর্ণ বিচারিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রধান বিচারপতিসহ বিচারপতি নিয়োগ, হাইকোর্টে বেঞ্চ গঠন, আইনজীবীদের সিনিয়রিটি প্রদানের বিষয়টিও নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। তবে অতিসম্প্রতি বিচারপতি নিয়োগে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁবেদারিতে সম্মান রক্ষা হয় না, বরং কালের বিবর্তনে পদদলিত হতে হয়। বিচার বিভাগের এ অসহায়ত্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য কে দায়ী? জাতির কাছে এ ব্যাখ্যা কে দেবেন?
বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতিসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের হাতে Hand cup দেখেছি। এখন একজন প্রধান বিচারপতিকে পিঠ মোড়া (দুই হাত পিছনে দিয়ে) Hand Cup অবস্থায় দেখছি। একজন প্রধান বিচারপতিকে গলাধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে তাড়ানোর দৃশ্যও দেশবাসী দেখেছে। এ দৃশ্য যেমন কাঙ্খিত নয়, অন্যদিকে ‘যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ’- এ সংস্কৃতির পরিণতি কি হয়, তাও উপলব্ধি করার বিষয়।
রাজনীতিবিদরা ১/১১ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, জুলাই/৩৬ থেকে আমাদের শিক্ষা হবে কি? ক্ষমতার অপব্যবহার-অন্তে মবজাস্টিস পাশাপাশি চলছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কথায় বলে- ‘কারো ভাদ্রমাস, কারো সর্বনাশ’। জুলাই চেতনা কারো জন্য Money Making Source হয়ে যাওয়ায় বিষয়টিও জনগণ প্রত্যাশা করে না। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। বাংলাদেশে কি কখনো প্রকৃতভাবে আইনের শাসন কায়েম হবে? নাকি ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চাই’- এ মহামূল্যবান শ্লোগান শুনতে শুনতে দিন পার হয়ে যাবে? আইন দ্বারা বিচার বিভাগ কোনদিনই স্বাধীন হবে না, যদি বিচারক নিজেকে নিজে স্বাধীন মনে না করেন। আমরা কি আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন করতে ভূলে যাচ্ছি? ঋতুর পরিবর্তন হয়, আকাশের রং বদলায়, কিন্তু বাঙালির ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না কেনো? বাঙালি আর কত রক্ত দেবে? আগে গায়েবি মামলার কষাঘাতে এ জাতি ছিল জর্জরিত, তার স্থলে এখন আবির্ভূত হয়েছে ‘মামলা বাণিজ্য’। প্রকৃত দোষীদের শাস্তি কামনা করি, কিন্তু ‘মামলা বাণিজ্য’ ‘গায়েবী মামলায়’ নামান্তর বিধান সমর্থন যোগ্য নয়।
ক্ষমতার হাত পরিবর্তন হলেও জনগণের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। একই আইন ক্ষেত্রমতে প্রয়োগ হচ্ছে ভিন্নভাবে। এ মর্মে পূর্বের মতই বিচার বিভাগ এখনো নীরব দর্শক।
লেখক : কলামিস্ট ও সিনিয়র আইনজীবী।




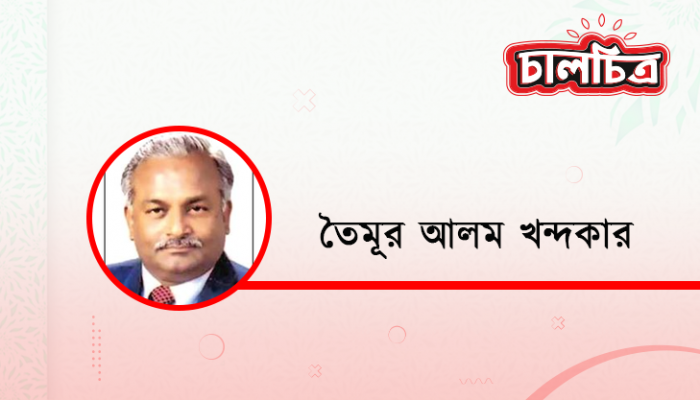 তৈমূর আলম খন্দকার
তৈমূর আলম খন্দকার