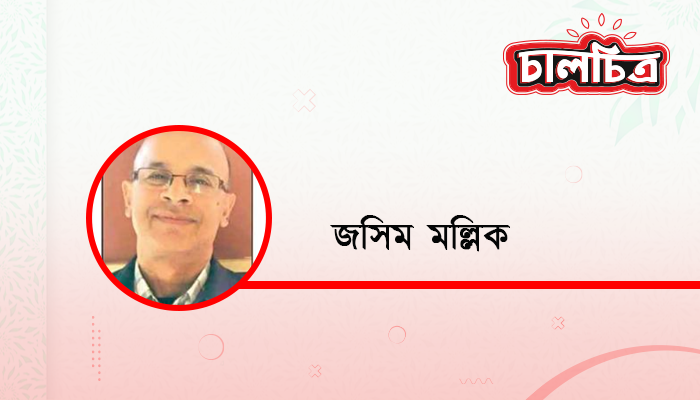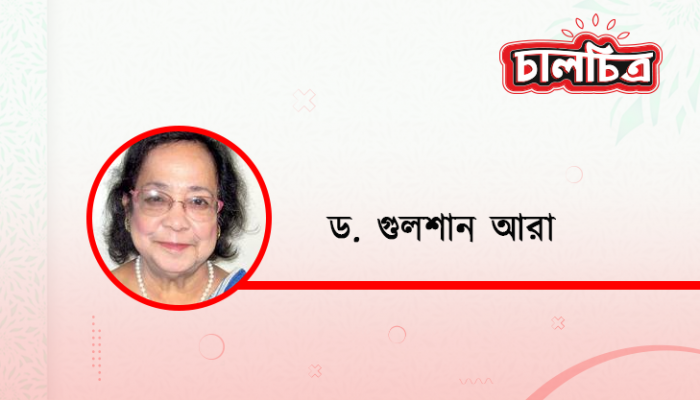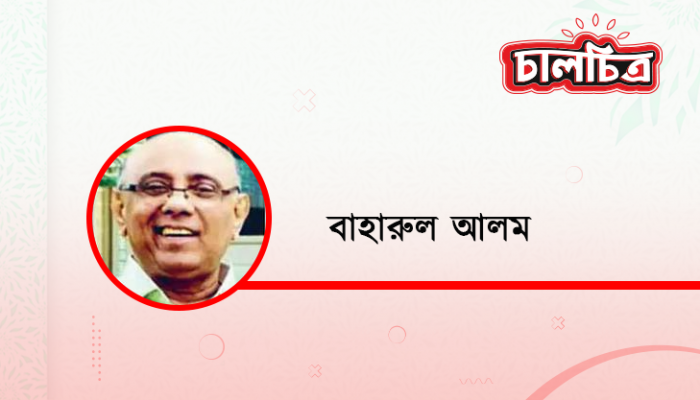বিদেশে এসে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ২২ বছর বিদেশে থেকে যা অর্জিত হয়েছে, তা সারা জীবন দেশে থেকেও অর্জন করতে পারিনি। আরও যত দিন থাকব তত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে। অভিজ্ঞতার ঝুলি উপচে পড়ছে। মাঝে মাঝে ভাবি এত অভিজ্ঞতা কোথায় রাখব। অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেছি। একটা কনসালট্যান্সি খুলে বসলে ভালো করব বলে আমার বিশ্বাস। অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। মানুষ তো আর নির্বিকার থাকতে পারে না। তাকে কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো কিছুতে অংশ নিতেই হয় এবং অর্জিত হয় নানা কিসিমের সব অভিজ্ঞতা। আমি কখনো জানতাম না যে একদিন আমি বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘাঁটি গাড়ব। বিদেশপ্রীতি বলতে যা বোঝায়, তা আমার নেই। অন্যত্র বসতি স্থাপনের সবিশেষ কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি আজ বিদেশে বসে অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি। কোনো অভিজ্ঞতাই বৃথা যায় না, সবকিছুই মূল্যবান...।
প্রথম প্রথম অনেকেই জানতে চাইত আমি কেন বিদেশে এলাম। কেন এলাম এর একটা ব্যাখ্যাও আছে। জানি, এটা এখন আর কেউ জানতে চায়নি। এসব নিয়ে আজকাল কেউ মাথাও ঘামায় না। কতজন আসে কতজন যায়, কে তার হিসাব রাখে। এটা ঠিক, আমি দেশ-বিদেশ ঘুরতে পছন্দ করি। লাসভেগাস থেকে লেছড়াগঞ্জ ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। কিন্তু কখনো ভাবিনি যে বিদেশ হবে আমার ঠিকানা। আমি কি আবার আমার ঠিকানা বদল করতে পারব? আমি কি আবার ফিরে যেতে পারব সেই ছায়া সুনিবিড় বরিশালের বাড়িতে, যেখানে রয়েছে আমার মা আর বাবার কবর? পারব কি ফিরতে? আবার কি প্রথম থেকে সব শুরু করা যায়?
আমি একদিন আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি যে প্রায় ২৬ বছর এই দেশে এসেছ, একবারও দেশে যাওনি। কেন গেলা না! তোমার তো মা-বাবা রয়েছেন দেশে। তোমার কি তাদের দেখতে মন চায় না! সে নির্বিকার উত্তর দিয়েছিল, আমার মন টানে না। আমি তাকে আর বলিনি যে আমি গত ২২ বছরে ২০ বার দেশে গিয়েছি। আমি বলিনি যে মা-বাবা চলে গেলে আর ফিরবে না। যে যায় সে আর ফেরে না। এই যে আমি বছর বছর দেশে গিয়েছি মায়ের পাশে একটু বসে থাকার জন্য, এখনো যখন রাত গভীর হয় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। মা ভাবে আমার জাদু চলে যাচ্ছে। আর কি দেখবে আমাকে! ভাবি মায়ের জন্য কত কী করার ছিল, কিছুই তো করলাম না। মায়ের পাশে আরও বেশি বেশি থাকতে পারতাম , থাকলাম না তো! মা যখন চেতন ও অবচেতনের মাঝামাঝি, তখন একদিন আমাকে বলেছিল, তুমি কেন বিদেশ গেলা! নিজের দেশ ছেড়ে কেউ যায়!
মানুষ হিসেবে আমি কেমন! এই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন। আমি কষ্টেসৃষ্টে বেড়ে ওঠা মানুষ। এটা ঠিক যে আমার সঙ্গে কারও কোনো আর্থিক লেনদেন নেই। আমি কখনো কাউকে ঠকাইনি। কারও কাছ থেকে টাকা ধার নিইনি। আমি যথাসময়ে সব বিল পরিশোধ করি। এগুলো হচ্ছে একটা অভ্যাসের ব্যাপার। অনেকেই করে। শুধু আমার যারা খুব কাছের, তাদের মাঝে মাঝে কষ্ট দিই, খেয়ালিপনা করি, রাগ দেখাই, নির্বিকার থাকি। জানি, তারা এটা মেনে নেবে। জেনেশুনে কারও ক্ষতি করিনি। তবে জীবনে অনেক ভুল করেছি। ভুলগুলো বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ভুগেছি, ভুল শুধরানোর চেষ্টা করেছি।
বিদেশে কেন এলাম-এই ব্যাখ্যাটা খুব কমন। সেকেলে। অনেকেই এই ব্যাখ্যা দেয়। বেশির ভাগ মানুষই বলে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য বিদেশে এসেছি। এটা বললে আবার অনেকে খেপে যায়। হইছে আর ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দোহাই দিতে অইবে না। আইছে নিজের স্বার্থে, এখন কয় ছেলেমেয়ের জন্য! আমার বিদেশ আসার কারণ একটু ভিন্ন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপার যদি বলতে হয় তাহলে আমার দায়িত্ব মোটামুটি শেষ। আমার ছেলে ও মেয়ে দুজনই টরন্টো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়া শেষ করে চাকরি করছে। সংসার হয়েছে। যে যার মতো থাকছে। আমার পাশেও নেই তারা। আবার একলা হয়ে গেছি। দুজনের সংসার শুরু হয়েছিল। আবার দুজন। ওদের লেখাপড়া নিয়ে আমি কখনো চিন্তিত ছিলাম না।
আমি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে চাইনি। আমি একটু জেদি, একরোখা! আমার জেদ অনেক কিছুই আমাকে পেতে দেয়নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমি অনেক ভুগেছি। দেশে থাকতে আমি কয়েকবার চাকরি ছেড়েছি। চাকরি ব্যাপারটাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু চাকরিই আমার ভরসা। এর বাইরে কিছু করার যোগ্যতা আমার নেই। কিছু মানুষ জন্মায়, যারা আমার মতো। নিজেকে ঠিকঠাকমতো যারা গুছিয়ে উঠতে পারে না। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই যাদের সময় চলে যায়। আমি হচ্ছি স্বপ্নবাজ। স্বপ্ন আছে বলে আমি বেঁচে থাকি। স্বপ্নরা সারাক্ষণ ওড়াউড়ি করে...।
চিঠির আবেদন কি হারিয়ে যাবে!
আচ্ছা, ডাক বিভাগ কি বন্ধ হয়ে যাবে? আজকাল এই প্রশ্নটি উঠছে। একমাত্র অফিশিয়াল চিঠি আর পার্সেল আদান-প্রদান ছাড়া ডাক বিভাগের আর কি কোনো ভূমিকা থাকবে? ইন্টারনেটের যুগে এসে এই প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফেসবুক বা টুইটারের মতো বিশাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কারণে হাতে লেখা চিঠির কথা মানুষ ভুলতে বসেছে। আমি নিজেই একসময় হাজার হাজার চিঠি লিখেছি। আমার ছিল অসংখ্য পত্রবন্ধু। পত্রলেখক হিসেবে আমার একটা খ্যাতি হয়েছিল। কই এখন তো আর আমি ডাক বিভাগের মাধ্যমে চিঠি লিখি না! এখন আমার দিনের অনেকটা সময় চলে যায় ফেসবুকের পেছনে। এমনকি আমার লেখালেখিরও ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেসবুক। হয়তো একসময় ফেসবুকও তার আবেদন হারিয়ে ফেলবে। আবার যেন মানুষ হাতের লেখা চিঠিতে ফিরে যায়। নতুন প্রজন্ম তো জানেই না একসময় মানুষ হাতে চিঠি লিখত!
প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ চিঠি লেখে কেন? চিঠি হচ্ছে ব্যক্তিমানুষের প্রকাশ। মানুষ তার নিঃসঙ্গতা, অনুভূতি, তার মনোভাব অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে চায়। চমৎকার বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যকে মুগ্ধ করতে চায়। কথার আবেদন চিরকালই থাকছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক কিছু বদলে যায়। এগিয়ে চলে বিশ্ব। হাইটেকের বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজ। ই-মেইল, ইন্টারনেট আর চ্যাট বক্সেরই এখন যুগ। হাইটেকের বিশ্ব অবশ্য গতি আর বেগ দিয়েছে, কিন্তু আবেগের জন্য আজও মানুষকে বেছে নিতে হচ্ছে ডাক বিভাগকেই। মনস্তাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন, এখন পর্যন্ত হাতে লেখা পত্রটিই মানুষের কাছে লিখন ও পঠনগত দিক থেকে অধিক আবেগপূর্ণ। মনস্তাত্ত্বিকদের ধারণা, অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা খবর আদান-প্রদান অনেক বেশি কার্যকর কিন্তু আবেগ আর মানসিক সম্পর্কের জন্য এখনো পত্র নামক বস্তুটিই বিশ্বের জনপ্রিয়তায় এগিয়ে।
চিঠি কখনো কখনো হয়ে উঠেছে পত্রসাহিত্য। সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন কোনো কোনো মনীষী লেখক। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র একটি উঁচুদরের সাহিত্য। ১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, ছিন্নপত্র প্রধানত তারই সংকলন। বহু চিঠিই রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেননি। অনেক চিঠির কোনো কোনো অংশ সাধারণের সমাদরযোগ্য নয় মনে করে বর্জনও করেন। বর্জিত অনেকগুলো পত্র এবং পত্রাংশ মূল খাতা দু’খানি অবলম্বনে ১৯৬০ এর অক্টোবরে ‘ছিন্ন পত্রাবলী’ নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, তাতে পাওয়া যায়।
‘কথা বলার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক-কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়.. চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই। লাউড স্পিকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা যায় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজ রূপ রক্ষা হতে পারে।’ ছিন্নপত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ কথাগুলো লিখে গিয়েছেন। সে সময় ছিন্নপত্রের ৬৭ নং পত্রে লেখা হয়েছে, ‘তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।’ এর প্রকাশযোগ্যতা সম্পর্কে কবি নিজের অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন।
নজরুলের নিজের হাতের লেখা চিঠি এখনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে তেষট্টিটি চিঠি রয়েছে, যার প্রতিটিরই রয়েছে সাহিত্যমূল্য। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৬ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের ‘মুক্তি’ শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। মুক্তি প্রকাশের পর বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকাটির সম্পাদককে একটি পত্র লেখেন নজরুল। পত্রখানি প্রায় ১০ বছর পরে সাপ্তাহিক সওগাতে প্রকাশিত হয়।
বালিকা কন্যা ইন্দিরার উদ্দেশে রচিত পিতা জওহরলাল নেহরুর পত্রাবলীর বৃহৎ সংকলন এমনই ইতিহাসসমৃদ্ধ যে, আমরা অনেক সময়ই ভুলে থাকি সর্বার্থে বড় এই গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য। পোশাকি নাম ‘গ্লিমসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি’। এটি রচিত হয়েছিল কন্যা ইন্দিরার উদ্দেশে কারান্তরাল থেকে প্রেরিত পিতার...পত্রধারা মাধ্যমে। কিন্তু ব্যক্তি ও সমসময়কে ছাপিয়ে এ গ্রন্থের আবেদন এমনই সর্বজনীন ও সর্বকালীন যে ফিরে ফিরেই পড়তে হয় এই পত্রাবলী। এসব চিঠিতে বিভিন্নকালে বিভিন্ন যুগে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নরনারীর প্রতিবেশী হয়ে নেহরু বসবাস করেছেন। কোথাও আবার অতীতের ঘটনা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে রক্ত-মাংস দিয়ে জীবন্ত রূপে সাজিয়ে তুলেছেন।
বুদ্ধদেব গুহর পত্রোপন্যাস ‘সবিনয় নিবেদন’ একটি অসাধারণ গ্রন্থ। শুধু পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে রচনা করা একটি পূর্ণাঙ্গ ও কৌতূহলকর উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন। শুধু আঙ্গিকগত নতুনত্বের জন্যই এ উপন্যাস বিশিষ্টরূপে নন্দিত হবে না, হবে এ সামগ্রিক আবেদনের জন্যও। বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাসে দীর্ঘকাল ধরেই চিঠিপত্রের একটা আলাদা স্থান। ‘একটু উষ্ণতার জন্য’র ছুটি ও সুকুমারের অথবা ‘মাধুকরী’র পৃথু ও কুর্চির চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তিজীবনেও চমৎকার চিঠি লেখেন বুদ্ধদেব গুহ। কিন্তু এই উপন্যাসে পত্রবিলাসী কথাকার যেন নিজেই নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছেন।
পুরীর পোস্ট মাস্টার একদিন তার অফিসে ‘ভগবান/জগন্নাথের মন্দির/ পোস্টাপিস পুরী’ এই ঠিকানায় লেখা কয়েকটি চিঠির সন্ধান পান। ভগবান নামে কোনো লোককে পিয়ন খুঁজে পাননি। কৌতূহলী হয়ে তিনি একটু কুণ্ঠার সঙ্গে খাম ছিঁড়ে চিঠিগুলো পড়ে দেখেন, সেগুলো খোদ ভগবানকেই লিখেছে কলকাতা থেকে ওরফে পোনু নামের একটি ছোট ছেলে। ভগবানের কাছে পোনুর কাতর মিনতি, তিনি যেন তার সমস্যাগুলো মিটিয়ে দেন। পোনু তখন বাংলা বানান শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না। সেই ভুল বানানেই চিঠিগুলো একের পর এক সাজিয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তার ‘পোনুর চিঠি’ বইয়ে। সব বয়সের পাঠক এই চিঠিগুলোর কৌতুক রস সমানভাবে উপভোগ করে থাকেন।
যামিনী রায়ের চিঠির মূল্য অসীম। কারও চিঠি ছাড়া অন্য কোনো লিখিত ভাষ্যে নিজের মনের কথা নথিবদ্ধ করেননি তিনি। যামিনী রায়ের শিল্পীসত্ত্বাকে বুঝতে হলে মানুষটিকেও সম্যক রূপে জানতে হবে। সে উদ্দেশ্য সাধনে চিঠিই একমাত্র সহায়। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা যামিনী রায়ের বেশ কিছু চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ-বিজয়চন্দ্র সম্পর্কেও ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ বিজয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিঠি-পত্রাদির অভাব। কালিদাস নাগ প্রবাসী পত্রিকায় চারখানি চিঠি সংকলন করেন তখন (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। তিনি আট-ন’খানির বেশি চিঠি লেখেননি। সূচনাতে তিনি লেখেন, ‘...তার কন্যা সুলেখিকা সুনীতি দেবী যে চিঠিগুলো রক্ষা করেছেন, সেগুলো নকল করে আমাদের পাঠান...।’
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫-১৯৬১) বাংলা সাহিত্যজগতে বিভিন্ন দিক থেকে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পগ্রন্থ ‘রিয়ালিস্ট’ পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে দীর্ঘ চিঠি দেন, তা প্রকাশিত হয়েছে ‘পরিচয়’ বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায়।
সাহিত্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের একটি নিবিড় সংযোগ রয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে চিঠিপত্রের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অনেক সাহিত্যিকই বিভিন্ন সময়ে চিঠি লিখেছেন আপনজনকে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বেশি পত্র যোগাযোগ করেছেন। এখনো তার লেখা চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটি চিঠির আবেদন চিরন্তন বলেই।
বাংলাদেশে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পত্রবিনিময় বা একে অন্যের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শাহাদত চৌধুরীর অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা। বিচিত্রার জন্মের শুরু থেকেই ‘পাঠকের পাতা’ জনপ্রিয় হতে থাকে। এই বিভাগের মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে একধরনের যোগাযোগসূত্র তৈরি হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে যখন ‘ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন’ বিভাগটি শুরু হয়, তখন প্রচণ্ড আলোড়ন তৈরি হয়। এটাকে বলা যায়, সে সময়ের চ্যাট বক্স। বিভাগটি তখন আর একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে সব বয়সীদের পত্রালাপের বা বিজ্ঞাপনালাপের বিষয়।
মায়েরা কেন যে হারিয়ে যায়!
এভাবেই সময় চলে যায়। কিছুতেই সময়ের রাশ টেনে ধরা যায় না। মনে হয়, এই তো সেদিন কানাডায় এলাম। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে প্রথম দিনের স্মৃতি, দৃশ্যপট। অথচ দেখতে দেখতে ২২ বছর হয়ে গেছে! যেদিন পিয়ারসন এয়ারপোর্টে নামলাম, সেদিন অদ্ভুত একটা ফিলিংস হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল, কীভাবে নিজের শিকড় উপড়ে ফেলে মানুষ! প্লেনে বসেই আমার বরিশাল, আমার মা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আমার সংগ্রামময় জীবন যে ঢাকা শহরÑসব ভিড় করে আসতে লাগল। কেবলই আমাকে পিছু টানছিল। প্লেনের সুস্বাদু খাবার বিস্বাদ লেগেছিল। টরন্টো নেমে আমরা সোজা অটোয়ার পথে রওনা হলাম। ঢাকা থেকে হিথ্রো, তারপর টরন্টো। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে।
হিথ্রোতে তিন ঘণ্টা ফ্লাইট ডিলে ছিল, মনে আছে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে নামলাম নতুন এক দেশে, নতুন এক পরিবেশে। ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি শেষ করে যখন সকাল ১০টায় এয়ারপোর্ট থেকে বের হলাম, তখন টরন্টোর আকাশ রৌদ্রকরোজ্জল। ফুরফুরে বাতাস। চারদিকে সবুজের সমাহার। ২৮ জুন ছিল সেটা। কানাডায় তখন তুমুল সামার। দুটো গাড়িতে আটটা বড় লাগেজ (প্রতিটি ৭০ পাউন্ড) এবং চারটা ক্যারিঅন ব্যাগ নিয়ে আমরা অটোয়ার পথে রওনা হলাম। টরন্টো থেকে আরও চার ঘণ্টার ড্রাইভ।
সুশৃঙ্খল হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। দু’পাশে সবুজ দৃশ্য দ্রুত অপসৃয়মাণ হচ্ছে। ১২০ কিলোমিটার স্পিড। হাইওয়ের নাম ৪০১। গাড়ি শহর ছাড়িয়ে পূর্ব দিকে ছুটে চলেছে। একটার পর একটা শহর পার হচ্ছি। পোর্ট ইউনিয়ন, পিকারিং, এজাক্স, হুইটবি, অশোয়া, বোমেনভিল...। দূরেই দৃশ্যমান হচ্ছে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। লেক অন্টারিও। দূর থেকেই দেখতে পেলাম লেকের জল রৌদ্রের আলো পড়ে চিকচিক করছে। অর্ক অরিত্রি দীর্ঘ প্লেন ভ্রমণে গাড়ির মধ্যে ঘুমে ঢুলু ঢুলু। জেসমিনের চোখ বাইরে। এক গভীর অনিশ্চয়তা সেখানে।
জেসমিন আসতে চায়নি কানাডায়। অর্ক অরিত্রি সব পরিবেশেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আর আমি কখনো কখনো আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করি না। পূর্বাপর ভেবে সবকিছু করা যায় না। আমার পুরো জীবনটাই এমন। আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমি। জীবন নিয়ে আমার কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। সারা জীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছি। বিদেশের জীবন হবে আরও বেশি প্রতিকূল, সেটা জানা আছে। আমি শুধু চাই আমার সন্তানদের সুখী করতে, সেটা যেকোনো জায়গায়ই হোক না কেন।
এত বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। ছেলেমেয়েদের নিজেদের জীবন হয়েছে, সংসার হয়েছে। আরও কত কী বদলে যাবে। আমি এসব টের পাই। আমার অবজারভেশন খুব ভালো। আমি আগাম টের পাই বলে জীবনে আমি অনেক অঘটন থেকে রেহাই পেয়েছি। তার পরও আমি ভুল করি। সবচেয়ে বড় ভুল হয় মানুষ চিনতে। মানুষকে আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করি এবং প্রায়ই ঠকি। কষ্ট পাই। কিন্তু সেসব নিয়ে আমার কোনো অনুতাপ হয় না। দেশে-বিদেশে সব জায়গায়ই মানুষের কারণে আমি অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি। কিন্তু সেসব আমি মনে রাখিনি। সবাই তো আর একরকম হবে না। আগে বেশি এসব নিয়ে আদিখ্যেতা করতাম। মাথা ঘামাতাম। এখন করি না। এটাই জীবন। এসব নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ যেমন নেই, দুঃখও নেই।
যেমন মা চলে গেলেন। এই তো সেদিনের কথা। অথচ দেখতে দেখতে ১৪টি বছর পার হয়ে গেল। ২০১০ এর এই দিনে মা চলে গেলেন। জীবন থেকে এভাবেই সময় চলে যায়। মা চলে গেলেও তিনি আছেন হৃদয়ে, স্মরণে, মননে, স্মৃতির আয়নায়। অনেক অসাধারণ সব স্মৃতি আছে আমাদের, যা সব সময় জ্বলজ্বল করে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো সব সময় মুক্তোর মতো ঔজ্জ্বল্য ছড়ায় প্রতিনিয়ত। একটা ঘটনা মনে আছে, তখন আমার বয়স ১০-১২ বছর হবে। মামাবাড়িতে গিয়েছি। অজ গ্রাম। একেক দিন সন্ধ্যাবেলা আমার খুব মন খারাপ লাগত। এমন একেকটা বিকেলবেলা আছে, যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় অন্তত একটা মায়াবী অপার্থিব আলো এসে পড়ত উঠোনে। আকাশের রং যেত পাল্টে। সমস্ত বাড়িটায় কেমন এক আলো-আঁধারির সৃষ্টি হতো। হঠাৎ হঠাৎ আমার বহুজনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আমাকে অনুভব করতাম। টের পেতাম, আমার আলাদা এক ‘আমি’ আছে। সেই সব বিষণ্ন বিকেলে আমার মাঝে মাঝে মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে হতো। প্রায়ই পশ্চিমের ঘরে মাকে খুঁজতে গিয়ে পেতাম না।
সারা বাড়ি খুঁজে মাকে হয়তো পেতাম বড় ঘরের পাটাতনের সিঁড়ির তলায় গামলায় চাল মেপে তুলছেন। আমি অবোধ দুর্জ্ঞেয় এক বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যে মায়ের কাছে গিয়েছি, তা মা বুঝতেন না। তবু একটুক্ষণের জন্য হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেন। একটুক্ষণের জন্য মাথাটা চেপে রাখতেন বুকে। আমি তখন মায়ের গা থেকে মা মা গন্ধটা পেতাম। মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করতেন, দুপুরে পেট ভরেছিল? আমি বুকভরে মায়ের গায়ের সুঘ্রাণ নিতাম। আজ মা নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই আনন্দ।
সেদিনের আকাশেও সপ্তর্ষি ছিল, ছায়াপথ ছিল না। মা বসে থাকেন পাশে। পিঠে হাত বোলান। কথা বলেন না। নীরবে মাতা-পুত্রের সময় পার হয়ে যায়। ধুলারাশির মতো আকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ বিপুল একটি অনির্দিষ্ট পথের মতো পড়ে থাকে, ওখানে রোজ ঝড় ওঠে, ঝোড়ো হাওয়ায় নক্ষত্রের গুঁড়ো উড়ে সমস্ত আকাশে ছড়ায়। সপ্তর্ষির চেহারা শান্ত। প্রশ্নচিহ্নের মতো। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সীমায় বসে আছেন সাতজন শান্ত-সমাহিত ঋষি। মৃত্যুর পর থাকে কি কোনো চেতনা? অথবা আরেকবার কি জন্ম নেওয়া যায়? মৃত্যু, মহান একটি ঘুম, তার বেশি কিছু নয়। ছেলেবেলায় ফাঁকা মাঠে শুয়ে আকাশ দেখা হতো। দেখতে দেখতে কোনো শূন্যতায় পৌঁছে যেত মন। পার্থিব কোনো কিছুই আর মনে থাকত না। তখন আকাশে থাকতেন দেবতারা, মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতেন। আজ তারা কেউ নেইÑনা মনে, না আকাশে। তবু আজও সপ্তর্ষির অদৃশ্য আলো শরীর আর মনে অনুভব করা যায়।
আবার যদি দেখা হয় মায়ের সঙ্গে। আবার যদি! আমার মাথায় একটু হাত রাখো তো মা, একটু হাত রাখো। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, কেন রে? সব ভুলিয়ে দাও তো মা, ভুলিয়ে দাও তো। বুদ্ধি, স্মৃতি, অবস্থা ভুলিয়ে দাও। আবার ছোট হয়ে কোলে ফিরে যাই...।





 জসিম মল্লিক
জসিম মল্লিক