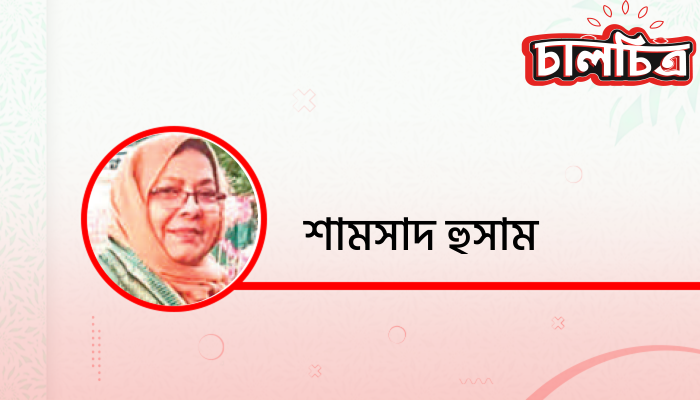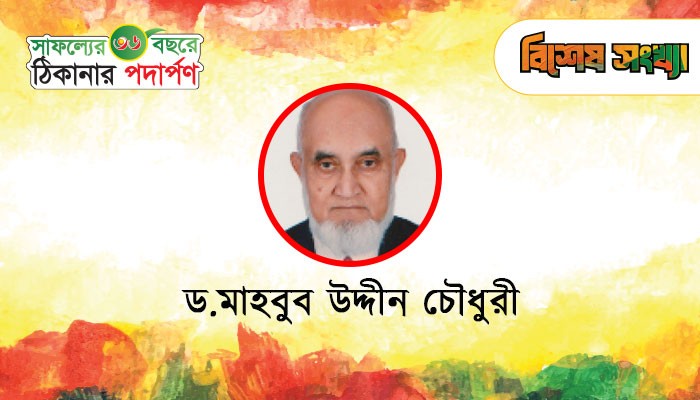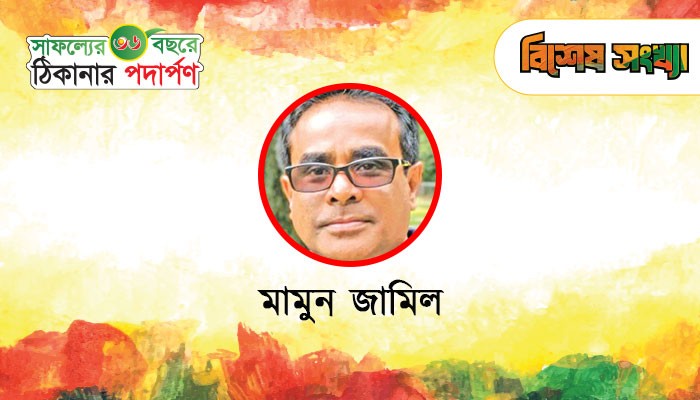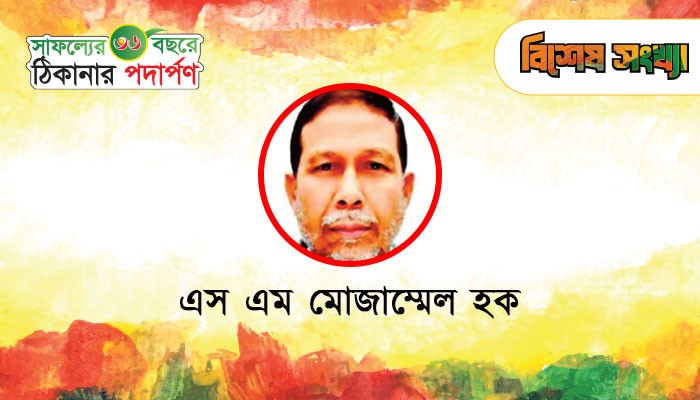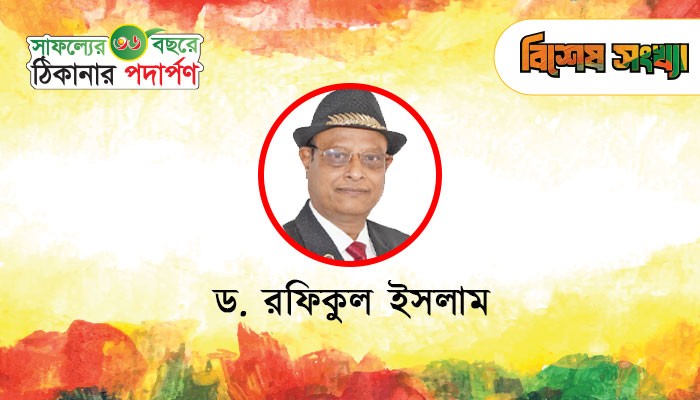পুলিশ কি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে? কিংবা আইনের ঊর্ধ্বে কি মার্কিন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটির ওজোন পার্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোর রোজারিও নিজ বাসায় এক পুলিশ সদস্যের গুলিতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হওয়ার পর আপামর জনগণের মনে এই প্রশ্নটি ওঠা শুরু হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে। অনেকেই বিষয়টিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন। ঘটনাটি হয়তো আর সব ঘটে যাওয়া ঘটনার মতো একসময় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলেই যেত, যদি না রোজারিও হত্যাকাণ্ডের এক মাস ছয় দিন পর গত ৩ মে নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশা জেমসের অফিস থেকে পুলিশের বডি ক্যামেরার ফুটেজটি প্রকাশ্যে না আসত।
স্থানীয় টেলিভিশনের নিউজে যখন ভিডিও ফুটেজটি দেখানো হচ্ছিল, তখন সেই দৃশ্য দেখে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক দর্শক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে আবার শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার সাহস করতে পারেননি। টিভির নবটি ঘুরিয়ে পর্দা অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বুকের ধুকপুকানি শুনে নিজেই অবাক হয়েছিলেন, একটি তরতাজা কিশোর, যে কিনা ওই সময়ে মানসিক অসুস্থতার কারণে ভারসাম্যহীন আচরণ করছিল; সেই রকম এক কিশোরকে মায়ের সামনে, ভাইয়ের সামনে পুলিশের দুই কর্মকর্তা অবলীলায় গুলি করে খুন করে ফেলল! কী করে তারা এমন অমানবিক কাজটি করল? কিছুতেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারছেন না অভিবাসী সমাজের মানুষ। কিন্তু তারা মানতে না পারলে কী এসে যায়? ইতিমধ্যে শহরের বৃহত্তম পুলিশ ইউনিয়ন ঠান্ডা মাথার দুই খুনি পুলিশের- যার মধ্যে একজনের নাম মালভেটর অ্যালোঙ্গি এবং অন্যজনের নাম ম্যাথিউ সিয়ানফ্রকো- প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছে। পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্যাটিক হোন্ডিও তার বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এই পুলিশ অফিসারদ্বয় এমন এক ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে একটি অস্ত্র ধরেছিল এবং একাধিক ব্যক্তিকে বিপদে ফেলেছিল।’ সভাপতি মহোদয় অবশ্য কিশোরটির হাতে ধরা অস্ত্রের বিবরণ দেননি। কী ধরনের অস্ত্র ছিল রোজারিওর হাতে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে না বললেও টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, রোজারিওর হাতে ওই সময়ে কিচেনের কাজে ব্যবহৃত একটি কাঁচি ছিল। যদি কাঁচি না থেকে বড় কোনো ছুরিও থাকত এবং সেটা দিয়ে সে অন্যকে আক্রমণের অজুহাত খুঁজত, তবু প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক, পুলিশ কি সেই অবস্থাতেও একটা অসুস্থ বাচ্চাকে খুন করার অধিকার রাখে?
এ সম্পর্কে ভিডিও ফুটেজটি প্রকাশ্যে আসার পর নিউইয়র্ক জাস্টিস কমিটির নির্বাহী পরিচালক ‘ইলডা কলোন’ মন্তব্য করেছেন, ‘ফুটেজটি খুবই কষ্টদায়ক এবং তা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার শামিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, এ পর্যন্ত মেয়র এরিক অ্যাডামসের অফিস থেকে ওই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধামাচাপা দেওয়া বক্তব্য ছাড়া কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। ওই দুই ঠান্ডা মাথার খুনি পুলিশ অফিসারদের বিচার কিংবা তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়েও এখন পর্যন্ত কোনো খবর নেই উদ্বিগ্ন প্রবাসী বাংলাদেশি মানুষদের কাছে। সাধারণ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে সাদা চামড়ার মানুষের বাইরে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি পুলিশ বাহিনীর এমন কিছু আচার-আচরণ সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। ‘হোয়াইট সুপ্রিমেসি’ অনুভূতিটি এখন এতটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে প্রশাসনসহ রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ মহলের মানুষদের কাছে, যার পরিণতিতে মানুষ আর মানুষ বলে গণ্য হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ফলে যার রক্ষক হওয়ার কথা, তিনি এখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই ভক্ষকের ভূমিকায় পুলিশ বাহিনীর সক্রিয় কাজ-কারবার এখন এতটাই বেপরোয়া যে, তার প্রমাণ হলো যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতিবছর পুলিশের হাতে মারা যায় বারো শ’র মতো মানুষ। যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে না, শুধু সন্দেহের বশে অথবা ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে পুলিশের কিছু কিছু ঠান্ডা মাথার খুনি এসব খুনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন।
২০১৩ থেকে ২০১৯ এই সময়কালের মধ্যে এ ধরনের খুনের ঘটনা ঘটেছে শুধু পুলিশের হাতে সাত হাজারেরও বেশি। কিন্তু সত্যি হলেও অবাক না হওয়ার বিষয় হচ্ছে, ওইসব খুনের ঘটনার পর ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় না। কারণ, দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি মামলায় পুলিশের ক্ষেত্রে বিশেষ এক সুরক্ষা আইন দ্বারা তাদেরকে প্রটেকশন দিয়ে রেখেছে রাষ্ট্র। এ ছাড়া পুলিশ এবং আইনজীবীÑএই দুই সম্প্রদায় হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার অংশ। শক্তি প্রয়োগের অধিকার পুলিশ বাহিনীকে দেওয়ায় আইনজীবী সম্প্রদায় পুলিশের বিপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁড়াতে চায় না। ফলে কদাচিৎ পুলিশের অপকর্মের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হলেও তার সংখ্যা হয় মোট ঘটনার ১ দশমিক ৩ শতাংশের মতো, যা নিতান্তই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বিষয়। পুলিশ বাহিনীকে রাষ্ট্র কর্তৃক এ ধরনের দায়মুক্তির অধিকার দেওয়ার ফলে তাদের আচরণ এখন সর্বক্ষেত্রে মারমুখী। তবে বর্ণবৈষম্য বিবেচনায় রেখে সাদা চামড়া ছাড়া বাদবাকি সব ধরনের মানুষের প্রতি পুলিশের আচরণ কখনোই মানবিকতাপূর্ণ হয় না। কেবল উইন রোজারিওকে উদাহরণ হিসেবে সামনে না এনেও এ রকম অনেক কিশোর-যুবক যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের খুনের টার্গেট হয়েছেন অতীতে। তার মধ্যে ২০১৪ সালে নিউইয়র্কের এরিক গার্নার, ২০১৯ সালে ডালাসের আতাতিয়ানা জেফারসন, ২০২০ সালে কেন্টাকির ব্রেওনা টেইলর, ২০১৫ সালে টেক্সাসের মান্দ্রা ব্ল্যান্ড, ২০১৫ সালে বাল্টিমোরের ফ্রেডি গ্রে, ২০১৪ সালে মাইকেল ব্রাউন, ২০১৭ সালে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ওয়াল্টার স্কট অন্যতম। এসব নিরপরাধ মানুষকে পুলিশ শুধু সন্দেহের বশে খুন করেছিল। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আদালত কোনো মামলা গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালত মামলা গ্রহণে রাজি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুরিবোর্ড চিহ্নিত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য হতে পারে না মন্তব্য করে বানচাল করে দিতে চেয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভ ও আন্দোলন জোরদার হলে আদালত পুলিশের চিহ্নিত আসামিকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছে অথবা চাকরিচ্যুত করেছে। তবে সেসব সংখ্যা নেহাতই কম।
ম্যাপিং পুলিশ ভায়োলেন্স নামের বেসরকারি এক সংস্থার মতে, প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে শ্বেতাঙ্গদের চাইতে তিনগুণ বেশি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ মারা যায়। সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন বাদামি চামড়ার মানুষেরা, যার উদাহরণ উইন রোজারিওর মতো অসহায় মানব সন্তানেরা।
তবে যে হত্যাকাণ্ডটি প্রশাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তা ছিল ২০২০ সালের মে মাসে মিনেসোটায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে সামান্য এক নকল নোট দিয়ে সিগারেট কেনার অজুহাতে পুলিশ কর্তৃক খুন হওয়ার বিষয়টি। জর্জ ফ্লয়েডকে পুলিশের এক কর্মকর্তা ডেরিক সৌভিন মাটিতে ফেলে তার হাঁটু দিয়ে ঘাড়ে নয় মিনিট ধরে গলা চেপে ধরেছিলেন। ফ্লয়েড তখন কাতর কণ্ঠে বারবার উচ্চারণ করছিলেন, প্লিজ, প্লিজ আই ক্যান্ট ব্রেথ। কিন্তু খুনি পুলিশের তাতে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্লয়েড তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত ডেরেক তার হাঁটু চেপে ধরে রেখেছিলেন। বিষয়টি শুধু আমেরিকার ভৌগোলিক সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ পর্যন্ত। ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়ার আকাশসীমা পর্যন্ত।
ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষেরা রাস্তার দ্বারে স্থাপিত বর্ণবাদী মানুষদের মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে তাদের নামে স্থাপিত রাস্তার নামকরণ পাল্টে দেওয়ার দাবি তুলেছিল। এ ছাড়া আমেরিকান নাগরিক অধিকার বিষয়ক সংস্থাটি তখন পুলিশের বাজেট কমিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো ছাড়াও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছিল। ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরগুলোতে পুলিশি ব্যবস্থার জন্য রাজস্ব কমিয়ে আনা হয়, যে কারণটির জন্য পুলিশ ইউনিয়নগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল তখন। তবে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুতে দেশজুড়ে এতটাই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে যে সেখান থেকে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের সূত্রপাত। জনগণের তীব্র আন্দোলনের ফলে মামলাটি আদালতে ওঠে এবং রায় ঘোষণার সময় মাননীয় বিচারক তার ২২ পৃষ্ঠার অভিমতে উল্লেখ করেন, যেহেতু ওই সময়ে খুনি ডেরেকের সঙ্গে আরও তিনজন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাই আদালত বিষয়টিকে ‘সংঘবদ্ধ অপরাধ’ বলে মনে করছে। বিচারের রায়ে খুনি পুলিশ ডেরেক সৌভিনকে সর্বোচ্চ সাড়ে ২২ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন আদালত।
রায়ের পর স্থানীয় ধর্মযাজক রেভারেন্ড আল মার্পটন বলেছিলেন, ‘এবার বলার সময় হয়েছে, এবার আপনাদের হাঁটু আমাদের গলার ওপর থেকে সরান।


 শামসাদ হুসাম
শামসাদ হুসাম