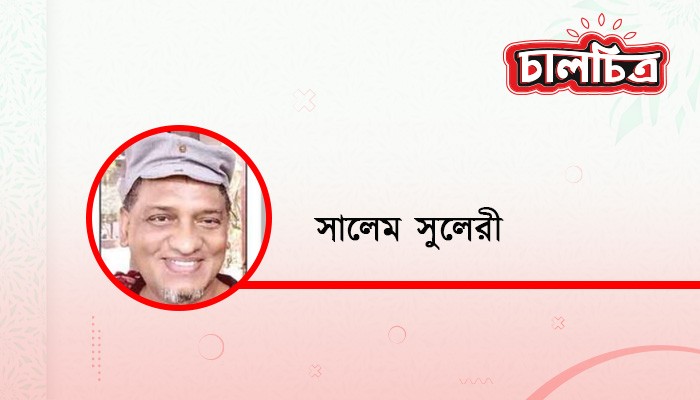
সরকারি ট্রাস্টের ঋদ্ধ কাগজ ছিল ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’, ‘দৈনিক বাংলা’। আশির দশকে সম্পাদক ছিলেন প্রধান কবি শামসুর রাহমান। ১৯৮৫-৮৬-তে তিনি এসবে প্রধান সম্পাদক হন। রাষ্ট্রক্ষমতায় তখন সামরিক শাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদ। তিনি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নামে কবিতাও লিখতেন।
‘শামসুর রাহমান মনোনীত কবিতা’ নামে বিভাগ ছিল বিচিত্রায়। তাতে কবিতা ছাপতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন সর্ববাংলার কবিরা। আমার সৌভাগ্য, তরুণ হলেও বিশেষ সমাদর পেয়েছি। সতীর্থ নাসিমা সুলতানা ও আমি ছিলাম তরুণদের মধ্যে এগিয়ে। ‘বিচিত্রা’, ‘দৈনিক বাংলা’ ও অন্যত্র আমার একার ১৪টি কবিতা। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত।
ভাষার মাস ‘ফেব্রুয়ারি’ বাংলাদেশের জন্মের আভাসচিত্র এঁকেছিল। ১৯৫২-এর মাতৃভাষা আন্দোলনেই বীজ রোপিত হয় স্বাধীনতার। সংশ্লিষ্ট আন্দোলন-সংগ্রামে শামসুর রাহমানের কবিতা ছিল বিশাল অনুপ্রেরণা। ‘আসাদের সার্ট’, ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘একটি মোনাজাতের খসড়া’-বহুল আলোচিত। ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা’ কবিতাটিও প্রেরণামূলক। ‘স্বাধীনতার কবি’ বিশেষণে শামসুর রাহমান বিশেষভাবে সমাদৃত।
আশির দশকে ‘মধ্য ফেব্রুয়ারি’ ছিল ছাত্র-গণ আন্দোলনের তীর্থমাস। সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে উন্মাদনা। ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি। তাতে ব্যাপক রক্তপাতের ঘটনায় বিপ্লবী কবিতা লিখেছিলাম। কবি শামসুর রাহমান দ্বিধাহীন চিত্তে সরকারি ট্রাস্টের কাগজে ছাপেন। ১৯৮৭-এর পয়লা-দোসরা ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় কবিতা’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রস্তাবেই উনি উৎসব কমিটির আহ্বায়ক হয়েছিলেন। ‘বর্ণমালা’ আমার দুখিনী বর্ণমালার কবি ভাষামাসে নানাভাবে সমাদৃত। ১৯৭৭- এ ‘দৈনিক বাংলা’ ও ‘বিচিত্রা’র সম্পাদকও হন ফেব্রুয়ারি মাসেই।
মধ্য ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে যেভাবে লেখা হলো ‘ঠেলা-অলা’ ॥ যেভাবে ছাপা হলো সরকারি ট্রাস্টের কাগজে
‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল। পটভূমিটি যেমন বিপ্লবের, তেমন রোমান্টিকতারও। কারণ ঘটনাকালটি ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি। ‘বিশ্ব ভালোবাসা দিবস’ বা ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’। না, সে দিনটায় প্রিয় বান্ধবীকে ফুল দিতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত সরকার-বিরোধী আন্দোলনে। ‘মজিদ খানের শিক্ষানীতি’ বাতিলের দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও। সামরিক সরকারের পেটোয়া বাহিনী সমানে বুলেট ছুড়ল।
তখন মুহসীন হলের ৩৬২ নম্বর কক্ষে আমার বসবাস। ‘হবু কবি-সাংবাদিক পরিচয়ে’ সবাই কিছুটা সমীহ করত। কিন্তু আমার জানালার কার্নিশেই আন্দোলনকারীদের সরঞ্জামাদি। রুম ৩৬৪ থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন ছাত্রনেতা শফি আহমেদ। কক্ষ-অধিকর্তা খায়রুজ্জামান কামালও তা জানতেন না। সেদিনের মহা-তাণ্ডবে শেফালী, জাফর, জয়নালসহ অসংখ্য নিহত। আগের রাতে আমি ছিলাম পুরান ঢাকায় সক্রিয়। ‘তাওয়াক্কাল প্রেস’ থেকে কম্পোজ ম্যাটারসহ যাচ্ছিলাম আরেকটিতে। গলির ওপর ধরে ফেলল অস্ত্রধারী টহল পুলিশ। কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ/সেন্টু ভাই তখন কৃষিমন্ত্রী। লেখক আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন অতিরিক্ত পুলিশ-প্রধান। ওনাদের নাম ভাঙিয়ে গায়ে-গতরে ছাড়া পেলাম। কিন্তু পরদিনের ট্র্র্যাজেডি থেকে মুক্তি পেলাম না।
সরকার সন্ধ্যা থেকেই কারফিউ ঘোষণা করল। পরদিন ভোর ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত শিথিল। রাজধানীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে হবে। অগ্রজ কবি-মুক্তিযোদ্ধা সরকার মাহবুবের বাসায় রাতযাপন। পরদিন ভোরেই হলে পৌঁছে ব্যাগ গোছানো। সাতসকালে সামরিক বাহিনী ‘যাচ্ছেতাই’ ব্যবহার করল। কাঁধভরা ব্যাগের ছাত্রজীবনকে অভিশপ্ত ও দায় মনে হলো।
‘মানুষ গড়ার আঙিনা’ থেকে ছিটকে পড়ল আমাদের তারুণ্য। প্রিয় বান্ধবী ‘হ্যাপী’ হারিয়ে গেল জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে। রক্তঝরা লাশগুলোর ঠিকমতো সৎকার বা জানাজা হলো না। অগ্রজের ‘বেইলি ড্যাম্প কলোনি’র বাসায় ব্যাগ রেখেই দৌড়। ১৮ তোপখানা রোডের মিডিয়ামুখর ‘জাতীয় প্রেসক্লাব।’ ভিড় এড়িয়ে দোতলায় সোজা লাইব্রেরি রুমে। ক্ষোভ ঝাড়লাম তরতাজা এক মেদহীন কবিতায়। না, স্লোগানধর্মী শব্দ-বাক্য-বয়ান নয়। শিল্পীত রূপে আন্দোলন ও রক্তদানের চিত্র আঁকলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণে রেখে ১৪ পঙ্্ক্তির কাব্য-পরিবেশনা ‘ঠেলা-অলা’।
মধ্যাহ্নভোজের পরপরই গেলাম নিকটস্থ ‘দৈনিক বাংলা’ ভবনে। ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’, ‘বাংলাদেশ টাইমসও’ একই ভবনের প্রকাশনা। কবি-সম্পাদক শামসুর রাহমান আমাদের নিদানকালের অভিভাবক। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত জানলেন। হস্তাক্ষরে কপি করা সদ্যোজাত কবিতাটি দিলাম।
তখন ইমেইল, কম্পিউটার কম্পোজের প্রক্রিয়া ছিল না। হাতে হাতে বা ডাকযোগে কবিতা পৌঁছাতে হতো। চোখকাড়া হস্তাক্ষরের লেখকেরা সম্পাদকের বিশেষ মনোযোগ পেতেন। উচ্চপদস্থরা ‘টাইপ রাইটার’ ব্যবহার করতেন। টরে-টক্কায় টাইপ করা কবিতা পাঠাতে দেখেছি তিনজনকে। দেশের প্রধান কবি-সম্পাদক শামসুর রাহমানকে। গুলশানে থাকা সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হককে। আর ক্ষমতাসীন কবি-রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে। উল্লেখ্য, সকল সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় ওনাদের কবিতা থাকত। এরশাদ সাহেবের কবিতা প্রায়ই প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। পুরো আশির দশক বাংলাদেশের মিডিয়ায় এমনটিই ঘটেছে।
জানতাম, ‘দৈনিক বাংলা’, ‘বিচিত্রা’ সরকারি ট্রাস্টের কাগজ। তাতে ‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি ছাপা হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে সম্পাদক শামসুর রাহমান জাদু দেখালেন। শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যায় সাড়ম্বরে ছাপলেন। সরকারি কাগজে চাকরি করেও জানান দিলেন তিনি গণতন্ত্রপন্থী, যেন সামরিক সরকারের আগ্রাসনকে উপেক্ষা করলেন। এই প্রেরণাতেই সাতাশির পয়লা-দোসরা ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় কবিতা উৎসব’। ওনার নাড়ি আমার জানা ছিল বলেই দু’হাত বাড়াই। ‘স্বৈরাচার-বিরোধী’ কবিতা উৎসবে নেতৃত্বের আহ্বান জানাই। আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ায় তিনি আজ ইতিহাস।
‘ঠেলা-অলা’ প্রকাশকালে রাহমান ভাই একটু কৌশলী হয়েছিলেন। ‘নতুন পহেলা মে’কে করেছিলেন ‘বিগত পহেলা মে’। পরে কানে কানে বলেছিলেন, এমনটির প্রয়োজন ছিল। অতীতে না নিয়ে গেলে ট্রাস্টের কাগজে ছাপা যেত না। হেলাল হাফিজের ‘এখন যৌবন যার’ ছাপানো যায়নি। উনসত্তরে কবি আহসান হাবীব তা ছাপতে পারেননি। কিন্তু তোমার ‘ঠেলা-অলা’ আমি ঠিকই ছেপে দিয়েছি। এটি ইতিহাসের সত্য, না ছাপলে মনোবেদনায় ভুগতাম। উল্লেখ্য, কবি-শ্রদ্ধেয় আহসান হাবীব দেখতেন সাহিত্য পাতা। বিশেষ সংখ্যাগুলো সম্পাদনা করতেন কবি শামসুর রাহমান স্বয়ং। হাবীব ভাইয়ের সম্পাদনা সহকারী ছিলেন কবি নাসির আহমেদ। রাহমান ভাইয়ের পাতার সমন্বয়ক সাংবাদিক-মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরী। কবিতায় ছন্দের পোশাক পরাতে উভয়েই আমাকে পরামর্শ দিতেন।
২০০৩-এ বেরোয় আমার প্রথম ‘কবিতা সংগ্রহ’। শিরোনাম : ‘কবিতা হাতের পাঁচ’, পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে’র সম্মিলনী। পাণ্ডুলিপিটি সমন্বয় করেছিল অনুজ কবি-গবেষক তৌফিক জহুর। তার মতে, ‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি সূচনায় দেওয়া যায়। তখন গ্রন্থভিত্তিক আয়োজনে তা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু শামসুর রাহমান মনোনীত সাসু’র কবিতায় সম্ভব হলো। ভীষণ পরিতৃপ্তি রোধ করছি বহুমাত্রিক কবিতাটির অগ্রযাত্রায়।
‘শামসুর রাহমান মনোনীত কবিতা’ নামে বিভাগ ছিল বিচিত্রায়। তাতে কবিতা ছাপতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন সর্ববাংলার কবিরা। আমার সৌভাগ্য, তরুণ হলেও বিশেষ সমাদর পেয়েছি। সতীর্থ নাসিমা সুলতানা ও আমি ছিলাম তরুণদের মধ্যে এগিয়ে। ‘বিচিত্রা’, ‘দৈনিক বাংলা’ ও অন্যত্র আমার একার ১৪টি কবিতা। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত।
ভাষার মাস ‘ফেব্রুয়ারি’ বাংলাদেশের জন্মের আভাসচিত্র এঁকেছিল। ১৯৫২-এর মাতৃভাষা আন্দোলনেই বীজ রোপিত হয় স্বাধীনতার। সংশ্লিষ্ট আন্দোলন-সংগ্রামে শামসুর রাহমানের কবিতা ছিল বিশাল অনুপ্রেরণা। ‘আসাদের সার্ট’, ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘একটি মোনাজাতের খসড়া’-বহুল আলোচিত। ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা’ কবিতাটিও প্রেরণামূলক। ‘স্বাধীনতার কবি’ বিশেষণে শামসুর রাহমান বিশেষভাবে সমাদৃত।
আশির দশকে ‘মধ্য ফেব্রুয়ারি’ ছিল ছাত্র-গণ আন্দোলনের তীর্থমাস। সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে উন্মাদনা। ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি। তাতে ব্যাপক রক্তপাতের ঘটনায় বিপ্লবী কবিতা লিখেছিলাম। কবি শামসুর রাহমান দ্বিধাহীন চিত্তে সরকারি ট্রাস্টের কাগজে ছাপেন। ১৯৮৭-এর পয়লা-দোসরা ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় কবিতা’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রস্তাবেই উনি উৎসব কমিটির আহ্বায়ক হয়েছিলেন। ‘বর্ণমালা’ আমার দুখিনী বর্ণমালার কবি ভাষামাসে নানাভাবে সমাদৃত। ১৯৭৭- এ ‘দৈনিক বাংলা’ ও ‘বিচিত্রা’র সম্পাদকও হন ফেব্রুয়ারি মাসেই।
মধ্য ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে যেভাবে লেখা হলো ‘ঠেলা-অলা’ ॥ যেভাবে ছাপা হলো সরকারি ট্রাস্টের কাগজে
‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফসল। পটভূমিটি যেমন বিপ্লবের, তেমন রোমান্টিকতারও। কারণ ঘটনাকালটি ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি। ‘বিশ্ব ভালোবাসা দিবস’ বা ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’। না, সে দিনটায় প্রিয় বান্ধবীকে ফুল দিতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত সরকার-বিরোধী আন্দোলনে। ‘মজিদ খানের শিক্ষানীতি’ বাতিলের দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও। সামরিক সরকারের পেটোয়া বাহিনী সমানে বুলেট ছুড়ল।
তখন মুহসীন হলের ৩৬২ নম্বর কক্ষে আমার বসবাস। ‘হবু কবি-সাংবাদিক পরিচয়ে’ সবাই কিছুটা সমীহ করত। কিন্তু আমার জানালার কার্নিশেই আন্দোলনকারীদের সরঞ্জামাদি। রুম ৩৬৪ থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন ছাত্রনেতা শফি আহমেদ। কক্ষ-অধিকর্তা খায়রুজ্জামান কামালও তা জানতেন না। সেদিনের মহা-তাণ্ডবে শেফালী, জাফর, জয়নালসহ অসংখ্য নিহত। আগের রাতে আমি ছিলাম পুরান ঢাকায় সক্রিয়। ‘তাওয়াক্কাল প্রেস’ থেকে কম্পোজ ম্যাটারসহ যাচ্ছিলাম আরেকটিতে। গলির ওপর ধরে ফেলল অস্ত্রধারী টহল পুলিশ। কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ/সেন্টু ভাই তখন কৃষিমন্ত্রী। লেখক আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন অতিরিক্ত পুলিশ-প্রধান। ওনাদের নাম ভাঙিয়ে গায়ে-গতরে ছাড়া পেলাম। কিন্তু পরদিনের ট্র্র্যাজেডি থেকে মুক্তি পেলাম না।
সরকার সন্ধ্যা থেকেই কারফিউ ঘোষণা করল। পরদিন ভোর ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত শিথিল। রাজধানীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে হবে। অগ্রজ কবি-মুক্তিযোদ্ধা সরকার মাহবুবের বাসায় রাতযাপন। পরদিন ভোরেই হলে পৌঁছে ব্যাগ গোছানো। সাতসকালে সামরিক বাহিনী ‘যাচ্ছেতাই’ ব্যবহার করল। কাঁধভরা ব্যাগের ছাত্রজীবনকে অভিশপ্ত ও দায় মনে হলো।
‘মানুষ গড়ার আঙিনা’ থেকে ছিটকে পড়ল আমাদের তারুণ্য। প্রিয় বান্ধবী ‘হ্যাপী’ হারিয়ে গেল জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে। রক্তঝরা লাশগুলোর ঠিকমতো সৎকার বা জানাজা হলো না। অগ্রজের ‘বেইলি ড্যাম্প কলোনি’র বাসায় ব্যাগ রেখেই দৌড়। ১৮ তোপখানা রোডের মিডিয়ামুখর ‘জাতীয় প্রেসক্লাব।’ ভিড় এড়িয়ে দোতলায় সোজা লাইব্রেরি রুমে। ক্ষোভ ঝাড়লাম তরতাজা এক মেদহীন কবিতায়। না, স্লোগানধর্মী শব্দ-বাক্য-বয়ান নয়। শিল্পীত রূপে আন্দোলন ও রক্তদানের চিত্র আঁকলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণে রেখে ১৪ পঙ্্ক্তির কাব্য-পরিবেশনা ‘ঠেলা-অলা’।
মধ্যাহ্নভোজের পরপরই গেলাম নিকটস্থ ‘দৈনিক বাংলা’ ভবনে। ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’, ‘বাংলাদেশ টাইমসও’ একই ভবনের প্রকাশনা। কবি-সম্পাদক শামসুর রাহমান আমাদের নিদানকালের অভিভাবক। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত জানলেন। হস্তাক্ষরে কপি করা সদ্যোজাত কবিতাটি দিলাম।
তখন ইমেইল, কম্পিউটার কম্পোজের প্রক্রিয়া ছিল না। হাতে হাতে বা ডাকযোগে কবিতা পৌঁছাতে হতো। চোখকাড়া হস্তাক্ষরের লেখকেরা সম্পাদকের বিশেষ মনোযোগ পেতেন। উচ্চপদস্থরা ‘টাইপ রাইটার’ ব্যবহার করতেন। টরে-টক্কায় টাইপ করা কবিতা পাঠাতে দেখেছি তিনজনকে। দেশের প্রধান কবি-সম্পাদক শামসুর রাহমানকে। গুলশানে থাকা সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হককে। আর ক্ষমতাসীন কবি-রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে। উল্লেখ্য, সকল সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় ওনাদের কবিতা থাকত। এরশাদ সাহেবের কবিতা প্রায়ই প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। পুরো আশির দশক বাংলাদেশের মিডিয়ায় এমনটিই ঘটেছে।
জানতাম, ‘দৈনিক বাংলা’, ‘বিচিত্রা’ সরকারি ট্রাস্টের কাগজ। তাতে ‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি ছাপা হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের অবাক করে সম্পাদক শামসুর রাহমান জাদু দেখালেন। শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যায় সাড়ম্বরে ছাপলেন। সরকারি কাগজে চাকরি করেও জানান দিলেন তিনি গণতন্ত্রপন্থী, যেন সামরিক সরকারের আগ্রাসনকে উপেক্ষা করলেন। এই প্রেরণাতেই সাতাশির পয়লা-দোসরা ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় কবিতা উৎসব’। ওনার নাড়ি আমার জানা ছিল বলেই দু’হাত বাড়াই। ‘স্বৈরাচার-বিরোধী’ কবিতা উৎসবে নেতৃত্বের আহ্বান জানাই। আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ায় তিনি আজ ইতিহাস।
‘ঠেলা-অলা’ প্রকাশকালে রাহমান ভাই একটু কৌশলী হয়েছিলেন। ‘নতুন পহেলা মে’কে করেছিলেন ‘বিগত পহেলা মে’। পরে কানে কানে বলেছিলেন, এমনটির প্রয়োজন ছিল। অতীতে না নিয়ে গেলে ট্রাস্টের কাগজে ছাপা যেত না। হেলাল হাফিজের ‘এখন যৌবন যার’ ছাপানো যায়নি। উনসত্তরে কবি আহসান হাবীব তা ছাপতে পারেননি। কিন্তু তোমার ‘ঠেলা-অলা’ আমি ঠিকই ছেপে দিয়েছি। এটি ইতিহাসের সত্য, না ছাপলে মনোবেদনায় ভুগতাম। উল্লেখ্য, কবি-শ্রদ্ধেয় আহসান হাবীব দেখতেন সাহিত্য পাতা। বিশেষ সংখ্যাগুলো সম্পাদনা করতেন কবি শামসুর রাহমান স্বয়ং। হাবীব ভাইয়ের সম্পাদনা সহকারী ছিলেন কবি নাসির আহমেদ। রাহমান ভাইয়ের পাতার সমন্বয়ক সাংবাদিক-মুক্তিযোদ্ধা সালেহ চৌধুরী। কবিতায় ছন্দের পোশাক পরাতে উভয়েই আমাকে পরামর্শ দিতেন।
২০০৩-এ বেরোয় আমার প্রথম ‘কবিতা সংগ্রহ’। শিরোনাম : ‘কবিতা হাতের পাঁচ’, পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে’র সম্মিলনী। পাণ্ডুলিপিটি সমন্বয় করেছিল অনুজ কবি-গবেষক তৌফিক জহুর। তার মতে, ‘ঠেলা-অলা’ কবিতাটি সূচনায় দেওয়া যায়। তখন গ্রন্থভিত্তিক আয়োজনে তা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু শামসুর রাহমান মনোনীত সাসু’র কবিতায় সম্ভব হলো। ভীষণ পরিতৃপ্তি রোধ করছি বহুমাত্রিক কবিতাটির অগ্রযাত্রায়।
