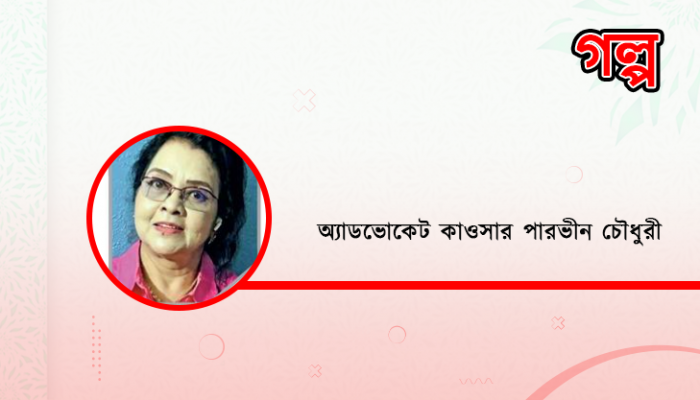
একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ক্রমেই অধীর করে তোলে রিমাকে। ঘুরেফিরে সে চারপাশ খোঁজে। নাহ্! কোথাও তো কেউ নেই। কিন্তু কাঁদছে কে? উন্মুখ হয়ে কান পাতে। চারদিকে হু হু বাতাস ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে তার নিজের ভেতরটাই কাঁদছে। গুঙিয়ে আনমনে কাঁদছে। হু হু খোলা হাওয়ার মতো বেদম কেঁদে চলছে।
ভরসন্ধ্যায় সে রোজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের হাডসন নদীর পাড় ধরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে একা। ভেতরটা তীব্র এক যন্ত্রণায় পুড়ছে। আসলেই কি সে এখন একা? না একা নয়। হাজার রকমের কষ্টের দানবরা তাদের পিণ্ডিচটকে একমাত্র রিমির মাথার ওপর ঠাঁই করে নিয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে সে। এসব কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছে এখানে কিন্তু কষ্টগুলোও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। দুঃখ, দুর্দশা তাকে ছাড়েনি।
সর্বশেষ আজকের ঘটনাটাই তার সবকিছু বদলে দিয়েছে। সে এত বেশি মর্মাহত হয়েছে যে এর থেকে কূলকিনারা পাওয়ার একটাই পথ। তাই শেষান্তে এই নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়।
আসলে বিপদের বুঝি সাত ভাই। এক ভাই উঁকি দিলে বাকি ছয় ভাই লাঠি, শাবল, দা, কুড়াল নিয়ে ভীষণ আকারে পাশে এসে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে আচমকা সাফোয়ানের মৃত্যু তার সবকিছু বদলে দিয়েছে। উল্টেপাল্টে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সাফোয়ানের মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠতম কষ্ট। সাফোয়ান আর নেই। আকস্মিক কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সাফোয়ান আর ফিরবে না ঘরে। কোনো দিনও আর ফিরবে না। এই ঘরে রিমা কেমন করে থাকবে এক।
সাফোয়ান চলে গেছে কিন্তু তার যাবতীয় কষ্টগুলো উগরে রেখে গেছে রিমার কাছে। মাতৃহারা সাফোয়ান তার বৈমাত্রেয় মা, ভাইদের আবাল্য শৈশবের যাবতীয় কষ্ট উগরে দিয়ে গেছে রিমার কাছে। একই গল্প সাফোয়ান রিমাকে বারবার বলেছে অবচেতন মনে। রিমা কান পেতে শ্রবণ করেছে কিন্তু কখনো ব্যক্ত করেনি এটা চেনা কাহিনি। আরও কয়েকবার সাফোয়ান তাকে বলেছে।
আসলে সাফোয়ান রিমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিজেকে নির্ভার করতে চেয়েছিল। কিন্তু পেরেছে কি? শেষ পর্যন্ত সামান্য জমিজমা-সম্পদের জন্য সাফোয়ানের বৈমাত্রেয় ভাইদের কূটকৌশলে নিজের প্রাণটুকু হারিয়ে ফেলল। সাফোয়ান আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার কষ্টগুলো সতেজ হয়ে বেঁচে আছে রিমার কাছে।
বিসিএস ক্যাডারভুক্ত হয়ে মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে সাফোয়ানের সঙ্গেই এক গাড়িতে রিমা আসা-যাওয়া করত। সে গাড়িতে রিমা একা একা কেমন করে যাবে। সাফোয়ানের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, গলার আওয়াজ চারদিকে ভোঁ ভোঁ বাতাসে ঘুরপাক খায় আর রিমা স্মৃতির দাপটে কোনো এক অতলান্তে তলিয়ে যায়। এর থেকে নিস্তার পেতেই সে বেছে নিয়েছে আমেরিকার প্রবাসী জীবন। তার ওপর সাফোয়ানের বৈমাত্রেয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের জাল তো আছেই।
সাফোয়ানের স্বল্পশিক্ষিত বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের প্রতিহিংসা আর লোভের আগুন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছে সাফোয়ানের সম্ভাবনাময় জীবন। বংশের উজ্জ্বলতম প্রদীপখানি। তাদের বোধেও নেই কোন সম্পদ আসল আর কোন সম্পদ নকল। এরপর রিমা কি তাদের থেকে পরিত্রাণ পাবে? তাই তো সে আমেরিকান এই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। একাকীই আমেরিকায় চলে এসেছে।
আসলে আমেরিকায় যারা আসে, তারা কেউ প্রথমে একাই আসে। তারপর বত্রিশ জন সদস্যকে কেউ একসঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। এ রকম কাহিনি রিমা অনেক শুনেছে। এমনও আছে, বাংলাদেশে যারা জীবনে একবার হলেও ট্রেনে চড়েনি, কোনো দিন রাজধানী ঢাকা শহর দেখেনি, তারাই ডিবি লটারির বরকতে আমেরিকায় এসে ক্রমে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে গেছে একসঙ্গে। কিন্তু কারও কারও পারিবারিক অশিক্ষাটা মূলেই থেকে গেছে। যেমন সাখিনা আপু। রিমার জবের ম্যানেজার। সাখিনা আপুর প্রকৃত নাম হয়তো সকিনা কিন্তু আমেরিকান উচ্চারণে তৈরি করে নিয়েছেন সাখিনা। সাখিনা আপুর অহংবোধের যাবতীয় আক্রোশের লক্ষ্যবস্তু ছিল একমাত্র রিমা।
রিমা বাংলাদেশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার চলনে-বলনে, আচরণে, কথায়-কাজে যেটুকু অভিব্যক্তি তার পুরোটাই সাখিনার মধ্যে অপূর্ণ। এই ভেদটুকু বুঝি প্রচণ্ড পীড়া দিত সাখিনা আপুকে। অগত্যা সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। অকারণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, কথায়-কাজে রিমাকে আঘাত করে বুঝি নিজে অন্য রকম এক স্বস্তি অনুভব করত। আচমকা অসময়ে রিমাকে আদেশ করত,
-যান তো আপু, স্টোরের সামনেটা একটু ঝাড়ু দিয়ে আসেন। কী নোংরা জমে গেছে। আমি এই কাজ পাঁচ বছর করেছি।
কিংবা অহেতুক আদেশ করে বসত,
-রিমাপু, কাস্টমারকে পাশের রুম থেকে চেয়ারটা টেনে দেন তো!
অথচ স্টোরের সামনে সদাই ঘোরাফেরা করা স্প্যানিশ লোকটাকে সারা মাসে ১০-২০ ডলার দিয়ে দিলে সব রকমের ফুটফরমাশ তাকে দিয়ে করানো যায়। আশপাশের স্টোরে সকলেই এভাবে করে।
কথায়, কাজে, দাপটে সাখিনা আপুর ব্যবহার এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে রিমার আত্মমর্যাদা শূন্যে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। জীবনবোধ, আত্মমর্যাদা ছাড়া মানুষ কী করে বাঁচে। অগত্যা চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে রিমা নিজের অহংবোধকে উজ্জীবিত করে।
আসলে পুরুষতান্ত্রিক অসমতার যুগে কোনো কোনো নারীই অপর নারীর শত্রু। সমাজ, সংস্কৃতি, কর্মে, দক্ষতায় কোনো নারী নিজের অবস্থান খানিকটা দৃঢ় করতে চাইলে অপর কোনো নারীই ঠ্যাং ধরে তাকে টেনেহিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আসে। কেবল নিজের অপূর্ণতা, নিজের অক্ষমতা আর প্রতিহিংসার কারণে।
তবে বাংলাদেশের নারীজীবনের চেয়ে আমেরিকান নারীজীবন অনেক অমর্যাদাপূর্ণ। বাংলাদেশে কয়েক দশক আগে থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান ছিল নারী। বিরোধীদলীয় প্রধান রূপেও নারী। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদেও বহুসংখ্যক নারী। অথচ বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকান বিশাল সাম্রাজ্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে নারীরা সবে এক পা দু’ পা করে এগোচ্ছে মাত্র।
বাংলাদেশে বিবাহ প্রথায় নারীকে যোগ্যতা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কাবিন নামক অর্থ প্রদানপূর্বক একজন পুরুষের সহধর্মিণী হয় নারী। কিন্তু আমেরিকায় বিবাহ ধর্মীয় প্রথায় সম্পন্ন করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কোনো বিষয় নয়। বিশেষ করে, আমেরিকায় নারীজীবন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতটাই মূল্যহীন যে একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই লিভ টুগেদারের নামে একজন নারীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিংবা নারীর স্বেচ্ছায় বিয়ে ছাড়াও যথেচ্ছ ভোগ করতে পারে বছরের পর বছর।
ঠিক সে রকমই বুঝি রিমার জীবনে ঘটতে যাচ্ছিল। তত দিনে রিমা আমেরিকান জীবনের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। জুড়িয়ে নিয়েছিল একফালি বেঁচে থাকাটাকে কোনো রকমে। কোটি মানুষের ভিড়ে আশাজাগানিয়া একটা জীবন। একটা জব, একটা ঘর, একটা বিছানা। একঝলক উনুনে ধোঁয়া ওঠা। চাল, ডাল, তেলের কিংবা সময়ের কোনো হিসাব কষতে হতো না। এক দুপুর, সকাল কিংবা রাতের খাবারটা উনুন জ্বলা ছাড়াও পার করে দেওয়া যেত প্যাকেটজাত খাবারে।
জ্যাকসন হাইটসে একটা শাড়ির দোকানে জবটা ছিল রিমার। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা। সপ্তাহে ছুটির দিনে মিশে যেত বাঙালিয়ানার কোন জম্পেশ উৎসবে। সেদিন নতুন শাড়ির ভাঁজ ভাঙে, খোঁপায় গুঁজে ফুল, কানে থাকে লতানো দুল। হাসি-কান্নার মিশেল জীবন পার হয়ে যাচ্ছিল নির্বিঘ্নে।
কিন্তু বিপত্তিটা তো তখনই বাধে, যখন মধ্যরাতে বেজে ওঠে রিমার মোবাইল ফোন। রিসিভারের অপর প্রান্তে স্বয়ং বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। রিমা এত রাতে ফোন পেয়ে অনেকটাই হতভম্ব হয়ে যায়। নিশ্চয় ভাড়ার টাকার তলবে ফোন। আসলে জবটা ছেড়ে দেওয়ায় দুই মাসের বকেয়া রয়ে গেছে। রিমা নতুন জবের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের গলার স্বরে এবার অন্য ধাঁচের প্রলোভন। শুরুটাই করে অন্য ভঙ্গিতে।
-আপনার ভাবি তো ছেলেপুলে নিয়া ভিজিটিংয়ে নিউইয়র্কের আউটসাইড গেছে। ভদ্রলোকের একটু গায়ে পড়া ভাব। আগে যখন তখন রিমাকে ফোন দিয়ে বসত। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল রিমা। যখন তখন বাড়িওয়ালার ফোন। সে ভুল করে দরজা খুলে চলে আসেনি তো। নাকি চুলা নেভাতেই ভুলে গেছে বলে পুরো বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু নাহ্, কিছুই না, নেহাত কুশলাদি বিনিময়ের জন্য বাড়িওয়ালার ফোন।
রিমা জানে, ভদ্রলোক অতীতে বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের একজন জবরদস্তর পিয়ন ছিল। ডিবি লটারি তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে তার সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার চলনে-বলনে, গলার স্বরে এখন অন্য রকম এক অহংকারী টান। মধ্যরাতেও ভদ্রলোক বেসুরো হাসতে থাকে।
রিমা অনন্যোপায়ে নির্বিকার হজম করতে চেষ্টা করতে থাকলেও শেষ কথাগুলোতে প্রচণ্ড রকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
-আমার অন্য দুইডা বাড়ির একটাত আপনি যাইয়া উডেন। ভাড়া দেওন লাগব না।
-কেন, কেন ভাড়া দেওয়া লাগবে না।
রিমা কুৎসিত প্রলোভনটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে।
ভদ্রলোক এবার আবেগে অতিশয় বিগলিত হয়ে জানান দেয়,
-এই ধরেন আমরা দুইজনে বন্ধু হইলাম। প্রিয় বন্ধু। আপনে খালি আপনের ভাবিরে জানায়েন না।
রিমা হিতাহিতজ্ঞানহীন হয়ে একরকম চেঁচিয়ে ওঠে,
-আপনি যদি কখনো আবার আমাকে কল দিয়েছেন, তাহলে আমি সত্যিই আগে আপনার ওয়াইফকে জানাব।
তার দিন সাতেক পরই ভদ্রলোক স্ত্রীসহ রিমার ঘরে এসে হাজির। দুজনেরই থমথমে চেহারা। খড়খড়ে গলার আওয়াজ।
-আগামী মাসে আমার বাড়িটা ছেড়ে দিবেন।
রিমা আর কথা বাড়ায় না। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না আক্রোশের কারণ। কিন্তু কী আশ্চর্য, রিমা লক্ষ করে, ভদ্রলোকের স্ত্রীও তার স্বামীর কথায় সায় দিয়ে অজান্তেই তার লাম্পট্যকে আরও তুঙ্গে তুলে দিচ্ছে। হায় অবলা নারী, সারা জীবন অতি কাছে থেকেও চিনতে পারলে না আপন পুরুষটিকে।
এরপর রিমা বেরিয়ে পড়ে বাইরে। আনমনে এসে দাঁড়ায় রোজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের হাডসন নদীর পাড়ে। জীবনের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের পালা বুঝি আজকেই তার শেষ। মাথার উপর সুবিস্তীর্ণ খোলা আকাশ আর সম্মুখে খলখলে প্রবাহিত হাডসন নদীর বিশাল জলস্রোত ছাড়া আর কিছুই নেই আর তার। অদূরেই শিশুদের কল্লোল আর টুকরো টুকরো কথার আওয়াজ রিমার কানে এসে আছড়ে পড়ে।
-হাই এথিনা, মাম কলিং ইউ।
ইংরেজিতে কথা বলছে কেউ। রিমাকেও বেশির ভাগ সময়ই ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলায় সবার সঙ্গে এখানে কথা বলা যায় না। রিমা ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে। নিজের দেশটাকে হারিয়ে ফেলেছে। সংসারটাকে হারিয়ে ফেলেছে। সাফোয়ানের অদম্য ভালোবাসাটাকে হারিয়ে ফেলেছে। আয়-রোজগারের চাকরিটাকে হারিয়ে ফেলেছে। শেষান্তে মাথা গোঁজার ঠাঁইটাকেও আজ হারিয়ে ফেলেছে। থাকল কী? পৃথিবীর তাবৎ দুঃখ-কষ্টের ইজারা সব বুঝি নিজের ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? কষ্টের আগুনে পোড় খাওয়া ঝলসানো জীবনটা অকারণে বয়ে বেড়ানোর দরকারটা কী? ফুরিয়ে গেছে জীবন, কেবল পড়ে আছে জীবন নামের শূন্য খোলস। আর তার ভারবাহিতা আজ এত বেশি যে আর সে বইতে পারছে না। দিশাহীন হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুতি নিতে থাকে। আচমকা নদীর স্রোত চোখ পড়ে তার। কুলু কুলু রবে বয়ে চলছে নদী। সামনেই বাঁক, পেছনেও বাঁক। নদী তো সব বাঁক পেরিয়েই ছুটছে, থেমে যায়নি তো কোনো। অদূরেই চোখে পড়ে পথ। বাঁক নিতে নিতে দূরে কোথাও মিশে গেছে, থেমে যায়নি তো পথ। মানুষের জীবনেও তো এমন দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার বাঁক আসে, তাহলে জীবন থেমে যাবে কেন? রিমা থেমে যাবে কেন? শুদ্ধতা হারিয়েছে আমেরিকায় কয়েকজন মানুষ। শুদ্ধতা হারিয়েছে বাংলাদেশের কয়েকজন মানুষ। রিমা তো নয়। রিমা তো এক বিশুদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সামনে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের মূর্তি মানুষের ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দম্ভভরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তো কেবল নিজের একক জীবনের কথা ভাবেননি। পুরো জাতির জীবন নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন বলেই বিশ্ব তাকে সারা জীবন মনে রেখেছে। আর রিমা কেবল নিজের একার জীবনটাই সমূলে বিনষ্ট করে দিতে চাচ্ছিল। চরম অনুশোচনায় রিমা ফিরে আসে নিজের চেতনার ভেতর। এতক্ষণে খেয়াল করে, নদীর ওপারে জ্যামিতিক নকশায় সুউচ্চ দালানগুলো ঝলমল আলোর দ্যুতিতে ভাসছে। নদীর দু’তীরে ভালোবাসার বন্ধন গড়েছে বুঝি হাডসন ব্রিজ। মাথার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ট্রামওয়ে ছুটছে। ব্রিজের ওপরে শাঁ শাঁ গাড়ি ছুটছে। জীবনের কী উদ্যম গতি। হু হু বাতাস বইছে। চারদিকে খোলা হাওয়া। নান্দনিক সৌন্দর্যে মনটা ভরে ওঠে তার।
প্রাণভরে নিঃশ্বাস টানে রিমা...।
ভরসন্ধ্যায় সে রোজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের হাডসন নদীর পাড় ধরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে একা। ভেতরটা তীব্র এক যন্ত্রণায় পুড়ছে। আসলেই কি সে এখন একা? না একা নয়। হাজার রকমের কষ্টের দানবরা তাদের পিণ্ডিচটকে একমাত্র রিমির মাথার ওপর ঠাঁই করে নিয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে সে। এসব কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছে এখানে কিন্তু কষ্টগুলোও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। দুঃখ, দুর্দশা তাকে ছাড়েনি।
সর্বশেষ আজকের ঘটনাটাই তার সবকিছু বদলে দিয়েছে। সে এত বেশি মর্মাহত হয়েছে যে এর থেকে কূলকিনারা পাওয়ার একটাই পথ। তাই শেষান্তে এই নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়।
আসলে বিপদের বুঝি সাত ভাই। এক ভাই উঁকি দিলে বাকি ছয় ভাই লাঠি, শাবল, দা, কুড়াল নিয়ে ভীষণ আকারে পাশে এসে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে আচমকা সাফোয়ানের মৃত্যু তার সবকিছু বদলে দিয়েছে। উল্টেপাল্টে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সাফোয়ানের মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠতম কষ্ট। সাফোয়ান আর নেই। আকস্মিক কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সাফোয়ান আর ফিরবে না ঘরে। কোনো দিনও আর ফিরবে না। এই ঘরে রিমা কেমন করে থাকবে এক।
সাফোয়ান চলে গেছে কিন্তু তার যাবতীয় কষ্টগুলো উগরে রেখে গেছে রিমার কাছে। মাতৃহারা সাফোয়ান তার বৈমাত্রেয় মা, ভাইদের আবাল্য শৈশবের যাবতীয় কষ্ট উগরে দিয়ে গেছে রিমার কাছে। একই গল্প সাফোয়ান রিমাকে বারবার বলেছে অবচেতন মনে। রিমা কান পেতে শ্রবণ করেছে কিন্তু কখনো ব্যক্ত করেনি এটা চেনা কাহিনি। আরও কয়েকবার সাফোয়ান তাকে বলেছে।
আসলে সাফোয়ান রিমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিজেকে নির্ভার করতে চেয়েছিল। কিন্তু পেরেছে কি? শেষ পর্যন্ত সামান্য জমিজমা-সম্পদের জন্য সাফোয়ানের বৈমাত্রেয় ভাইদের কূটকৌশলে নিজের প্রাণটুকু হারিয়ে ফেলল। সাফোয়ান আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার কষ্টগুলো সতেজ হয়ে বেঁচে আছে রিমার কাছে।
বিসিএস ক্যাডারভুক্ত হয়ে মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে সাফোয়ানের সঙ্গেই এক গাড়িতে রিমা আসা-যাওয়া করত। সে গাড়িতে রিমা একা একা কেমন করে যাবে। সাফোয়ানের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, গলার আওয়াজ চারদিকে ভোঁ ভোঁ বাতাসে ঘুরপাক খায় আর রিমা স্মৃতির দাপটে কোনো এক অতলান্তে তলিয়ে যায়। এর থেকে নিস্তার পেতেই সে বেছে নিয়েছে আমেরিকার প্রবাসী জীবন। তার ওপর সাফোয়ানের বৈমাত্রেয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের জাল তো আছেই।
সাফোয়ানের স্বল্পশিক্ষিত বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের প্রতিহিংসা আর লোভের আগুন এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছে সাফোয়ানের সম্ভাবনাময় জীবন। বংশের উজ্জ্বলতম প্রদীপখানি। তাদের বোধেও নেই কোন সম্পদ আসল আর কোন সম্পদ নকল। এরপর রিমা কি তাদের থেকে পরিত্রাণ পাবে? তাই তো সে আমেরিকান এই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। একাকীই আমেরিকায় চলে এসেছে।
আসলে আমেরিকায় যারা আসে, তারা কেউ প্রথমে একাই আসে। তারপর বত্রিশ জন সদস্যকে কেউ একসঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। এ রকম কাহিনি রিমা অনেক শুনেছে। এমনও আছে, বাংলাদেশে যারা জীবনে একবার হলেও ট্রেনে চড়েনি, কোনো দিন রাজধানী ঢাকা শহর দেখেনি, তারাই ডিবি লটারির বরকতে আমেরিকায় এসে ক্রমে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে গেছে একসঙ্গে। কিন্তু কারও কারও পারিবারিক অশিক্ষাটা মূলেই থেকে গেছে। যেমন সাখিনা আপু। রিমার জবের ম্যানেজার। সাখিনা আপুর প্রকৃত নাম হয়তো সকিনা কিন্তু আমেরিকান উচ্চারণে তৈরি করে নিয়েছেন সাখিনা। সাখিনা আপুর অহংবোধের যাবতীয় আক্রোশের লক্ষ্যবস্তু ছিল একমাত্র রিমা।
রিমা বাংলাদেশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার চলনে-বলনে, আচরণে, কথায়-কাজে যেটুকু অভিব্যক্তি তার পুরোটাই সাখিনার মধ্যে অপূর্ণ। এই ভেদটুকু বুঝি প্রচণ্ড পীড়া দিত সাখিনা আপুকে। অগত্যা সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। অকারণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, কথায়-কাজে রিমাকে আঘাত করে বুঝি নিজে অন্য রকম এক স্বস্তি অনুভব করত। আচমকা অসময়ে রিমাকে আদেশ করত,
-যান তো আপু, স্টোরের সামনেটা একটু ঝাড়ু দিয়ে আসেন। কী নোংরা জমে গেছে। আমি এই কাজ পাঁচ বছর করেছি।
কিংবা অহেতুক আদেশ করে বসত,
-রিমাপু, কাস্টমারকে পাশের রুম থেকে চেয়ারটা টেনে দেন তো!
অথচ স্টোরের সামনে সদাই ঘোরাফেরা করা স্প্যানিশ লোকটাকে সারা মাসে ১০-২০ ডলার দিয়ে দিলে সব রকমের ফুটফরমাশ তাকে দিয়ে করানো যায়। আশপাশের স্টোরে সকলেই এভাবে করে।
কথায়, কাজে, দাপটে সাখিনা আপুর ব্যবহার এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে রিমার আত্মমর্যাদা শূন্যে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। জীবনবোধ, আত্মমর্যাদা ছাড়া মানুষ কী করে বাঁচে। অগত্যা চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে রিমা নিজের অহংবোধকে উজ্জীবিত করে।
আসলে পুরুষতান্ত্রিক অসমতার যুগে কোনো কোনো নারীই অপর নারীর শত্রু। সমাজ, সংস্কৃতি, কর্মে, দক্ষতায় কোনো নারী নিজের অবস্থান খানিকটা দৃঢ় করতে চাইলে অপর কোনো নারীই ঠ্যাং ধরে তাকে টেনেহিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আসে। কেবল নিজের অপূর্ণতা, নিজের অক্ষমতা আর প্রতিহিংসার কারণে।
তবে বাংলাদেশের নারীজীবনের চেয়ে আমেরিকান নারীজীবন অনেক অমর্যাদাপূর্ণ। বাংলাদেশে কয়েক দশক আগে থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান ছিল নারী। বিরোধীদলীয় প্রধান রূপেও নারী। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদেও বহুসংখ্যক নারী। অথচ বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকান বিশাল সাম্রাজ্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে নারীরা সবে এক পা দু’ পা করে এগোচ্ছে মাত্র।
বাংলাদেশে বিবাহ প্রথায় নারীকে যোগ্যতা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কাবিন নামক অর্থ প্রদানপূর্বক একজন পুরুষের সহধর্মিণী হয় নারী। কিন্তু আমেরিকায় বিবাহ ধর্মীয় প্রথায় সম্পন্ন করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কোনো বিষয় নয়। বিশেষ করে, আমেরিকায় নারীজীবন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতটাই মূল্যহীন যে একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই লিভ টুগেদারের নামে একজন নারীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিংবা নারীর স্বেচ্ছায় বিয়ে ছাড়াও যথেচ্ছ ভোগ করতে পারে বছরের পর বছর।
ঠিক সে রকমই বুঝি রিমার জীবনে ঘটতে যাচ্ছিল। তত দিনে রিমা আমেরিকান জীবনের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। জুড়িয়ে নিয়েছিল একফালি বেঁচে থাকাটাকে কোনো রকমে। কোটি মানুষের ভিড়ে আশাজাগানিয়া একটা জীবন। একটা জব, একটা ঘর, একটা বিছানা। একঝলক উনুনে ধোঁয়া ওঠা। চাল, ডাল, তেলের কিংবা সময়ের কোনো হিসাব কষতে হতো না। এক দুপুর, সকাল কিংবা রাতের খাবারটা উনুন জ্বলা ছাড়াও পার করে দেওয়া যেত প্যাকেটজাত খাবারে।
জ্যাকসন হাইটসে একটা শাড়ির দোকানে জবটা ছিল রিমার। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা। সপ্তাহে ছুটির দিনে মিশে যেত বাঙালিয়ানার কোন জম্পেশ উৎসবে। সেদিন নতুন শাড়ির ভাঁজ ভাঙে, খোঁপায় গুঁজে ফুল, কানে থাকে লতানো দুল। হাসি-কান্নার মিশেল জীবন পার হয়ে যাচ্ছিল নির্বিঘ্নে।
কিন্তু বিপত্তিটা তো তখনই বাধে, যখন মধ্যরাতে বেজে ওঠে রিমার মোবাইল ফোন। রিসিভারের অপর প্রান্তে স্বয়ং বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। রিমা এত রাতে ফোন পেয়ে অনেকটাই হতভম্ব হয়ে যায়। নিশ্চয় ভাড়ার টাকার তলবে ফোন। আসলে জবটা ছেড়ে দেওয়ায় দুই মাসের বকেয়া রয়ে গেছে। রিমা নতুন জবের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের গলার স্বরে এবার অন্য ধাঁচের প্রলোভন। শুরুটাই করে অন্য ভঙ্গিতে।
-আপনার ভাবি তো ছেলেপুলে নিয়া ভিজিটিংয়ে নিউইয়র্কের আউটসাইড গেছে। ভদ্রলোকের একটু গায়ে পড়া ভাব। আগে যখন তখন রিমাকে ফোন দিয়ে বসত। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল রিমা। যখন তখন বাড়িওয়ালার ফোন। সে ভুল করে দরজা খুলে চলে আসেনি তো। নাকি চুলা নেভাতেই ভুলে গেছে বলে পুরো বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু নাহ্, কিছুই না, নেহাত কুশলাদি বিনিময়ের জন্য বাড়িওয়ালার ফোন।
রিমা জানে, ভদ্রলোক অতীতে বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের একজন জবরদস্তর পিয়ন ছিল। ডিবি লটারি তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে তার সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার চলনে-বলনে, গলার স্বরে এখন অন্য রকম এক অহংকারী টান। মধ্যরাতেও ভদ্রলোক বেসুরো হাসতে থাকে।
রিমা অনন্যোপায়ে নির্বিকার হজম করতে চেষ্টা করতে থাকলেও শেষ কথাগুলোতে প্রচণ্ড রকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
-আমার অন্য দুইডা বাড়ির একটাত আপনি যাইয়া উডেন। ভাড়া দেওন লাগব না।
-কেন, কেন ভাড়া দেওয়া লাগবে না।
রিমা কুৎসিত প্রলোভনটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে।
ভদ্রলোক এবার আবেগে অতিশয় বিগলিত হয়ে জানান দেয়,
-এই ধরেন আমরা দুইজনে বন্ধু হইলাম। প্রিয় বন্ধু। আপনে খালি আপনের ভাবিরে জানায়েন না।
রিমা হিতাহিতজ্ঞানহীন হয়ে একরকম চেঁচিয়ে ওঠে,
-আপনি যদি কখনো আবার আমাকে কল দিয়েছেন, তাহলে আমি সত্যিই আগে আপনার ওয়াইফকে জানাব।
তার দিন সাতেক পরই ভদ্রলোক স্ত্রীসহ রিমার ঘরে এসে হাজির। দুজনেরই থমথমে চেহারা। খড়খড়ে গলার আওয়াজ।
-আগামী মাসে আমার বাড়িটা ছেড়ে দিবেন।
রিমা আর কথা বাড়ায় না। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না আক্রোশের কারণ। কিন্তু কী আশ্চর্য, রিমা লক্ষ করে, ভদ্রলোকের স্ত্রীও তার স্বামীর কথায় সায় দিয়ে অজান্তেই তার লাম্পট্যকে আরও তুঙ্গে তুলে দিচ্ছে। হায় অবলা নারী, সারা জীবন অতি কাছে থেকেও চিনতে পারলে না আপন পুরুষটিকে।
এরপর রিমা বেরিয়ে পড়ে বাইরে। আনমনে এসে দাঁড়ায় রোজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের হাডসন নদীর পাড়ে। জীবনের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের পালা বুঝি আজকেই তার শেষ। মাথার উপর সুবিস্তীর্ণ খোলা আকাশ আর সম্মুখে খলখলে প্রবাহিত হাডসন নদীর বিশাল জলস্রোত ছাড়া আর কিছুই নেই আর তার। অদূরেই শিশুদের কল্লোল আর টুকরো টুকরো কথার আওয়াজ রিমার কানে এসে আছড়ে পড়ে।
-হাই এথিনা, মাম কলিং ইউ।
ইংরেজিতে কথা বলছে কেউ। রিমাকেও বেশির ভাগ সময়ই ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলায় সবার সঙ্গে এখানে কথা বলা যায় না। রিমা ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে। নিজের দেশটাকে হারিয়ে ফেলেছে। সংসারটাকে হারিয়ে ফেলেছে। সাফোয়ানের অদম্য ভালোবাসাটাকে হারিয়ে ফেলেছে। আয়-রোজগারের চাকরিটাকে হারিয়ে ফেলেছে। শেষান্তে মাথা গোঁজার ঠাঁইটাকেও আজ হারিয়ে ফেলেছে। থাকল কী? পৃথিবীর তাবৎ দুঃখ-কষ্টের ইজারা সব বুঝি নিজের ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? কষ্টের আগুনে পোড় খাওয়া ঝলসানো জীবনটা অকারণে বয়ে বেড়ানোর দরকারটা কী? ফুরিয়ে গেছে জীবন, কেবল পড়ে আছে জীবন নামের শূন্য খোলস। আর তার ভারবাহিতা আজ এত বেশি যে আর সে বইতে পারছে না। দিশাহীন হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুতি নিতে থাকে। আচমকা নদীর স্রোত চোখ পড়ে তার। কুলু কুলু রবে বয়ে চলছে নদী। সামনেই বাঁক, পেছনেও বাঁক। নদী তো সব বাঁক পেরিয়েই ছুটছে, থেমে যায়নি তো কোনো। অদূরেই চোখে পড়ে পথ। বাঁক নিতে নিতে দূরে কোথাও মিশে গেছে, থেমে যায়নি তো পথ। মানুষের জীবনেও তো এমন দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার বাঁক আসে, তাহলে জীবন থেমে যাবে কেন? রিমা থেমে যাবে কেন? শুদ্ধতা হারিয়েছে আমেরিকায় কয়েকজন মানুষ। শুদ্ধতা হারিয়েছে বাংলাদেশের কয়েকজন মানুষ। রিমা তো নয়। রিমা তো এক বিশুদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সামনে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের মূর্তি মানুষের ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দম্ভভরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তো কেবল নিজের একক জীবনের কথা ভাবেননি। পুরো জাতির জীবন নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন বলেই বিশ্ব তাকে সারা জীবন মনে রেখেছে। আর রিমা কেবল নিজের একার জীবনটাই সমূলে বিনষ্ট করে দিতে চাচ্ছিল। চরম অনুশোচনায় রিমা ফিরে আসে নিজের চেতনার ভেতর। এতক্ষণে খেয়াল করে, নদীর ওপারে জ্যামিতিক নকশায় সুউচ্চ দালানগুলো ঝলমল আলোর দ্যুতিতে ভাসছে। নদীর দু’তীরে ভালোবাসার বন্ধন গড়েছে বুঝি হাডসন ব্রিজ। মাথার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ট্রামওয়ে ছুটছে। ব্রিজের ওপরে শাঁ শাঁ গাড়ি ছুটছে। জীবনের কী উদ্যম গতি। হু হু বাতাস বইছে। চারদিকে খোলা হাওয়া। নান্দনিক সৌন্দর্যে মনটা ভরে ওঠে তার।
প্রাণভরে নিঃশ্বাস টানে রিমা...।
