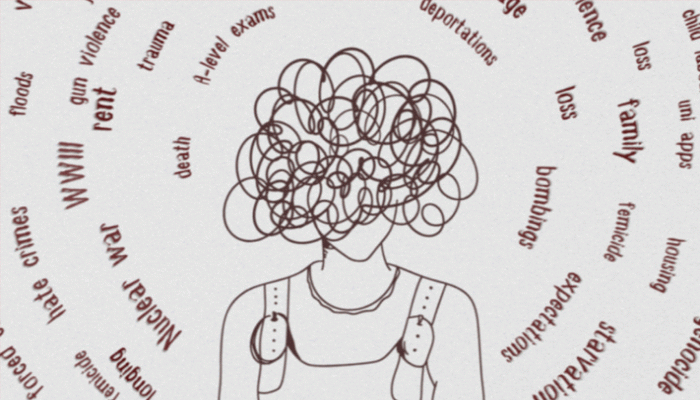
যুদ্ধ, বোমা হামলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঘৃণামূলক অপরাধ আর নারী নির্যাতনের খবর– ডিজিটাল যুগে এমন ভয়াবহ তথ্য এখন আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা চোখ সরাতে পারছি না স্ক্রিন থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষের মস্তিষ্ক কি এতো দ্রুত এতো নেতিবাচক তথ্য গ্রহণ করার জন্য তৈরি? নাকি ক্রমাগত এমন খবর দেখতে দেখতে আমাদের মন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে?
আগে খবর পেতে হলে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, অথবা কারও মারফত খবর আসতো। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। আমাদের প্রজন্ম জন্ম থেকেই দেখেছে কীভাবে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার স্ক্রল করলেই মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের সব খবর চলে আসে। সবাই যেন অন্যদের চেয়ে বেশি খবর জানার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
করাচির একটি স্নায়ুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শাফা রশীদ বলেছেন, ‘সঠিক মতামত দেওয়ার চাপ’ এবং কী বলা উচিত বা উচিত নয়, তা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে। এর ফলে আমাদের আবেগ আর ইন্দ্রিয়গুলো এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার শিকার হচ্ছে, যা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এখন একটি বড় সমস্যা।
আজকের দিনে ‘সচেতনতা’ যেন অতি-সচেতনতায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন থেকে শুরু করে একজন স্থানীয় প্রভাবশালীর কুকুরের হজমের সমস্যা পর্যন্ত সব খবরই এক ক্লিকে হাতের কাছে। খবর সহজেই পাওয়ার কারণে আমরা বিশ্বের নানা নৃশংসতা সম্পর্কে জানতে পারি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি, রাজনৈতিক অপপ্রচার চিনতে পারি। কিন্তু এর একটা বিশাল চাপ আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পড়ে, যার ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
আসলে সমস্যা খবরের সহজলভ্যতা নয়, বরং এর অন্তহীন প্রকৃতি। ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা থেকে কঙ্গোর ঘটনা, পাকিস্তানের বিতর্কিত নির্বাচন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসা, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বা ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, ভারত-বাংলাদেশের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা- দুঃখজনক খবর যেন শেষই হতে চায় না। আর তাই, এই ‘ডুমস্ক্রোলিং’ বা খারাপ খবর দেখতে থাকার প্রবণতাও কখনো থামে না।
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আফরাহ আরশাদ বলেন, বারবার দুঃখজনক খবর দেখতে দেখতে আমাদের মস্তিষ্ক এক ধরনের আবেগ ভারাক্রান্ততায় ডুবে যায়। এর ফলে মন নিজেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার কারণে মানসিক অসাড়তা বা অনুভূতিহীনতা দেখা দেয়। অনেক তরুণই এমন ‘ট্রিগারড’ বা ‘অভিভূত’ হওয়ার কথা বলেছেন। তারা শুরুতে আবেগপ্রবণ হলেও পরে এসব খবরে আর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখান না।
গত দুই বছরে অনেকেই দুঃখজনক খবরের প্রতি এক ধরনের উদাসীন হয়ে পড়েছেন। যারা নিয়মিত খবরের আপডেট বা সাহায্যের জন্য তথ্য শেয়ার করতেন, তারাও এখন তেমনটা করেন না। অনেক তরুণ-তরুণী মনে করেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার পেছনে এই মানসিক অবসাদও একটি কারণ। এমন পরিবেশে নিজেদের মানসিক সুস্থতা ধরে রাখাটা সত্যিই এক বড় চ্যালেঞ্জ। সূত্র : ডন
ঠিকানা/এসআর
আগে খবর পেতে হলে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, অথবা কারও মারফত খবর আসতো। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। আমাদের প্রজন্ম জন্ম থেকেই দেখেছে কীভাবে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার স্ক্রল করলেই মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের সব খবর চলে আসে। সবাই যেন অন্যদের চেয়ে বেশি খবর জানার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
করাচির একটি স্নায়ুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শাফা রশীদ বলেছেন, ‘সঠিক মতামত দেওয়ার চাপ’ এবং কী বলা উচিত বা উচিত নয়, তা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে। এর ফলে আমাদের আবেগ আর ইন্দ্রিয়গুলো এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার শিকার হচ্ছে, যা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এখন একটি বড় সমস্যা।
আজকের দিনে ‘সচেতনতা’ যেন অতি-সচেতনতায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন থেকে শুরু করে একজন স্থানীয় প্রভাবশালীর কুকুরের হজমের সমস্যা পর্যন্ত সব খবরই এক ক্লিকে হাতের কাছে। খবর সহজেই পাওয়ার কারণে আমরা বিশ্বের নানা নৃশংসতা সম্পর্কে জানতে পারি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি, রাজনৈতিক অপপ্রচার চিনতে পারি। কিন্তু এর একটা বিশাল চাপ আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পড়ে, যার ফলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
আসলে সমস্যা খবরের সহজলভ্যতা নয়, বরং এর অন্তহীন প্রকৃতি। ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা থেকে কঙ্গোর ঘটনা, পাকিস্তানের বিতর্কিত নির্বাচন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসা, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বা ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, ভারত-বাংলাদেশের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা- দুঃখজনক খবর যেন শেষই হতে চায় না। আর তাই, এই ‘ডুমস্ক্রোলিং’ বা খারাপ খবর দেখতে থাকার প্রবণতাও কখনো থামে না।
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আফরাহ আরশাদ বলেন, বারবার দুঃখজনক খবর দেখতে দেখতে আমাদের মস্তিষ্ক এক ধরনের আবেগ ভারাক্রান্ততায় ডুবে যায়। এর ফলে মন নিজেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার কারণে মানসিক অসাড়তা বা অনুভূতিহীনতা দেখা দেয়। অনেক তরুণই এমন ‘ট্রিগারড’ বা ‘অভিভূত’ হওয়ার কথা বলেছেন। তারা শুরুতে আবেগপ্রবণ হলেও পরে এসব খবরে আর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখান না।
গত দুই বছরে অনেকেই দুঃখজনক খবরের প্রতি এক ধরনের উদাসীন হয়ে পড়েছেন। যারা নিয়মিত খবরের আপডেট বা সাহায্যের জন্য তথ্য শেয়ার করতেন, তারাও এখন তেমনটা করেন না। অনেক তরুণ-তরুণী মনে করেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার পেছনে এই মানসিক অবসাদও একটি কারণ। এমন পরিবেশে নিজেদের মানসিক সুস্থতা ধরে রাখাটা সত্যিই এক বড় চ্যালেঞ্জ। সূত্র : ডন
ঠিকানা/এসআর
