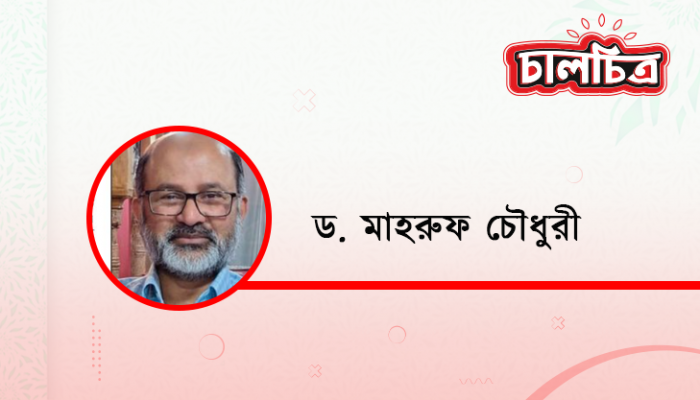
বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে এক নিঃস্বার্থ, স্বাধীন ও মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিসর; যেখানে সত্যের অনুসন্ধানই প্রধান সাধনা। আর সেখানেই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির পথ ধরে গড়ে ওঠে সমাজ সংস্কারের বুনিয়াদ। বিশ্ববিদ্যালয় একসময় কেবল পুঁথিগত বিদ্যার কেন্দ্র নয়, বরং তা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। সেখানে তৈরি হতো জিজ্ঞাসু মন, ন্যায়বোধসম্পন্ন নাগরিক এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। মধ্যযুগে ইউরোপে পোপের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল, সেভাবেই উপনিবেশ-উত্তর প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়কে কল্পনা করা হয়েছিল মুক্তচিন্তার আধার হিসেবে। কিন্তু আজকের বাস্তবতায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের বহু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আদর্শচিন্তা গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর কেবল জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা পরিণত হয়েছে স্বজনপ্রীতির বলয়ে আবদ্ধ, দুর্নীতির দ্বারা সংক্রমিত এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের বিনিময়ে সুবিধা আদায়ের এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে। এখানে জ্ঞান নয়, বরং ক্ষমতার বলয়, গোষ্ঠীগত আনুগত্য এবং ব্যক্তি-স্বার্থই হয়ে উঠছে প্রশাসনিক ও একাডেমিক সিদ্ধান্তের প্রধান নিয়ামক শক্তি।
এই বাস্তবতায় একটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় : বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, নাকি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তা হয়ে উঠেছে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও রাজনীতির এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ? পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদায়ন এবং সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্যতা ও সক্ষমতার তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও গোষ্ঠীগত আনুগত্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘আমার ছাত্র’, ‘আমার দলের লোক’ কিংবা ‘আমার এলাকার মানুষ’ এই পরিচিতিগুলোর ভিত্তিতে যারা সুযোগ পাচ্ছে, তারা প্রায়শই যোগ্যতায় দুর্বল হলেও অনায়াসে দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করছে। অদৃশ্য অথচ প্রবল এক ‘নেটওয়ার্কিং’ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা এখন আর গোপন নয়, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ফলে নিয়োগ বোর্ডের স্বচ্ছতা আজ গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। মেধা, গবেষণায় অবদান কিংবা একাডেমিক উৎকর্ষের চেয়ে কার সঙ্গে কার সম্পর্ক এই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে উঠেছে নিয়োগপ্রাপ্তি ও পদায়নের মাপকাঠি।
এমন পরিস্থিতিতে পিয়েরে বুরদিয়ুর ‘সাংস্কৃতিক পুঁজি’র ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর জ্ঞানচর্চার নৈতিক পুঁজি তৈরি করছে না; বরং এখানে রাজনৈতিক প্রভাব-বলয়ে সামাজিক পুঁজির অপপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার বৃত্ত তৈরি করা হচ্ছে। ফলে গোষ্ঠীগত অনুগত্যই সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে শুধু যে জ্ঞানচর্চার মান কমছে তা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামাজিক মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দুর্নীতি এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এটি যেন এক দুরারোগ্য কাঠামোগত ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে, যা একাডেমিক থেকে প্রশাসনিক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জাম কেনাকাটা, আবাসন ব্যবস্থা, এমনকি গবেষণার বাজেট কোনো কিছুই এই দুর্নীতির জাল থেকে মুক্ত নয়। বাস্তবে দেখা যায়, গবেষণার নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তার ফলাফল প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। গবেষণার উদ্দেশ্য যেখানে হওয়া উচিত জ্ঞান উৎপাদন, নীতিনির্ধারণে সহায়তা বা সামাজিক উন্নয়ন, সেখানে অনেক শিক্ষক প্রজেক্ট গ্রহণ করছেন কেবল আর্থিক লাভের আশায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্পের রিপোর্টই জমা পড়ে না, অথচ কাগজে-কলমে সবই ঠিকঠাক।
এই ‘কাজীর গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই’ প্রক্রিয়া অ্যান্তোনিও গ্রামশির ‘প্যাসিভ রেভ্যুলুশন’ ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের ছদ্মাবরণে মূলত বিদ্যমান ক্ষমতার বলয়ই পুনরুৎপাদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে দরপত্র ছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা মালামাল সরবরাহের কাজ ভাগ করে দেওয়া, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যবসায়ী বা ঠিকাদারদের নিয়মিত সুবিধা প্রদান এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার চূড়ান্ত অভাব সব মিলিয়ে এটি এক গভীরতর নৈতিক অবক্ষয়ের নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নতুন চিন্তা জন্ম নেওয়ার কথা, সেখানে এখন দুর্নীতির মাধ্যমে পুরোনো ক্ষমতার কাঠামোকেই কেবল আরও দৃঢ় করা হচ্ছে। ছাত্রাবাস থেকে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত এক অদৃশ্য দুর্নীতির বলয় তৈরি হয়েছে, যা ভাঙা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকেই ধ্বংস করছে না, বরং দেশের সামগ্রিক জ্ঞানীয় অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের ভিত্তিকেও বিপন্ন করে তুলছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষক রাজনীতি আজ আর আদর্শভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রিক চর্চা নয়; বরং তা হয়ে উঠেছে ক্ষমতা অর্জনের কৌশল এবং পেশাগত সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার এক দারুণ কার্যকর মাধ্যম। শিক্ষকেরা যাঁরা একসময় ছিলেন সমাজের নৈতিক দিকনির্দেশক, আজ তাদের অনেকেই দলীয় বিভাজনের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষক ফোরামগুলো নীতির পক্ষে নয়, বরং প্রশাসনিক পদ-পদবি ভাগাভাগির গোপন বোঝাপড়ায় ব্যস্ত। একসময় যে শিক্ষকতা ছিল জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রতীক, আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছে গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত ‘পেশাদার’ লেবাসধারী রাজনৈতিক দলদাস। ছাত্ররাজনীতির চিত্রটিও একইভাবে দুর্বিষহ। যেখানে ছাত্ররাজনীতি হওয়ার কথা ছিল মতপ্রকাশ, ন্যায়বোধ ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র, সেখানে তা অনেকাংশেই রূপ নিয়েছে সন্ত্রাস, নিয়ন্ত্রণ ও অনৈতিক সুবিধা আদায়ের হাতিয়ারে।
মিশেল ফুকোর ‘জ্ঞান ও ক্ষমতা’র পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে যদি দেখি, তবে এটি বোঝা যায়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটিও এখন ক্ষমতাচর্চার একটি অনুসারী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার প্রকৃত লক্ষ্য সত্য ও মানবিকতাকে তুলে ধরা নয়, বরং ক্ষমতার পুনরুৎপাদন। ছাত্রসংগঠনগুলো অনেক সময় ছাত্রদের প্রতিনিধি না হয়ে পরিণত হচ্ছে রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রূপ নিচ্ছে তাদের দখলদারিত্বের যুদ্ধক্ষেত্রে। ফলে শিক্ষক-ছাত্র উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের বদলে ক্ষমতার অনুশীলনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। আদর্শ, নীতি কিংবা মুক্তচিন্তার জায়গায় এসেছে পদোন্নতি, নিয়োগ এবং প্রশাসনিক পদলাভের প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি তাই আজ আর সমাজবদলের অনুঘটক নয়, বরং নিজস্ব ক্ষমতার বলয়ের ভিত শক্ত করার কৌশলমাত্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয় কি এক দিনে এ অবস্থায় পৌঁছেছে? না; তা একদমই নয়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল, যেখানে নীরব অনৈতিকতা, প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার এক অদৃশ্য কিন্তু সুগঠিত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে এই দুরবস্থার ভিত গড়ে তুলেছে।
রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেননি, অন্যদিকে জবাবদিহির কাঠামোও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তা এড়িয়ে গেছেন। ক্ষমতার বলয়ে থাকা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর সুবিধা নিশ্চিত করতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র না রেখে ‘নিয়ন্ত্রিত অধীনতার’ এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে দায় শুধু বাইরের নয়, ভেতরেরও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা বিবেকবান অংশ যাদের দায়িত্ব ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, প্রতিষ্ঠানকে নৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া, তারাও অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ, ভয় বা সুবিধাবাদের কারণে নীরব থেকেছেন। এ অবস্থা হান্না আরেন্ডের ‘মন্দের অস্বাভাবিকতা’ (বেনালিটি অব ইভিল) ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তি প্রতিদিনের অনৈতিকতার সঙ্গে আপস করতে করতে ধীরে ধীরে তার দায়বোধ হারিয়ে ফেলে। এই নৈতিক নিষ্ক্রিয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবক্ষয়কে আরও বেগবান করেছে। অতএব, দায় নির্দিষ্ট একটি পক্ষের নয়; এটি একটি সম্মিলিত ব্যর্থতা, যেখানে রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির প্রত্যেকেরই দায় রয়েছে।
সংগত কারণে প্রশ্ন করা যেতে পারে : তাহলে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী? কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার প্রকৃত চরিত্র জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, গবেষণার ক্ষেত্র এবং নৈতিক নেতৃত্ব তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এ কথা অনস্বীকার্য, এর জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে একটি নীতিনিষ্ঠ, পেশাদার ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে নিয়োগ ও পদায়নের প্রতিটি ধাপে; যেখানে ‘কে কার লোক’ নয়, বরং কে কতটা ‘যোগ্য ও সক্ষম’, সেটিই হবে মূল বিবেচ্য বিষয়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগে কঠোর, প্রকাশ্য নিয়মকানুন প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়নে স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও আপিল প্রক্রিয়া গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে গবেষণার গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য প্রণীত হতে পারে স্বতন্ত্র পিয়ার-রিভিউ কমিটি এবং প্রয়োজন দুর্নীতিবিরোধী স্বশাসিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা, যা সর্বাবস্থায় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকবে। এখানে দক্ষিণ কোরিয়া বা জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য; যেখানে গবেষণার মান, পেশাগত মূল্যায়ন ও স্বচ্ছতা একত্রে বিবেচিত হয়।
অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতিকে প্রতিরোধ নয়, বরং তাকে লেজুড়বৃত্তির বাইরে রেখে ইতিবাচক রূপান্তরের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা শেখানো, বিতর্ক, বৌদ্ধিক চর্চা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চা ছাত্ররাজনীতির কেন্দ্রে থাকতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের নেতৃত্ব নির্বাচনেও দলীয় আনুগত্য নয়; একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, গবেষণায় অবদান ও নৈতিক অবস্থান এই গুণগুলোই প্রধান হয়ে উঠবে। এসবকে মূল ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক সংস্কৃতি, যা রাজনৈতিক আনুগত্যের সংস্কৃতিকে দ্রুত মাটিচাপা দেবে। এভাবে একটি নতুন ধারার, নৈতিক ও পেশাগতভাবে পরিশীলিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে মূল শক্তি হবে জ্ঞানের সাধনা, গবেষণার বিস্তার ও মানবিক উৎকর্ষতা। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞান উৎপাদনের কেন্দ্র নয়, এটি একটি জাতির মেধা, মনন, নৈতিকতা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতীক। যে সমাজ তার বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মান দেয় না, স্বচ্ছ রাখে না, বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করে, সে সমাজ নিজের ভবিষ্যৎকেই অবমূল্যায়ন করে। অথচ আজ আমাদের বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও রাজনীতির দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ চক্র চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একাডেমিক ক্ষয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং গোটা সমাজের মূল্যবোধ, বিচারবোধ ও নৈতিক ভিত্তিও ভেঙে পড়বে।
বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মৌল আদর্শে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন এক সম্মিলিত নৈতিক জাগরণ, যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক এবং নীতিনির্ধারকেরা সকলে মিলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও পেশাদারিত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞানচর্চা কখনোই ক্ষমতার দাস হতে পারে না। যদি তা হয়, তবে সমাজ তার ভবিষ্যতের পথ হারাবে। যদি আমরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আত্মঘাতী প্রবণতাগুলোকে রুখে না দাঁড়াই এবং নীরব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার উপনিবেশে পরিণত হতে দিই, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কেবল অযোগ্য নেতৃত্ব, বিকৃত বিবেক আর আত্মপরতার নাগরিকই তৈরি করব। যারা জানবে না কীভাবে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে কিংবা কেন ন্যায়, জ্ঞান ও মূল্যবোধ ছাড়া কোনো জাতির দীর্ঘ সময় টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই এখনই উৎকৃষ্ট সময়, সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘ক্ষমতার উপনিবেশ’ থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়ার, যেন তা আবারও হয়ে উঠতে পারে চিন্তার মুক্তাঞ্চল, সত্যের অনুসন্ধানক্ষেত্র এবং একটি কল্যাণমুখী মানবিক রাষ্ট্রের রূপকার ও বাহক।
লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
এই বাস্তবতায় একটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় : বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, নাকি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তা হয়ে উঠেছে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও রাজনীতির এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ? পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদায়ন এবং সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্যতা ও সক্ষমতার তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও গোষ্ঠীগত আনুগত্যকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘আমার ছাত্র’, ‘আমার দলের লোক’ কিংবা ‘আমার এলাকার মানুষ’ এই পরিচিতিগুলোর ভিত্তিতে যারা সুযোগ পাচ্ছে, তারা প্রায়শই যোগ্যতায় দুর্বল হলেও অনায়াসে দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করছে। অদৃশ্য অথচ প্রবল এক ‘নেটওয়ার্কিং’ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা এখন আর গোপন নয়, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ফলে নিয়োগ বোর্ডের স্বচ্ছতা আজ গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। মেধা, গবেষণায় অবদান কিংবা একাডেমিক উৎকর্ষের চেয়ে কার সঙ্গে কার সম্পর্ক এই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে উঠেছে নিয়োগপ্রাপ্তি ও পদায়নের মাপকাঠি।
এমন পরিস্থিতিতে পিয়েরে বুরদিয়ুর ‘সাংস্কৃতিক পুঁজি’র ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর জ্ঞানচর্চার নৈতিক পুঁজি তৈরি করছে না; বরং এখানে রাজনৈতিক প্রভাব-বলয়ে সামাজিক পুঁজির অপপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার বৃত্ত তৈরি করা হচ্ছে। ফলে গোষ্ঠীগত অনুগত্যই সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে শুধু যে জ্ঞানচর্চার মান কমছে তা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামাজিক মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দুর্নীতি এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এটি যেন এক দুরারোগ্য কাঠামোগত ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে, যা একাডেমিক থেকে প্রশাসনিক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জাম কেনাকাটা, আবাসন ব্যবস্থা, এমনকি গবেষণার বাজেট কোনো কিছুই এই দুর্নীতির জাল থেকে মুক্ত নয়। বাস্তবে দেখা যায়, গবেষণার নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তার ফলাফল প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। গবেষণার উদ্দেশ্য যেখানে হওয়া উচিত জ্ঞান উৎপাদন, নীতিনির্ধারণে সহায়তা বা সামাজিক উন্নয়ন, সেখানে অনেক শিক্ষক প্রজেক্ট গ্রহণ করছেন কেবল আর্থিক লাভের আশায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্পের রিপোর্টই জমা পড়ে না, অথচ কাগজে-কলমে সবই ঠিকঠাক।
এই ‘কাজীর গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই’ প্রক্রিয়া অ্যান্তোনিও গ্রামশির ‘প্যাসিভ রেভ্যুলুশন’ ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের ছদ্মাবরণে মূলত বিদ্যমান ক্ষমতার বলয়ই পুনরুৎপাদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে দরপত্র ছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা মালামাল সরবরাহের কাজ ভাগ করে দেওয়া, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যবসায়ী বা ঠিকাদারদের নিয়মিত সুবিধা প্রদান এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার চূড়ান্ত অভাব সব মিলিয়ে এটি এক গভীরতর নৈতিক অবক্ষয়ের নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নতুন চিন্তা জন্ম নেওয়ার কথা, সেখানে এখন দুর্নীতির মাধ্যমে পুরোনো ক্ষমতার কাঠামোকেই কেবল আরও দৃঢ় করা হচ্ছে। ছাত্রাবাস থেকে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত এক অদৃশ্য দুর্নীতির বলয় তৈরি হয়েছে, যা ভাঙা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকেই ধ্বংস করছে না, বরং দেশের সামগ্রিক জ্ঞানীয় অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের ভিত্তিকেও বিপন্ন করে তুলছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষক রাজনীতি আজ আর আদর্শভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রিক চর্চা নয়; বরং তা হয়ে উঠেছে ক্ষমতা অর্জনের কৌশল এবং পেশাগত সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার এক দারুণ কার্যকর মাধ্যম। শিক্ষকেরা যাঁরা একসময় ছিলেন সমাজের নৈতিক দিকনির্দেশক, আজ তাদের অনেকেই দলীয় বিভাজনের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষক ফোরামগুলো নীতির পক্ষে নয়, বরং প্রশাসনিক পদ-পদবি ভাগাভাগির গোপন বোঝাপড়ায় ব্যস্ত। একসময় যে শিক্ষকতা ছিল জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রতীক, আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছে গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত ‘পেশাদার’ লেবাসধারী রাজনৈতিক দলদাস। ছাত্ররাজনীতির চিত্রটিও একইভাবে দুর্বিষহ। যেখানে ছাত্ররাজনীতি হওয়ার কথা ছিল মতপ্রকাশ, ন্যায়বোধ ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র, সেখানে তা অনেকাংশেই রূপ নিয়েছে সন্ত্রাস, নিয়ন্ত্রণ ও অনৈতিক সুবিধা আদায়ের হাতিয়ারে।
মিশেল ফুকোর ‘জ্ঞান ও ক্ষমতা’র পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে যদি দেখি, তবে এটি বোঝা যায়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটিও এখন ক্ষমতাচর্চার একটি অনুসারী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার প্রকৃত লক্ষ্য সত্য ও মানবিকতাকে তুলে ধরা নয়, বরং ক্ষমতার পুনরুৎপাদন। ছাত্রসংগঠনগুলো অনেক সময় ছাত্রদের প্রতিনিধি না হয়ে পরিণত হচ্ছে রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রূপ নিচ্ছে তাদের দখলদারিত্বের যুদ্ধক্ষেত্রে। ফলে শিক্ষক-ছাত্র উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের বদলে ক্ষমতার অনুশীলনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। আদর্শ, নীতি কিংবা মুক্তচিন্তার জায়গায় এসেছে পদোন্নতি, নিয়োগ এবং প্রশাসনিক পদলাভের প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি তাই আজ আর সমাজবদলের অনুঘটক নয়, বরং নিজস্ব ক্ষমতার বলয়ের ভিত শক্ত করার কৌশলমাত্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয় কি এক দিনে এ অবস্থায় পৌঁছেছে? না; তা একদমই নয়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফল, যেখানে নীরব অনৈতিকতা, প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার এক অদৃশ্য কিন্তু সুগঠিত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে এই দুরবস্থার ভিত গড়ে তুলেছে।
রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেননি, অন্যদিকে জবাবদিহির কাঠামোও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তা এড়িয়ে গেছেন। ক্ষমতার বলয়ে থাকা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর সুবিধা নিশ্চিত করতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র না রেখে ‘নিয়ন্ত্রিত অধীনতার’ এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে দায় শুধু বাইরের নয়, ভেতরেরও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা বিবেকবান অংশ যাদের দায়িত্ব ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, প্রতিষ্ঠানকে নৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া, তারাও অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ, ভয় বা সুবিধাবাদের কারণে নীরব থেকেছেন। এ অবস্থা হান্না আরেন্ডের ‘মন্দের অস্বাভাবিকতা’ (বেনালিটি অব ইভিল) ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তি প্রতিদিনের অনৈতিকতার সঙ্গে আপস করতে করতে ধীরে ধীরে তার দায়বোধ হারিয়ে ফেলে। এই নৈতিক নিষ্ক্রিয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবক্ষয়কে আরও বেগবান করেছে। অতএব, দায় নির্দিষ্ট একটি পক্ষের নয়; এটি একটি সম্মিলিত ব্যর্থতা, যেখানে রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির প্রত্যেকেরই দায় রয়েছে।
সংগত কারণে প্রশ্ন করা যেতে পারে : তাহলে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী? কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার প্রকৃত চরিত্র জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, গবেষণার ক্ষেত্র এবং নৈতিক নেতৃত্ব তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এ কথা অনস্বীকার্য, এর জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে একটি নীতিনিষ্ঠ, পেশাদার ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে নিয়োগ ও পদায়নের প্রতিটি ধাপে; যেখানে ‘কে কার লোক’ নয়, বরং কে কতটা ‘যোগ্য ও সক্ষম’, সেটিই হবে মূল বিবেচ্য বিষয়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগে কঠোর, প্রকাশ্য নিয়মকানুন প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়নে স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও আপিল প্রক্রিয়া গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে গবেষণার গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য প্রণীত হতে পারে স্বতন্ত্র পিয়ার-রিভিউ কমিটি এবং প্রয়োজন দুর্নীতিবিরোধী স্বশাসিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা, যা সর্বাবস্থায় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকবে। এখানে দক্ষিণ কোরিয়া বা জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য; যেখানে গবেষণার মান, পেশাগত মূল্যায়ন ও স্বচ্ছতা একত্রে বিবেচিত হয়।
অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতিকে প্রতিরোধ নয়, বরং তাকে লেজুড়বৃত্তির বাইরে রেখে ইতিবাচক রূপান্তরের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা শেখানো, বিতর্ক, বৌদ্ধিক চর্চা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চা ছাত্ররাজনীতির কেন্দ্রে থাকতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের নেতৃত্ব নির্বাচনেও দলীয় আনুগত্য নয়; একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, গবেষণায় অবদান ও নৈতিক অবস্থান এই গুণগুলোই প্রধান হয়ে উঠবে। এসবকে মূল ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক সংস্কৃতি, যা রাজনৈতিক আনুগত্যের সংস্কৃতিকে দ্রুত মাটিচাপা দেবে। এভাবে একটি নতুন ধারার, নৈতিক ও পেশাগতভাবে পরিশীলিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে মূল শক্তি হবে জ্ঞানের সাধনা, গবেষণার বিস্তার ও মানবিক উৎকর্ষতা। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞান উৎপাদনের কেন্দ্র নয়, এটি একটি জাতির মেধা, মনন, নৈতিকতা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতীক। যে সমাজ তার বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মান দেয় না, স্বচ্ছ রাখে না, বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করে, সে সমাজ নিজের ভবিষ্যৎকেই অবমূল্যায়ন করে। অথচ আজ আমাদের বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও রাজনীতির দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ চক্র চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একাডেমিক ক্ষয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং গোটা সমাজের মূল্যবোধ, বিচারবোধ ও নৈতিক ভিত্তিও ভেঙে পড়বে।
বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মৌল আদর্শে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন এক সম্মিলিত নৈতিক জাগরণ, যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসক এবং নীতিনির্ধারকেরা সকলে মিলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও পেশাদারিত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞানচর্চা কখনোই ক্ষমতার দাস হতে পারে না। যদি তা হয়, তবে সমাজ তার ভবিষ্যতের পথ হারাবে। যদি আমরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আত্মঘাতী প্রবণতাগুলোকে রুখে না দাঁড়াই এবং নীরব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার উপনিবেশে পরিণত হতে দিই, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কেবল অযোগ্য নেতৃত্ব, বিকৃত বিবেক আর আত্মপরতার নাগরিকই তৈরি করব। যারা জানবে না কীভাবে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে কিংবা কেন ন্যায়, জ্ঞান ও মূল্যবোধ ছাড়া কোনো জাতির দীর্ঘ সময় টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই এখনই উৎকৃষ্ট সময়, সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘ক্ষমতার উপনিবেশ’ থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়ার, যেন তা আবারও হয়ে উঠতে পারে চিন্তার মুক্তাঞ্চল, সত্যের অনুসন্ধানক্ষেত্র এবং একটি কল্যাণমুখী মানবিক রাষ্ট্রের রূপকার ও বাহক।
লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
