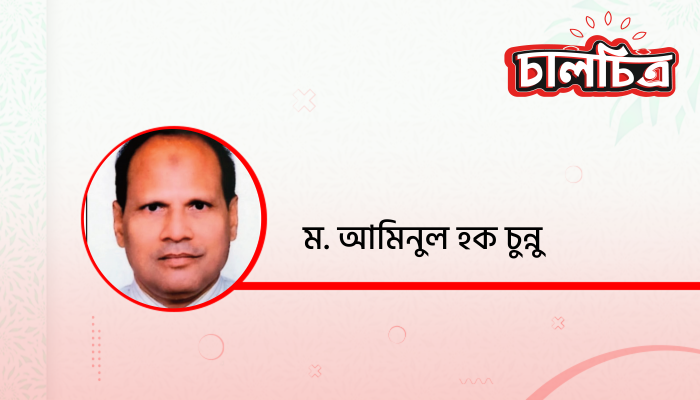
(গত সপ্তাহের পর)
প্রাচীনকালের মানুষ আজকের মানুষের চাইতে কম জ্ঞানপিপাসু ছিল না। কিন্তু আধুনিক সময়ের পুস্তক-সমন্বিত গ্রন্থাগারের কথা প্রাচীনকালের মানুষ ভাবতেও পারেনি। গুরুপ্রদত্ত মহামূল্যবান জ্ঞানরাজি শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা মুখস্থ করে স্মৃতিপটে ধরে রাখতেন এবং লোকপরম্পরায় জ্ঞানপিপাসু মানুষ তা আয়ত্ত করতেন। তারপর চিন্তাশীল মানুষ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানরাজি তালপত্রে, ভূর্জপত্রে বা শিলাখণ্ডে এমনকি পশুচর্মে লিপিবদ্ধ করে একত্র করে রাখতেন। তাই আজকের গ্রন্থাগারের আসল চেহারা, যা পূর্বের মূল কাঠামো ছিল। তারপর মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বহুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষের জ্ঞান অর্জনের চাহিদা মেটাতে লাগল। আর বিভিন্ন জ্ঞানধারার বহুসংখ্যক বইয়ের সঞ্চয়নে প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রন্থাগার রূপে। অতল জ্ঞানসমুদ্ররূপে এই গ্রন্থাগার সভ্য মানবজীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাধিয়া রাখিতে পারি তো যে ঘুমন্ত শিশুর মত চুপ করিয়া থাকি তো তবে সেই নীরব মহাসক্তির সাথে গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। মানবতার ওমর আলোকে কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ের মাথায় কঠিন তুষারের যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি মানব হৃদয়ের বন্যা সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।’ কিন্তু আমাদের দেশে যেসব গ্রন্থাগার আছে, তা দেশের জনগণের অন্ধকার মোচনে একেবারেই অপ্রতুল, যা লক্ষ কোটি জনগণের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে অসমর্থ, তা একেবারেই সিন্দুকে রাবিবিন্দুরই মতো। জাতির সর্বগ্রাসী ব্যাধি অশিক্ষাকে নির্মূল করতে প্রতিটি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন জনগণকে গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান। সে জন্য প্রধান ভূমিকা নিতে হবে সরকার ও দেশের যুবসমাজকে। তা ছাড়া একমাত্র গ্রন্থাগারই পারে ক্লান্ত, বুভুক্ষু মানুষের মনকে প্রফুল্ল করতে, তাকে পছন্দমাফিক জিনিসের স্থান দিয়ে তার মনের খোরাক জোগাতে।
গ্রন্থাগারে পাঠক সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার স্পর্শ পায়, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের হৃদয় কল্লোল। শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতান ধ্বনি। দেশে দেশে হৃদয়ে রচিত হয় অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন। তবে ধারণা করা হয়, প্রাচীন রোমে সর্বসাধারণের জন্য প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। তবে এর আগে অনুমান করা যায়, গ্রন্থাগার ছিল যা ব্যাবিলনের ভূগর্ভ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য এক ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে অর্থাৎ ১৯৫৪ ইংরেজির ৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। তাই দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ইতিহাস বলার কারণ স্পষ্ট হয় মানবসভ্যতার বিকাশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আগে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
লাইব্রেরি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের বলছিলাম লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার উপকারিতার কথা। আর বলছিলাম আমি বা আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন নিয়মিত লাইব্রেরিতে যেতাম। ওখানে গিয়ে ক্লাসে যেই বই ফলো করা হতো, তার বাইরে অন্য বইগুলো নিয়ে বসতাম পড়তাম এবং সেগুলো থেকে নোট তৈরি করতাম। ছাত্ররা তখন একযোগে বলে উঠল, স্যার, এখন তো লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই, বসার স্থান পাওয়া কঠিন, সেইখানে সবাই বিসিএস প্রস্তুতির জন্য সকালবেলায় লাইন দিয়ে সমস্ত জায়গা দখল করে ফেলে। নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর কোনো জায়গা থাকে না। আমি শুনে আশ্চর্য। একটা বিশ্ববিদ্যালয় কি এমন হতে পারে?’
ছাত্ররা লাইব্রেরিতে যাবে না, ক্লাসে শিক্ষক যে বই ফলো করেন, সেই বই দেখবে না, সেই বইয়ের বাইরে এসে বিষয়ের অন্য বই পড়বে না, বিভিন্ন দৈনিক ও ম্যাগাজিন জার্নাল পড়বে না। এ কি হতে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি মানের বিশাল একটি লাইব্রেরি আছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন দেখেছি সমসাময়িক জার্নাল ও বইয়ে যতটা না সমৃদ্ধ, তার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ পুরোনো জার্নাল ও বইয়ে। অন্যদিকে আমাদের দেশে অর্থাৎ এমনও আছে, যেখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এমনকি ২০-৩০টা গ্রামের মাঝে একটিও লাইব্রেরি নেই। তখন মনে হয়, বাংলাদেশ কী বিচিত্র দেশ। অতএব, দেশের যুব ও শিক্ষিত সমাজ এই দেশের শহর বন্দর তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পাঠাগার স্থাপনে সাম্প্রতিক সময়ে এগিয়ে আসবে।
জাতীয় জীবনকে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশের সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষালাভ সহজ হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরি, ফ্রান্সের বি ব্লিওথিক লাইব্রেরি, রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগ্রাদ শহরের লাইব্রেরি, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং ভারতের কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বিশ্বব্যাপীখ্যাত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরি এবং কিছুসংখ্যক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আছে।
তবে পৃথিবীর প্রথম বইমেলা কোথায় বসেছিল, খুঁজতে গেলে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের নাম আসে। দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময় হাতে লেখা বইয়ের পসরা বসেছিল ওই শহরের বাণিজ্য মেলায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী মাইনৎস শহরে এবং ইউহানেস গুটেনবার্গে ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। ছাপাখানার বই নিয়ে প্রথম বইমেলা বসে ফ্রাঙ্কফুর্টে ১৪৬২ সালে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের উৎসব হিসেবে পালিত বইমেলার গোড়াপত্তন ফ্রাঙ্কফুর্টের ওই বইমেলা থেকেই। তবে বাংলাদেশের বইমেলা অন্যান্য সব দেশের বইমেলা থেকে এক অন্য রকম বৈশিষ্ট্য ভাস্বর। বাংলাদেশের বইমেলা বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক। আর বাংলাদেশের জন্য আত্মাহুতি এই ভাষাতাত্ত্বিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উৎস। তা ছাড়া একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। হাজার বছরের বাঙালির সবচেয়ে বড় বিজয় সূচিত হলো। বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ তো আছেই। এই সমস্ত উদ্্যাপনের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা-সংবলিত উৎসব বইমেলা।
মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ঢাকার প্রকাশনাশিল্প পেয়েছে নতুন প্রাণ, নিজস্ব সত্তা। মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা সেই ১৯৭২ সালে বীজ বপন করলেন বইমেলার। বাংলা একাডেমির বটতলায় চটের ওপর মাত্র ৩২টি বই নিয়ে সাজানো সেই বইমেলার গল্প আমাদের জানা। এখন সেই বইমেলা বাংলা একাডেমি চত্বর ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দখল করে নিয়েছে। বইমেলাকে ঘিরে হাজার হাজার বই প্রকাশ হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার বেচাকেনা। মফস্বল শহরগুলোতেও বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। দেশের বাইরে লন্ডন, ফ্রান্স, নিউইয়র্কের মতো বড় বড় শহরে আয়োজন হচ্ছে বাঙালিদের বইমেলা। ধীরে ধীরে পুরান ঢাকার বাংলাবাজার ছাড়িয়ে বইমেলা ছড়িয়ে পড়েছে নতুন ঢাকায় নতুন আঙ্গিকে। তা ছাড়া পশ্চিম বাংলাতেও এখন বাংলা বইয়ের রমরমা অবস্থা।
শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একবার বলেছিলেন, ‘ঢাকা শহরে এখন প্রতিটি অলিগলিতে খাবারের দোকান বাড়ছে, প্রতি দোকানেই ভিড় করছে তরুণেরা অথচ সে তুলনায় লাইব্রেরির সংখ্যা তো বাড়েইনি বরং কমে গেছে।’
একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাবে লাইব্রেরির প্রতি মানুষের অনীহা কতটা। ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় ২৩টি পাঠাগার ছিল। বর্তমানে তা ৭টিতে নেমে এসেছে। অথচ ঢাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ!
দেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৪ থেকে ৩০ বছর, যাদেরকে আমরা কিশোর কিংবা তরুণ বলে থাকি। তরুণদের দেখা যায় গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়তে, তাদের দেখা যায় ইভটিজিং, ধর্ষণ, এমনকি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়াতে। এ জন্য কি শুধু তারাই দায়ী?
মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্পে আক্রান্ত গোটা সমাজ। মাদকের থাবায় আক্রান্ত হতাশাগ্রস্ত তরুণসমাজ ধীরে ধীরে পা বাড়ায় অপরাধের দিকে। খুন, টেন্ডারবাজি, রাজনৈতিক মাস্তানি, জমি দখল ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসীদের অনেকেই ভাড়ায় খাটে।
ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে একটি গোষ্ঠী তরুণদের ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে যেমন গহনা হয় না, প্রয়োজন হয় খাদের; তেমনি পরিপূর্ণ মানুষ হতে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকাও আবশ্যক। আমাদের সমাজে বর্তমানে খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির রয়েছে অপর্যাপ্ততা। ফলে ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত চাপ, পুরোনো ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা ও মুখস্থবিদ্যার প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অল্প বয়সেই পড়াশোনার প্রতি একধরনের অনীহা সৃষ্টি হয়।
জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, ‘হে প্রভু, তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও, যাতে আমি আরও বেশি করে বই পড়তে পারি। এমন প্রার্থনা তার পক্ষে করা সম্ভব, যিনি আজীবন জ্ঞান সাধনা করেছেন এবং জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন। আমরা যারা সাধারণ তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কিছুই চাই কিন্তু বইপড়ার জন্য বেঁচে থাকার আকুতি জানাই না। এখানেই হলো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন জ্ঞানসাধকের পার্থক্য।’
প্রাচীন চীনা সভ্যতায় বেশ কিছু জ্ঞানসাধক ছিলেন, যারা জ্ঞানসাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যতিক্রম প্রক্রিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরূপ একজন জ্ঞানসাধকের কথা জানা যায়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। রাতের বেলায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেল কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। এ মানুষটি বেশ কিছু জোনাকি পোকাকে বোতলে ভরে সেগুলোর আলোতে রাতের বেলায় বই পড়তেন। আরেকজন জ্ঞানসাধকের কথা জানা যায়, যিনি তার মাথার চুল রশি দিয়ে ঘরের আড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন।
গভীর রাতে বই পড়তে পড়তে ঝিমুনি এলে রশিতে বাঁধা চুলগুলোতে টান পড়ত, ফলে তার ঝিমুনি কেটে যেত। বর্তমান বাংলাদেশেও দুর্বৃত্ত কালচারে এ ধরনের মানুষকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করা হয়। সমাজে জ্ঞানের কদর নেই, কিন্তু বিত্তের কদর আছে। সে জন্যই মুষ্টিমেয় সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষ যারা এখনো বাংলাদেশের সমাজে টিকে আছেন। তাদের অনেক সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়। এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য বিত্তশালীরাই করে না, রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যারা আপনজন, তারাও ওই ব্যাপারে কম নন।
আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র পরিসর নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের বইমেলার। স্বাধীন বাংলাদেশের নবীনকালে এর সূচনা হলেও বর্তমানে বইমেলা একটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ ঘিরে ১৯৭৫-এ ফেব্রুয়ারি মাসে যে বইমেলা শুরু হয়েছিল অত্যন্ত দীনহীনভাবে, বর্তমানে সেই বইমেলা বাংলা একাডেমির চত্বর ও মাঠ ছাড়িয়ে বইয়ের সুবিশাল রাস্তার দু’ধারের দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ থেকে। কখনো যেন এর ঘাটতি না ঘটে।
বইমেলা বাংলা ভাষার জাগরণ আর বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আমাদের জাতিসত্তার একটি অনিবার্য মাইলফলক। বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকের মাঝে এক চমৎকার সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের নামকরা লেখকদের সঙ্গে সমানতালে অসংখ্য নবীন লেখক জেগে উঠেছে। লেখকদের অংশগ্রহণের ফলে বইমেলায় প্রচুর সমাগম ঘটে থাকে এবং বাংলা একাডেমির নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে মাসব্যাপী বইমেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।
তা ছাড়া প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে সরকারিভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই বইমেলার জন্ম হয়েছিল নব্বইয়ের গোড়ার দিকে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ছাড়াও বিশ্বের কয়েকটি দেশের প্রকাশনা স্থান পায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। বর্তমানে আরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে।
তবে ইদানীং সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। হেন অপরাধ নেই, যা আজ বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে না। এসব অপরাধ নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার সব সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য অনেক কারণই দায়ী। তবে গ্রন্থবিমুখতা কম দায়ী নয়। যদি দেশব্যাপী বইপড়ার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করা সম্ভব হতো, তাহলে হয়তো সামাজিক মালিন্য অনেকটা হ্রাস পেত।
মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। কোনো খারাপ আসক্তিকে দূর করতে হলে ভালো কোনো আসক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদিক থেকে পাঠের প্রতি আসক্তি খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু পাঠ করার কথা বলব কেন? দেশকে জানা, সমাজকে জানা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করাও বড় ধরনের কাজ। এর ফলে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। (ক্রমশ)
লেখক : লোকসংস্কৃতি গবেষক ও প্রাবন্ধিক। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট। পিএইচডি ফেলো, নিউইয়র্ক।
প্রাচীনকালের মানুষ আজকের মানুষের চাইতে কম জ্ঞানপিপাসু ছিল না। কিন্তু আধুনিক সময়ের পুস্তক-সমন্বিত গ্রন্থাগারের কথা প্রাচীনকালের মানুষ ভাবতেও পারেনি। গুরুপ্রদত্ত মহামূল্যবান জ্ঞানরাজি শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা মুখস্থ করে স্মৃতিপটে ধরে রাখতেন এবং লোকপরম্পরায় জ্ঞানপিপাসু মানুষ তা আয়ত্ত করতেন। তারপর চিন্তাশীল মানুষ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানরাজি তালপত্রে, ভূর্জপত্রে বা শিলাখণ্ডে এমনকি পশুচর্মে লিপিবদ্ধ করে একত্র করে রাখতেন। তাই আজকের গ্রন্থাগারের আসল চেহারা, যা পূর্বের মূল কাঠামো ছিল। তারপর মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বহুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষের জ্ঞান অর্জনের চাহিদা মেটাতে লাগল। আর বিভিন্ন জ্ঞানধারার বহুসংখ্যক বইয়ের সঞ্চয়নে প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রন্থাগার রূপে। অতল জ্ঞানসমুদ্ররূপে এই গ্রন্থাগার সভ্য মানবজীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাধিয়া রাখিতে পারি তো যে ঘুমন্ত শিশুর মত চুপ করিয়া থাকি তো তবে সেই নীরব মহাসক্তির সাথে গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। মানবতার ওমর আলোকে কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ের মাথায় কঠিন তুষারের যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি মানব হৃদয়ের বন্যা সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।’ কিন্তু আমাদের দেশে যেসব গ্রন্থাগার আছে, তা দেশের জনগণের অন্ধকার মোচনে একেবারেই অপ্রতুল, যা লক্ষ কোটি জনগণের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে অসমর্থ, তা একেবারেই সিন্দুকে রাবিবিন্দুরই মতো। জাতির সর্বগ্রাসী ব্যাধি অশিক্ষাকে নির্মূল করতে প্রতিটি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন জনগণকে গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান। সে জন্য প্রধান ভূমিকা নিতে হবে সরকার ও দেশের যুবসমাজকে। তা ছাড়া একমাত্র গ্রন্থাগারই পারে ক্লান্ত, বুভুক্ষু মানুষের মনকে প্রফুল্ল করতে, তাকে পছন্দমাফিক জিনিসের স্থান দিয়ে তার মনের খোরাক জোগাতে।
গ্রন্থাগারে পাঠক সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার স্পর্শ পায়, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের হৃদয় কল্লোল। শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতান ধ্বনি। দেশে দেশে হৃদয়ে রচিত হয় অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন। তবে ধারণা করা হয়, প্রাচীন রোমে সর্বসাধারণের জন্য প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। তবে এর আগে অনুমান করা যায়, গ্রন্থাগার ছিল যা ব্যাবিলনের ভূগর্ভ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য এক ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে অর্থাৎ ১৯৫৪ ইংরেজির ৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। তাই দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ইতিহাস বলার কারণ স্পষ্ট হয় মানবসভ্যতার বিকাশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আগে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
লাইব্রেরি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের বলছিলাম লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার উপকারিতার কথা। আর বলছিলাম আমি বা আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন নিয়মিত লাইব্রেরিতে যেতাম। ওখানে গিয়ে ক্লাসে যেই বই ফলো করা হতো, তার বাইরে অন্য বইগুলো নিয়ে বসতাম পড়তাম এবং সেগুলো থেকে নোট তৈরি করতাম। ছাত্ররা তখন একযোগে বলে উঠল, স্যার, এখন তো লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই, বসার স্থান পাওয়া কঠিন, সেইখানে সবাই বিসিএস প্রস্তুতির জন্য সকালবেলায় লাইন দিয়ে সমস্ত জায়গা দখল করে ফেলে। নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর কোনো জায়গা থাকে না। আমি শুনে আশ্চর্য। একটা বিশ্ববিদ্যালয় কি এমন হতে পারে?’
ছাত্ররা লাইব্রেরিতে যাবে না, ক্লাসে শিক্ষক যে বই ফলো করেন, সেই বই দেখবে না, সেই বইয়ের বাইরে এসে বিষয়ের অন্য বই পড়বে না, বিভিন্ন দৈনিক ও ম্যাগাজিন জার্নাল পড়বে না। এ কি হতে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি মানের বিশাল একটি লাইব্রেরি আছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন দেখেছি সমসাময়িক জার্নাল ও বইয়ে যতটা না সমৃদ্ধ, তার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ পুরোনো জার্নাল ও বইয়ে। অন্যদিকে আমাদের দেশে অর্থাৎ এমনও আছে, যেখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এমনকি ২০-৩০টা গ্রামের মাঝে একটিও লাইব্রেরি নেই। তখন মনে হয়, বাংলাদেশ কী বিচিত্র দেশ। অতএব, দেশের যুব ও শিক্ষিত সমাজ এই দেশের শহর বন্দর তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পাঠাগার স্থাপনে সাম্প্রতিক সময়ে এগিয়ে আসবে।
জাতীয় জীবনকে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশের সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষালাভ সহজ হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরি, ফ্রান্সের বি ব্লিওথিক লাইব্রেরি, রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগ্রাদ শহরের লাইব্রেরি, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং ভারতের কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বিশ্বব্যাপীখ্যাত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরি এবং কিছুসংখ্যক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আছে।
তবে পৃথিবীর প্রথম বইমেলা কোথায় বসেছিল, খুঁজতে গেলে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের নাম আসে। দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময় হাতে লেখা বইয়ের পসরা বসেছিল ওই শহরের বাণিজ্য মেলায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী মাইনৎস শহরে এবং ইউহানেস গুটেনবার্গে ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। ছাপাখানার বই নিয়ে প্রথম বইমেলা বসে ফ্রাঙ্কফুর্টে ১৪৬২ সালে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের উৎসব হিসেবে পালিত বইমেলার গোড়াপত্তন ফ্রাঙ্কফুর্টের ওই বইমেলা থেকেই। তবে বাংলাদেশের বইমেলা অন্যান্য সব দেশের বইমেলা থেকে এক অন্য রকম বৈশিষ্ট্য ভাস্বর। বাংলাদেশের বইমেলা বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক। আর বাংলাদেশের জন্য আত্মাহুতি এই ভাষাতাত্ত্বিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উৎস। তা ছাড়া একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। হাজার বছরের বাঙালির সবচেয়ে বড় বিজয় সূচিত হলো। বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ তো আছেই। এই সমস্ত উদ্্যাপনের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা-সংবলিত উৎসব বইমেলা।
মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ঢাকার প্রকাশনাশিল্প পেয়েছে নতুন প্রাণ, নিজস্ব সত্তা। মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা সেই ১৯৭২ সালে বীজ বপন করলেন বইমেলার। বাংলা একাডেমির বটতলায় চটের ওপর মাত্র ৩২টি বই নিয়ে সাজানো সেই বইমেলার গল্প আমাদের জানা। এখন সেই বইমেলা বাংলা একাডেমি চত্বর ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দখল করে নিয়েছে। বইমেলাকে ঘিরে হাজার হাজার বই প্রকাশ হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার বেচাকেনা। মফস্বল শহরগুলোতেও বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। দেশের বাইরে লন্ডন, ফ্রান্স, নিউইয়র্কের মতো বড় বড় শহরে আয়োজন হচ্ছে বাঙালিদের বইমেলা। ধীরে ধীরে পুরান ঢাকার বাংলাবাজার ছাড়িয়ে বইমেলা ছড়িয়ে পড়েছে নতুন ঢাকায় নতুন আঙ্গিকে। তা ছাড়া পশ্চিম বাংলাতেও এখন বাংলা বইয়ের রমরমা অবস্থা।
শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একবার বলেছিলেন, ‘ঢাকা শহরে এখন প্রতিটি অলিগলিতে খাবারের দোকান বাড়ছে, প্রতি দোকানেই ভিড় করছে তরুণেরা অথচ সে তুলনায় লাইব্রেরির সংখ্যা তো বাড়েইনি বরং কমে গেছে।’
একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাবে লাইব্রেরির প্রতি মানুষের অনীহা কতটা। ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় ২৩টি পাঠাগার ছিল। বর্তমানে তা ৭টিতে নেমে এসেছে। অথচ ঢাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ!
দেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৪ থেকে ৩০ বছর, যাদেরকে আমরা কিশোর কিংবা তরুণ বলে থাকি। তরুণদের দেখা যায় গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়তে, তাদের দেখা যায় ইভটিজিং, ধর্ষণ, এমনকি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়াতে। এ জন্য কি শুধু তারাই দায়ী?
মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্পে আক্রান্ত গোটা সমাজ। মাদকের থাবায় আক্রান্ত হতাশাগ্রস্ত তরুণসমাজ ধীরে ধীরে পা বাড়ায় অপরাধের দিকে। খুন, টেন্ডারবাজি, রাজনৈতিক মাস্তানি, জমি দখল ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসীদের অনেকেই ভাড়ায় খাটে।
ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে একটি গোষ্ঠী তরুণদের ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও পদ্ধতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে যেমন গহনা হয় না, প্রয়োজন হয় খাদের; তেমনি পরিপূর্ণ মানুষ হতে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকাও আবশ্যক। আমাদের সমাজে বর্তমানে খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির রয়েছে অপর্যাপ্ততা। ফলে ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত চাপ, পুরোনো ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা ও মুখস্থবিদ্যার প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অল্প বয়সেই পড়াশোনার প্রতি একধরনের অনীহা সৃষ্টি হয়।
জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, ‘হে প্রভু, তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও, যাতে আমি আরও বেশি করে বই পড়তে পারি। এমন প্রার্থনা তার পক্ষে করা সম্ভব, যিনি আজীবন জ্ঞান সাধনা করেছেন এবং জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন। আমরা যারা সাধারণ তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কিছুই চাই কিন্তু বইপড়ার জন্য বেঁচে থাকার আকুতি জানাই না। এখানেই হলো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন জ্ঞানসাধকের পার্থক্য।’
প্রাচীন চীনা সভ্যতায় বেশ কিছু জ্ঞানসাধক ছিলেন, যারা জ্ঞানসাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যতিক্রম প্রক্রিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরূপ একজন জ্ঞানসাধকের কথা জানা যায়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। রাতের বেলায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেল কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। এ মানুষটি বেশ কিছু জোনাকি পোকাকে বোতলে ভরে সেগুলোর আলোতে রাতের বেলায় বই পড়তেন। আরেকজন জ্ঞানসাধকের কথা জানা যায়, যিনি তার মাথার চুল রশি দিয়ে ঘরের আড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন।
গভীর রাতে বই পড়তে পড়তে ঝিমুনি এলে রশিতে বাঁধা চুলগুলোতে টান পড়ত, ফলে তার ঝিমুনি কেটে যেত। বর্তমান বাংলাদেশেও দুর্বৃত্ত কালচারে এ ধরনের মানুষকে পাগল বলেই সাব্যস্ত করা হয়। সমাজে জ্ঞানের কদর নেই, কিন্তু বিত্তের কদর আছে। সে জন্যই মুষ্টিমেয় সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষ যারা এখনো বাংলাদেশের সমাজে টিকে আছেন। তাদের অনেক সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়। এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য বিত্তশালীরাই করে না, রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যারা আপনজন, তারাও ওই ব্যাপারে কম নন।
আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র পরিসর নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের বইমেলার। স্বাধীন বাংলাদেশের নবীনকালে এর সূচনা হলেও বর্তমানে বইমেলা একটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ ঘিরে ১৯৭৫-এ ফেব্রুয়ারি মাসে যে বইমেলা শুরু হয়েছিল অত্যন্ত দীনহীনভাবে, বর্তমানে সেই বইমেলা বাংলা একাডেমির চত্বর ও মাঠ ছাড়িয়ে বইয়ের সুবিশাল রাস্তার দু’ধারের দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ থেকে। কখনো যেন এর ঘাটতি না ঘটে।
বইমেলা বাংলা ভাষার জাগরণ আর বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আমাদের জাতিসত্তার একটি অনিবার্য মাইলফলক। বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকের মাঝে এক চমৎকার সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের নামকরা লেখকদের সঙ্গে সমানতালে অসংখ্য নবীন লেখক জেগে উঠেছে। লেখকদের অংশগ্রহণের ফলে বইমেলায় প্রচুর সমাগম ঘটে থাকে এবং বাংলা একাডেমির নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে মাসব্যাপী বইমেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।
তা ছাড়া প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে সরকারিভাবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই বইমেলার জন্ম হয়েছিল নব্বইয়ের গোড়ার দিকে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ছাড়াও বিশ্বের কয়েকটি দেশের প্রকাশনা স্থান পায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। বর্তমানে আরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে।
তবে ইদানীং সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। হেন অপরাধ নেই, যা আজ বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে না। এসব অপরাধ নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার সব সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য অনেক কারণই দায়ী। তবে গ্রন্থবিমুখতা কম দায়ী নয়। যদি দেশব্যাপী বইপড়ার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করা সম্ভব হতো, তাহলে হয়তো সামাজিক মালিন্য অনেকটা হ্রাস পেত।
মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। কোনো খারাপ আসক্তিকে দূর করতে হলে ভালো কোনো আসক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদিক থেকে পাঠের প্রতি আসক্তি খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু পাঠ করার কথা বলব কেন? দেশকে জানা, সমাজকে জানা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করাও বড় ধরনের কাজ। এর ফলে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। (ক্রমশ)
লেখক : লোকসংস্কৃতি গবেষক ও প্রাবন্ধিক। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট। পিএইচডি ফেলো, নিউইয়র্ক।
