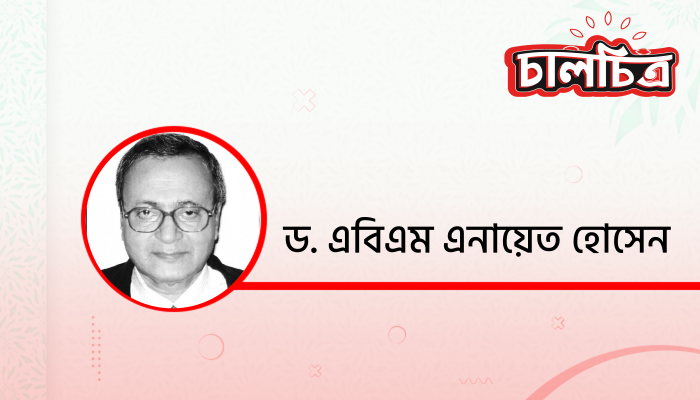
(গত সপ্তাহের পর)
বিলুপ্ত গ্রামীণ সংস্কৃতিরূপে ঢাল-সড়কি দিয়ে দুই পক্ষ বা দুই গ্রামবাসীর মধ্যে কোনো কারণে (বিরোধ) সামনাসামনি লড়াই বা যুদ্ধ হতো। শৈশবকালে একবার এরূপ গ্রাম্য লড়াই দেখার সুযোগ হয়েছিল, অবশ্য অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থেকে। ঢাল-সড়কি, রামদা, ভুজালি নিয়ে আমাদের গ্রামের জোয়ান ও শক্তিধর লোকেরা প্রতিপক্ষ গ্রাম, অর্থাৎ নলডাঙ্গা বিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ঘাঘা-যোগিয়ার লাঠিয়ালদের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায়। আমাদের গ্রামের পক্ষে পাশের পড়শি বাড়ির রূপই শেখের বড় ছেলে খোকা শেখ তার ঢালটা ঘর থেকে বের করে মাঠের দিকে রওনা হলো ত্বরিত পায়ে। খোকা শেখ তখন একজন তুখোড় নওজোয়ান। সুঠাম এবং দীর্ঘদেহী। উচ্চতায় ছয় ফুটেরও ঊর্ধ্বে। সময় তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধংদেহী ও মুখোমুখি, তখন দুই পক্ষের কয়েকজন গ্রাম্য মাতবর খুনোখুনিটা বন্ধ করতে সক্ষম হলেন। কথা হলো, যথাসময়ে গ্রাম্য সালিস ডেকে উভয় পক্ষের শুনানি ও দলিল-দস্তাবেজ দেখে এ সমস্যার সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
লড়াই থামার পর খোকা শেখ তার ঢাল-সড়কিটা এনে তাদের উঠানে রাখল। উঠানে তখন অনেক লোকসমাগম। নানাজনের নানা রকম প্রশ্ন! আমি জীবনে এই প্রথম ঢাল-সড়কি কী জিনিস তা চাক্ষুষ করলাম। ঢাল নির্মাণের সূক্ষ্ম কারুশিল্প, বাঁশের চিকন সরু শলাকা, সুতা ও বেতের বয়ন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! কিন্তু ঢাল-নির্মাতারা তত দিনে চাহিদা না থাকায় বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছে হয়তো।
এ তো গেল ঢাল-সড়কির লড়াইয়ের কথা। শৈশব ও কৈশোরে খেলার সাথিদের মধ্যে কখনো কখনো শক্তিমত্তার লড়াই বা কুস্তি হতে দেখতাম। কে কাকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে যে কাত করে মাটির ওপর ফেলে দিতে পারে এবং পরে চিত করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে রাখতে পারে। যে উপরে থাকবে, সে-ই জিতে যায় স্বরূপে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধে।
সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা ছিল এঁড়ে গরু ও ষাঁড়ের যুদ্ধ। শীতকালে যখন মাঠের রবি শস্য আহরণ শেষ, তখন খোলা ময়দানে গ্রামবাসী যার যার গৃহপালিত এঁড়ে গরু ও ষাঁড় গরুকে প্রথমে গোসল করিয়ে, পরে সাজিয়ে-গুজিয়ে, গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে, অনেকে কপালে আলতা-সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং দুটি শিংকে কাচের ভাঙা টুকরো বা ধারালো চাকু দিয়ে চেঁছে পালিশ ও চোখা করে। এরূপ ধারালো শিংওয়ালা এঁড়ে গরু/ষাঁড় নিয়ে নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলতে তুলতে মাঠের দিকে নিয়ে চলে। লড়াইয়ের আগে কেউ কেউ আবার নিজের পোষা লড়াকু গরুটিকে ভুসি, খৈল ও ফেন খাইয়ে গায়ে অতিরিক্ত শক্তি জোগান দেয়।
রবি ফসলের খালি মাঠে গ্রামের অসংখ্য দর্শক গোল হয়ে সবাই লড়াকু গরুগুলোকে দেখতে থাকে। অনেকের সঙ্গে আবার কৌতূহলী কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত হয়। কিন্তু সমস্যা ও আশঙ্কা হলো রণে পরাজিত গরুটি পালিয়ে যাওয়ার সময়ে দিগ্্বিদিক বিচার না করেই এলোপাতাড়িভাবে দৌড় দেয়! আর বিজয়ী গরুটি উল্লসিত হয়ে বিজিত গরুটিকে ধাওয়া করে। এ সময় দর্শকদের মধ্যে লেগে যায় হুড়োহুড়ি-দৌড়াদৌড়ি! কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে জমিনের ওপর পড়ে যায়। যদি দুর্ভাগ্যবশত কেউ পলায়নরত লড়াকু গরুর পায়ের নিচে পড়ে যায়, তাহলে কী ঘটতে পারে, তা একটু ভেবে দেখুন না! সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাটিতে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা লুকানো আছে বলে মনে হয়।
নাটক-বাটিকা বা যাত্রাভিনয়ে তখনো পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে অংশগ্রহণ প্রচলিত হয়নি। যদিও ব্যতিক্রমী ঘটনা যে দু-একটি নাটকে ঘটেনি, তা নয়! তছলিম উদ্দিন পরিচালিত একটি নাটকে সর্বপ্রথম বন্দনা সরকার নামের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করার অনুমতি আদায় করা হলো তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। এটি ছিল ১৯৫৮ সালের কথা। তখন এ খবর সবার মুখে মুখে। যাহোক, নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল আমাদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। দর্শক-শ্রোতা প্রশংসিত এ নাটকের পরই বন্দনা ও তার পরিবার (অক্ষয় কুমার সরকার ও তার স্ত্রীসহ অন্যান্য সন্তান-সন্ততি) ওপার বাংলায় পাড়ি জমায়।
সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একবার ইতনা স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, স্কুলের চৌহদ্দিতে একটা ভালো যাত্রাদল ভাড়া করে এনে পরপর তিন দিন-তিন রাত অবধি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নড়াইলের দিক থেকে একটা নামকরা যাত্রাদলকে ভাড়া করা হলো। প্রথম রাতে অনুষ্ঠিত হলো ‘সীতার বনবাস’। যথারীতি মুখ্য চরিত্রে অভিনয়কারী সীতা সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। এ সময় আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। পূজা উপলক্ষে গেট সাজানো থেকে যাত্রার দর্শক-শ্রোতাদের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আমরা কতিপয় সিনিয়র ছাত্র। যাত্রাপালার দ্বিতীয় দিন আমার কাছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র পূর্বপাড়ার ইলু শেখ ও তার চাচাতো ভাই শেখ জহির এক আজব প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত!
‘আমরা যাত্রাদলের সীতার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই। ভাই এনায়েত! যে করেই হোক, আমাগোর জন্যি এটু দেহা করার ব্যবস্থা করতি হবে।’
‘কিন্তু তোমরা দেখা করবার জন্য এতডা পাগল ইইছো ক্যান, কও দেহি!’
‘ সীতারে দেহে আমার চাচাতো ভাই জহিরের মাথাডা ঘুরে গেছে! সে ওরে বান্ধবী বানাইতে চায়।’ ইলু কিছুটা ইতস্তত করে জবাব দিল।
‘তোমরা সত্যি সত্যিই পাগল হইছো! সীতা তো মাইয়ে না, ব্যাটা ছাওয়াল। তাও যদি তোমরা বিশ্বাস না করতে চাও, তাইলে তাও বাজি ধরো আমার সাথে।’
ওরা দুজন বাজি ধরতে রাজি হয়ে গেল। হারু পার্টি শান্তি ময়রার সন্দেশ কিনে খাওয়াবে সবাইকে। এসব কথাবার্তা যখন চলছিল, তখন সকাল ১১-১২টা। যাত্রাদলের সবাই সবেমাত্র ঘুম ভেঙে সকালের কাজকাম শেষ করে নাশতা-পানি সারতে ব্যস্ত। আমি ওদের দুজনকে যাত্রাদলের সাজঘরের মুখে দাঁড়াতে বলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম, অধিকারী বাবু আধশোয়া অবস্থায় একটা পাশ বালিশে হেলান দিয়ে পান চিবোচ্ছে। আমি ভেতরে ঢুকবার অনুমতি নিয়ে অধিকারীকে আদাব দিয়ে বললাম :
‘দাদা, আদাব! আমার নাম নাম এনায়েত। সরস্বতী পূজা এবং যাত্রা-আয়োজক কমিটির একজন সদস্য। এ স্কুলের আমি দশম শ্রেণির ফার্স্ট বয়। আপনার কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছি!’
‘বিষয়টা কী তা একটু খুলে বলুন তো, বাবু!’
‘যদি কিছু মনে না করেন, দাদা! আপনার দলের সীতা চরিত্রে অভিনয়কারীর সাথে দুই মিনিট আলাপ করতে চাই আমরা তিন বন্ধু মিলে। ওকে একটু সাজঘরের বাইরে আসতে বলবেন?’
‘ও, এই ব্যাপার! তা আপনার আর দুজন বন্ধু কোথায়?’
‘ওরা সাজঘরের বাইরেই অপেক্ষা করছে।’
আমার এ কথা শুনে অধিকারী বাবু উচ্চস্বরে একটা হাঁক দিলেন :
‘বলাই, ও বলাই। এদিকে একটু আয় তো দেহি। এই খোকা বাবুর সাথে তাঁবুর বাইরে গিয়ে কিছু আলাপ কর।’
ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা রঙের এক যুবক প্রবেশপথের কাছে এগিয়ে এল। সঙ্গে তার আরেকজন সহচর। দেখে আমার চিনতে একটুও কষ্ট হলো না! এই যুবকই যাত্রাপালায় বিবেকের ভূমিকায় অংশ নেয়। ওদের দুজনকে আমার সাথে বাইরে দেখতে পেয়ে ইলু ও জহিরও এগিয়ে আসে পরিচিত হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর মোদ্দাকথা দাঁড়াল, যাত্রাদলে সত্যিই কোনো মেয়ে অভিনেত্রী নেই এবং সীতা চরিত্রে অভিনয়কারী শিল্পী স্বয়ং ‘বলাই’ আমাদের সামনে উপস্থিত! এভাবেই বাজি ধরার বিষয়টার ফয়সালা হলো।
গ্রামীণ আড়ং, বারুনি ও মেলা ছিল সে সময়কার গ্রাম্য পসরার ব্যাপক বিকিকিনির সুযোগ। সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এ যেন আনন্দ-মিলনমেলা। নানাবিধ ঘরগৃহস্থালির সামগ্রী, যথা ডালা, খালই, চালুনি, পাটা-পুতা (শীল-নোড়া), দড়ি, কাঁচি, কোদাল, চাকু, হাতপাখা, মাদুর-দড়মা, ধামা, পেকা, টোকা ইত্যাদিসহ রান্নাঘরের তৈজসপত্র (অ্যালুমিনিয়ম, পিতল কিংবা গোড়া মাটির তৈরি), ফুলঝাড়ু, ঘটি-বাটি, কলসি-হাঁড়ি আরও কত কী!
খাবারদাবারের মধ্যে মুড়ি-মুড়কি, চিড়া-গুড়, কটকটি, কদমা, বাতাসা, জিলাপি, গজা, তুলোর মিষ্টি, দানাদার প্রভৃতি স্তূপাকারে সাজিয়ে বিক্রেতারা ঠোঙা/পাতায় পেঁচিয়ে বিপণনে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রঙিন প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের খেলনা-বাটির সেট, পুতুল, বাঁশের বাঁশি কিংবা হুইসেল দেওয়ার বাঁশি, বেলুন, আলতা-সিঁদুর আর কমদামি লিপস্টিক কেনার জন্য মেয়েদেরকে বাবা-ভাইয়ের কাছে আবদার করাটা পরিচিত দৃশ্য। কখনো কখনো সাধ ও সাধ্যের মধ্যে না কুলাতে পারার কারণে অবুঝ ছেলেমেয়েদের অঝোর ধারায় কান্না করার দৃশ্য লক্ষণীয়। বিনোদনের জন্য চরকিতে চড়া ড্রিল কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ শিহরণ। আর এসব গ্রামীণ মেলা বসত বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণে। উদাহরণস্বরূপ চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও কার্তিক পূজার কথা উল্লেখ করা যায়।
মুসলমান সম্প্রদায়ে সাধারণত বছরে দুটি ঈদ আনন্দোৎসব ছাড়া কোনো কোনো সচ্ছল পরিবারে মুসলমানি (খতনা) দেওয়া উপলক্ষে ক্ষীর ও চালের আটার রুটি বিলানো এবং বিশেষ করে শবে বরাত উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি রুটি (চালের আটার) ও ক্ষীর বণ্টন করা ছিল একধরনের প্রথা বা ঐতিহ্য। তবে শেষোক্ত প্রচলনটির ক্রমবিলুপ্তি বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর মূল কারণ অবশ্য উপরিউক্ত ঐতিহ্যের ধর্মভিত্তিক কোনো দলিল না পাওয়া।
হালখাতা ও নবান্ন সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়! বাঙালি ব্যবসায়ী, দোকানি ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের বহু প্রাচীন এক প্রথার নাম হালখাতা। এ উৎসবটি বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন, অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ এ নতুন হিসাবের খাতা খুলে পালিত হয় দিনটি। প্রথাটি মূলত মুঘল সম্রাট ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে প্রথম বাঙালি সৌর মহরত অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। হালখাতা উৎসব বাঙালি জাতির প্রায় ৪৩০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য।
বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা তাদের পুরাতন জমাখরচের হিসাব-সংক্রান্ত খাতার বদলে নতুন বছরের জন্য নতুন খতিয়ান বই খোলেন। ক্রেতাদেরকে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয় পুরোনো পাওনা-দেনা পরিশোধ করার জন্য। হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা সাধারণত এ দিনের সূচনা করেন বিশেষ পূজা (লক্ষ্মীপূজা) দিয়ে এবং প্রসাদ (রসগোল্লা) বিতরণের মাধ্যমে। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে মিষ্টির সাথে লুচি-পরোটা এমনকি নানাবিধ উপহারও দেওয়া হয়ে থাকে।
বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা ও আসাম রাজ্যে নবান্ন নামে নানা প্রকার খাদ্য (খাবারদাবার) পরিবেশন এবং নাচ- গানের অপর একটি উৎসব পালিত হয়। খাদ্যোৎসবের উপকরণ হলো পায়েস, গ্রাম্য নানাবিধ পিঠা, যেমন চালি, পাকান (পাকওয়ান), আন্দাশা (ভাজা পিঠা), রস চিতই, ভাপা, হাতে-কাটা সেমাই, পাটিসাপটা, মালপোয়া ইত্যাদি। নবান্ন উৎসব পালিত হতো সাধারণত মেলা উদ্্যাপনের মাধ্যমে। সব ধর্মাবলম্বী লোকেরাই এ উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও বৈচিত্র্য বিনির্মাণে নবান্ন উৎসবের বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। বর্তমানে নবান্ন উৎসব পালিত হয় প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসে। অসংখ্য সংস্কৃতিমনা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, সংগঠন ও শিল্পীবৃন্দ এ উৎসবে সানন্দে অংশগ্রহণ করে।
গ্রামীণ খেলাধুলার জগৎটা ছিল সবচাইতে বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছেলেবেলা থেকে কৈশোর অবধি আমাদের দুর্বার আকর্ষণ ছিল বাড়ির বহিঃমহল। জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক ও প্রযোজক ‘মাটি ও মানুষ’ শীর্ষক সিরিজ প্রোগ্রামের স্রষ্টা শাইখ সিরাজ গ্রামীণ খেলাধুলা ও ঐতিহ্যের একজন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক। তবে গ্রামীণ খেলাধুলা জগতের সার্বিক বৈচিত্র্য, বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্নতার অফুরন্ত ভান্ডার এখনো ইলেকট্রনিক পর্দায় প্রতিফলিত ও প্রচারিত হয়নি। যা হয়েছে, সে কেবল দু-চারটে গ্রামের প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত খেলাধুলার প্রতিযোগিতার খণ্ডচিত্র মাত্র।
শৈশবে গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা পাতা, ডালপালা ও বুনো গাছপালার মঞ্জরী (এবং ফুল) কিংবা ফল দিয়ে রান্নাবাটি খেলা খেলতে ছিল আগ্রহী। এতে মেয়ে-বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গিয়ে রান্নাবান্নার নতুন করে কিংবা জোর করে রান্নার কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হতো না। এ ছাড়া মেয়েদের সবারই পছদের খেলনা মাটির পুতুল। হোক না মাটির তৈরি কিংবা প্লাস্টিক বা কাঠনির্মিত। একজনের কনে-পুতুলের সাথে অন্য একজন খেলার সাথির বর-পুতুলের বিয়ে দেওয়া! এ সবই ছিল ঐতিহ্যের পরম্পরা।
একটু বড় হয়ে লুকোচুরি, গোল্লাছুট, এক্কা-দোক্কা, কিং স্কিপিং (রশি লাফানি)। ছেলেরা একটু বড় হয়েই ডাংগুলি, মারবেল খেলা, হাডুডু কিংবা মধ্যবিত্ত/উচ্চমধ্যবিত্তদের পরিবারে অভ্যন্তরীণ খেলা হিসেবে ক্যারম, লুডো (সাপ কিংবা কোট), ব্যাগাডুলি বা দাবা খেলা চলত। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রচলিত আধুনিক খেলা, যেমন লং জাম্প, হাই জাম্প (উচ্চ লম্ফ), পোল ভল্ট (বাঁশ দিয়ে উচ্চ লম্ফ), জেভলিন ছোড়া, গোলক নিক্ষেপ ছাড়াও বস্তা দৌড়, বিস্কুট খাওয়ার দৌড়, সুই-সুতা ভরা, চামচের ওপর কাগজি লেবু রেখে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দ্রুত হাঁটার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছিল মজার খেলা।
তা ছাড়া গ্রামের অবারিত মাঠে ও প্রান্তরে ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা ছিল সত্যিকার অর্থে দর্শনীয়। এ কারণে অনেকেই নানা আকার ও আকৃতির সুদৃশ্য ঘুড়ি কিনে আনত গ্রাম্য মেলা ও আড়ং থেকে। তারপর লাটাইয়ের সুতায় মাজন দেওয়ার পালা। অনেকে আবার সুতায় কাচের গুঁড়া লাগাত আঠা দিয়ে, যাতে অন্যের ঘুড়িকে সহজেই কাটা যায়! কিন্তু গ্রামীণ ঘুড়ি ওড়ানো খেলা ও প্রতিযোগিতা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে এখন বলতে গেলে ভাটি অঞ্চলে হয়ে গেছে প্রায় অদৃশ্য! এর মুখ্য কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে বায়ুপ্রবাহের ঘাটতি, যা মূলত মৌসুমি জলবায়ুর তীব্রতা ও কার্যকারিতা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট।
গ্রামীণ খেলাধুলার অধিকাংশই আজকাল লুপ্ত কিংবা কিংবা বিলুপ্তির পথে। হাডুডুর পরিবর্তে আমাদের জাতীয় খেলা এখন কাবাড়ি। কিন্তু আমার শৈশব ও কৈশোর বয়সে আমি কোনো দিন দেখিনি কাবাডি খেলতে গ্রামে!
গ্রামেগঞ্জে এখন ক্রিকেট খেলাই তুঙ্গে অবস্থান করছে। খেলার সরঞ্জাম থাক বা না থাক, কিছুই যায় আসে না। এক টুকরো লম্বা তক্তার একদিকে কিছুটা সরু করে হাতলের মতো বানিয়ে ক্রিকেট ব্যাট আর একটি টেনিস বল জোগাড় করেই ক্রিকেট খেলার মহড়া চলতে থাকে!
একসময় ফুটবল খেলা জনপ্রিয় থাকলেও ক্রমশ এটি লোকপ্রিয়তা হারাচ্ছে। গ্রামের ছেলেদের ফুটবল কেনার মতো সামর্থ্য না থাকায় অনেকে বাতাবি লেবু গাছ থেকে চুরি করে বাতাবি লেবু পেড়ে ফুটবল হিসেবে খেলত। মাঝেমধ্যে আশপাশের গ্রামের ফুটবল দলের সাথে মোকাবিলাও অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু আজ ফুটবল কেনার মতো সক্ষমতা গ্রামীণ যুবসমাজের বর্তমান।
সেই মাঠও বর্তমান, যা তঝলু’র মাঠ নামে পরিচিত ছিল। তবে এখন এ মাঠে আর কেউই ফুটবল খেলে না! আশপাশের গৃহস্থ বাড়ির গরু-বাছুরগুলোকে মুক্ত অবস্থায়, আবার কখনো-বা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘাস কিংবা শুকনো খড় খেতে দেয়!
ডিজিটাল বিশ্বে এখন প্রায় সর্বত্রই এর আসর দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও এখন স্মার্টফোন, আইফোন ব্যবহার করে। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে সারা বিশ্ব প্রত্যেকের মুঠোবদ্ধ। প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ায় ব্যাপক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শিশুরাও যেন মায়ের পেটে থাকতেই মোবাইল ফোনের আইকনগুলো টেপাটেপি করে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে! এ অবস্থায় গ্রামীণ ঐতিহ্য, পরম্পরা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে ও বা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে শুধু ইতিহাস হয়ে রইবে, তা একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই বলে দেবে! (সমাপ্ত)
বিলুপ্ত গ্রামীণ সংস্কৃতিরূপে ঢাল-সড়কি দিয়ে দুই পক্ষ বা দুই গ্রামবাসীর মধ্যে কোনো কারণে (বিরোধ) সামনাসামনি লড়াই বা যুদ্ধ হতো। শৈশবকালে একবার এরূপ গ্রাম্য লড়াই দেখার সুযোগ হয়েছিল, অবশ্য অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থেকে। ঢাল-সড়কি, রামদা, ভুজালি নিয়ে আমাদের গ্রামের জোয়ান ও শক্তিধর লোকেরা প্রতিপক্ষ গ্রাম, অর্থাৎ নলডাঙ্গা বিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ঘাঘা-যোগিয়ার লাঠিয়ালদের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায়। আমাদের গ্রামের পক্ষে পাশের পড়শি বাড়ির রূপই শেখের বড় ছেলে খোকা শেখ তার ঢালটা ঘর থেকে বের করে মাঠের দিকে রওনা হলো ত্বরিত পায়ে। খোকা শেখ তখন একজন তুখোড় নওজোয়ান। সুঠাম এবং দীর্ঘদেহী। উচ্চতায় ছয় ফুটেরও ঊর্ধ্বে। সময় তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধংদেহী ও মুখোমুখি, তখন দুই পক্ষের কয়েকজন গ্রাম্য মাতবর খুনোখুনিটা বন্ধ করতে সক্ষম হলেন। কথা হলো, যথাসময়ে গ্রাম্য সালিস ডেকে উভয় পক্ষের শুনানি ও দলিল-দস্তাবেজ দেখে এ সমস্যার সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
লড়াই থামার পর খোকা শেখ তার ঢাল-সড়কিটা এনে তাদের উঠানে রাখল। উঠানে তখন অনেক লোকসমাগম। নানাজনের নানা রকম প্রশ্ন! আমি জীবনে এই প্রথম ঢাল-সড়কি কী জিনিস তা চাক্ষুষ করলাম। ঢাল নির্মাণের সূক্ষ্ম কারুশিল্প, বাঁশের চিকন সরু শলাকা, সুতা ও বেতের বয়ন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! কিন্তু ঢাল-নির্মাতারা তত দিনে চাহিদা না থাকায় বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছে হয়তো।
এ তো গেল ঢাল-সড়কির লড়াইয়ের কথা। শৈশব ও কৈশোরে খেলার সাথিদের মধ্যে কখনো কখনো শক্তিমত্তার লড়াই বা কুস্তি হতে দেখতাম। কে কাকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে যে কাত করে মাটির ওপর ফেলে দিতে পারে এবং পরে চিত করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে রাখতে পারে। যে উপরে থাকবে, সে-ই জিতে যায় স্বরূপে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধে।
সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা ছিল এঁড়ে গরু ও ষাঁড়ের যুদ্ধ। শীতকালে যখন মাঠের রবি শস্য আহরণ শেষ, তখন খোলা ময়দানে গ্রামবাসী যার যার গৃহপালিত এঁড়ে গরু ও ষাঁড় গরুকে প্রথমে গোসল করিয়ে, পরে সাজিয়ে-গুজিয়ে, গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে, অনেকে কপালে আলতা-সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং দুটি শিংকে কাচের ভাঙা টুকরো বা ধারালো চাকু দিয়ে চেঁছে পালিশ ও চোখা করে। এরূপ ধারালো শিংওয়ালা এঁড়ে গরু/ষাঁড় নিয়ে নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলতে তুলতে মাঠের দিকে নিয়ে চলে। লড়াইয়ের আগে কেউ কেউ আবার নিজের পোষা লড়াকু গরুটিকে ভুসি, খৈল ও ফেন খাইয়ে গায়ে অতিরিক্ত শক্তি জোগান দেয়।
রবি ফসলের খালি মাঠে গ্রামের অসংখ্য দর্শক গোল হয়ে সবাই লড়াকু গরুগুলোকে দেখতে থাকে। অনেকের সঙ্গে আবার কৌতূহলী কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত হয়। কিন্তু সমস্যা ও আশঙ্কা হলো রণে পরাজিত গরুটি পালিয়ে যাওয়ার সময়ে দিগ্্বিদিক বিচার না করেই এলোপাতাড়িভাবে দৌড় দেয়! আর বিজয়ী গরুটি উল্লসিত হয়ে বিজিত গরুটিকে ধাওয়া করে। এ সময় দর্শকদের মধ্যে লেগে যায় হুড়োহুড়ি-দৌড়াদৌড়ি! কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে জমিনের ওপর পড়ে যায়। যদি দুর্ভাগ্যবশত কেউ পলায়নরত লড়াকু গরুর পায়ের নিচে পড়ে যায়, তাহলে কী ঘটতে পারে, তা একটু ভেবে দেখুন না! সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাটিতে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা লুকানো আছে বলে মনে হয়।
নাটক-বাটিকা বা যাত্রাভিনয়ে তখনো পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে অংশগ্রহণ প্রচলিত হয়নি। যদিও ব্যতিক্রমী ঘটনা যে দু-একটি নাটকে ঘটেনি, তা নয়! তছলিম উদ্দিন পরিচালিত একটি নাটকে সর্বপ্রথম বন্দনা সরকার নামের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করার অনুমতি আদায় করা হলো তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। এটি ছিল ১৯৫৮ সালের কথা। তখন এ খবর সবার মুখে মুখে। যাহোক, নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল আমাদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। দর্শক-শ্রোতা প্রশংসিত এ নাটকের পরই বন্দনা ও তার পরিবার (অক্ষয় কুমার সরকার ও তার স্ত্রীসহ অন্যান্য সন্তান-সন্ততি) ওপার বাংলায় পাড়ি জমায়।
সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একবার ইতনা স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, স্কুলের চৌহদ্দিতে একটা ভালো যাত্রাদল ভাড়া করে এনে পরপর তিন দিন-তিন রাত অবধি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নড়াইলের দিক থেকে একটা নামকরা যাত্রাদলকে ভাড়া করা হলো। প্রথম রাতে অনুষ্ঠিত হলো ‘সীতার বনবাস’। যথারীতি মুখ্য চরিত্রে অভিনয়কারী সীতা সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। এ সময় আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। পূজা উপলক্ষে গেট সাজানো থেকে যাত্রার দর্শক-শ্রোতাদের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আমরা কতিপয় সিনিয়র ছাত্র। যাত্রাপালার দ্বিতীয় দিন আমার কাছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র পূর্বপাড়ার ইলু শেখ ও তার চাচাতো ভাই শেখ জহির এক আজব প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত!
‘আমরা যাত্রাদলের সীতার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই। ভাই এনায়েত! যে করেই হোক, আমাগোর জন্যি এটু দেহা করার ব্যবস্থা করতি হবে।’
‘কিন্তু তোমরা দেখা করবার জন্য এতডা পাগল ইইছো ক্যান, কও দেহি!’
‘ সীতারে দেহে আমার চাচাতো ভাই জহিরের মাথাডা ঘুরে গেছে! সে ওরে বান্ধবী বানাইতে চায়।’ ইলু কিছুটা ইতস্তত করে জবাব দিল।
‘তোমরা সত্যি সত্যিই পাগল হইছো! সীতা তো মাইয়ে না, ব্যাটা ছাওয়াল। তাও যদি তোমরা বিশ্বাস না করতে চাও, তাইলে তাও বাজি ধরো আমার সাথে।’
ওরা দুজন বাজি ধরতে রাজি হয়ে গেল। হারু পার্টি শান্তি ময়রার সন্দেশ কিনে খাওয়াবে সবাইকে। এসব কথাবার্তা যখন চলছিল, তখন সকাল ১১-১২টা। যাত্রাদলের সবাই সবেমাত্র ঘুম ভেঙে সকালের কাজকাম শেষ করে নাশতা-পানি সারতে ব্যস্ত। আমি ওদের দুজনকে যাত্রাদলের সাজঘরের মুখে দাঁড়াতে বলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম, অধিকারী বাবু আধশোয়া অবস্থায় একটা পাশ বালিশে হেলান দিয়ে পান চিবোচ্ছে। আমি ভেতরে ঢুকবার অনুমতি নিয়ে অধিকারীকে আদাব দিয়ে বললাম :
‘দাদা, আদাব! আমার নাম নাম এনায়েত। সরস্বতী পূজা এবং যাত্রা-আয়োজক কমিটির একজন সদস্য। এ স্কুলের আমি দশম শ্রেণির ফার্স্ট বয়। আপনার কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছি!’
‘বিষয়টা কী তা একটু খুলে বলুন তো, বাবু!’
‘যদি কিছু মনে না করেন, দাদা! আপনার দলের সীতা চরিত্রে অভিনয়কারীর সাথে দুই মিনিট আলাপ করতে চাই আমরা তিন বন্ধু মিলে। ওকে একটু সাজঘরের বাইরে আসতে বলবেন?’
‘ও, এই ব্যাপার! তা আপনার আর দুজন বন্ধু কোথায়?’
‘ওরা সাজঘরের বাইরেই অপেক্ষা করছে।’
আমার এ কথা শুনে অধিকারী বাবু উচ্চস্বরে একটা হাঁক দিলেন :
‘বলাই, ও বলাই। এদিকে একটু আয় তো দেহি। এই খোকা বাবুর সাথে তাঁবুর বাইরে গিয়ে কিছু আলাপ কর।’
ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা রঙের এক যুবক প্রবেশপথের কাছে এগিয়ে এল। সঙ্গে তার আরেকজন সহচর। দেখে আমার চিনতে একটুও কষ্ট হলো না! এই যুবকই যাত্রাপালায় বিবেকের ভূমিকায় অংশ নেয়। ওদের দুজনকে আমার সাথে বাইরে দেখতে পেয়ে ইলু ও জহিরও এগিয়ে আসে পরিচিত হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর মোদ্দাকথা দাঁড়াল, যাত্রাদলে সত্যিই কোনো মেয়ে অভিনেত্রী নেই এবং সীতা চরিত্রে অভিনয়কারী শিল্পী স্বয়ং ‘বলাই’ আমাদের সামনে উপস্থিত! এভাবেই বাজি ধরার বিষয়টার ফয়সালা হলো।
গ্রামীণ আড়ং, বারুনি ও মেলা ছিল সে সময়কার গ্রাম্য পসরার ব্যাপক বিকিকিনির সুযোগ। সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এ যেন আনন্দ-মিলনমেলা। নানাবিধ ঘরগৃহস্থালির সামগ্রী, যথা ডালা, খালই, চালুনি, পাটা-পুতা (শীল-নোড়া), দড়ি, কাঁচি, কোদাল, চাকু, হাতপাখা, মাদুর-দড়মা, ধামা, পেকা, টোকা ইত্যাদিসহ রান্নাঘরের তৈজসপত্র (অ্যালুমিনিয়ম, পিতল কিংবা গোড়া মাটির তৈরি), ফুলঝাড়ু, ঘটি-বাটি, কলসি-হাঁড়ি আরও কত কী!
খাবারদাবারের মধ্যে মুড়ি-মুড়কি, চিড়া-গুড়, কটকটি, কদমা, বাতাসা, জিলাপি, গজা, তুলোর মিষ্টি, দানাদার প্রভৃতি স্তূপাকারে সাজিয়ে বিক্রেতারা ঠোঙা/পাতায় পেঁচিয়ে বিপণনে ব্যস্ত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রঙিন প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের খেলনা-বাটির সেট, পুতুল, বাঁশের বাঁশি কিংবা হুইসেল দেওয়ার বাঁশি, বেলুন, আলতা-সিঁদুর আর কমদামি লিপস্টিক কেনার জন্য মেয়েদেরকে বাবা-ভাইয়ের কাছে আবদার করাটা পরিচিত দৃশ্য। কখনো কখনো সাধ ও সাধ্যের মধ্যে না কুলাতে পারার কারণে অবুঝ ছেলেমেয়েদের অঝোর ধারায় কান্না করার দৃশ্য লক্ষণীয়। বিনোদনের জন্য চরকিতে চড়া ড্রিল কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ শিহরণ। আর এসব গ্রামীণ মেলা বসত বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণে। উদাহরণস্বরূপ চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও কার্তিক পূজার কথা উল্লেখ করা যায়।
মুসলমান সম্প্রদায়ে সাধারণত বছরে দুটি ঈদ আনন্দোৎসব ছাড়া কোনো কোনো সচ্ছল পরিবারে মুসলমানি (খতনা) দেওয়া উপলক্ষে ক্ষীর ও চালের আটার রুটি বিলানো এবং বিশেষ করে শবে বরাত উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি রুটি (চালের আটার) ও ক্ষীর বণ্টন করা ছিল একধরনের প্রথা বা ঐতিহ্য। তবে শেষোক্ত প্রচলনটির ক্রমবিলুপ্তি বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর মূল কারণ অবশ্য উপরিউক্ত ঐতিহ্যের ধর্মভিত্তিক কোনো দলিল না পাওয়া।
হালখাতা ও নবান্ন সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়! বাঙালি ব্যবসায়ী, দোকানি ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের বহু প্রাচীন এক প্রথার নাম হালখাতা। এ উৎসবটি বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন, অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ এ নতুন হিসাবের খাতা খুলে পালিত হয় দিনটি। প্রথাটি মূলত মুঘল সম্রাট ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে প্রথম বাঙালি সৌর মহরত অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। হালখাতা উৎসব বাঙালি জাতির প্রায় ৪৩০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য।
বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা তাদের পুরাতন জমাখরচের হিসাব-সংক্রান্ত খাতার বদলে নতুন বছরের জন্য নতুন খতিয়ান বই খোলেন। ক্রেতাদেরকে আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয় পুরোনো পাওনা-দেনা পরিশোধ করার জন্য। হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা সাধারণত এ দিনের সূচনা করেন বিশেষ পূজা (লক্ষ্মীপূজা) দিয়ে এবং প্রসাদ (রসগোল্লা) বিতরণের মাধ্যমে। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে মিষ্টির সাথে লুচি-পরোটা এমনকি নানাবিধ উপহারও দেওয়া হয়ে থাকে।
বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা ও আসাম রাজ্যে নবান্ন নামে নানা প্রকার খাদ্য (খাবারদাবার) পরিবেশন এবং নাচ- গানের অপর একটি উৎসব পালিত হয়। খাদ্যোৎসবের উপকরণ হলো পায়েস, গ্রাম্য নানাবিধ পিঠা, যেমন চালি, পাকান (পাকওয়ান), আন্দাশা (ভাজা পিঠা), রস চিতই, ভাপা, হাতে-কাটা সেমাই, পাটিসাপটা, মালপোয়া ইত্যাদি। নবান্ন উৎসব পালিত হতো সাধারণত মেলা উদ্্যাপনের মাধ্যমে। সব ধর্মাবলম্বী লোকেরাই এ উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও বৈচিত্র্য বিনির্মাণে নবান্ন উৎসবের বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। বর্তমানে নবান্ন উৎসব পালিত হয় প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসে। অসংখ্য সংস্কৃতিমনা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, সংগঠন ও শিল্পীবৃন্দ এ উৎসবে সানন্দে অংশগ্রহণ করে।
গ্রামীণ খেলাধুলার জগৎটা ছিল সবচাইতে বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছেলেবেলা থেকে কৈশোর অবধি আমাদের দুর্বার আকর্ষণ ছিল বাড়ির বহিঃমহল। জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক ও প্রযোজক ‘মাটি ও মানুষ’ শীর্ষক সিরিজ প্রোগ্রামের স্রষ্টা শাইখ সিরাজ গ্রামীণ খেলাধুলা ও ঐতিহ্যের একজন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক। তবে গ্রামীণ খেলাধুলা জগতের সার্বিক বৈচিত্র্য, বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্নতার অফুরন্ত ভান্ডার এখনো ইলেকট্রনিক পর্দায় প্রতিফলিত ও প্রচারিত হয়নি। যা হয়েছে, সে কেবল দু-চারটে গ্রামের প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত খেলাধুলার প্রতিযোগিতার খণ্ডচিত্র মাত্র।
শৈশবে গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা পাতা, ডালপালা ও বুনো গাছপালার মঞ্জরী (এবং ফুল) কিংবা ফল দিয়ে রান্নাবাটি খেলা খেলতে ছিল আগ্রহী। এতে মেয়ে-বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গিয়ে রান্নাবান্নার নতুন করে কিংবা জোর করে রান্নার কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হতো না। এ ছাড়া মেয়েদের সবারই পছদের খেলনা মাটির পুতুল। হোক না মাটির তৈরি কিংবা প্লাস্টিক বা কাঠনির্মিত। একজনের কনে-পুতুলের সাথে অন্য একজন খেলার সাথির বর-পুতুলের বিয়ে দেওয়া! এ সবই ছিল ঐতিহ্যের পরম্পরা।
একটু বড় হয়ে লুকোচুরি, গোল্লাছুট, এক্কা-দোক্কা, কিং স্কিপিং (রশি লাফানি)। ছেলেরা একটু বড় হয়েই ডাংগুলি, মারবেল খেলা, হাডুডু কিংবা মধ্যবিত্ত/উচ্চমধ্যবিত্তদের পরিবারে অভ্যন্তরীণ খেলা হিসেবে ক্যারম, লুডো (সাপ কিংবা কোট), ব্যাগাডুলি বা দাবা খেলা চলত। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রচলিত আধুনিক খেলা, যেমন লং জাম্প, হাই জাম্প (উচ্চ লম্ফ), পোল ভল্ট (বাঁশ দিয়ে উচ্চ লম্ফ), জেভলিন ছোড়া, গোলক নিক্ষেপ ছাড়াও বস্তা দৌড়, বিস্কুট খাওয়ার দৌড়, সুই-সুতা ভরা, চামচের ওপর কাগজি লেবু রেখে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দ্রুত হাঁটার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছিল মজার খেলা।
তা ছাড়া গ্রামের অবারিত মাঠে ও প্রান্তরে ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা ছিল সত্যিকার অর্থে দর্শনীয়। এ কারণে অনেকেই নানা আকার ও আকৃতির সুদৃশ্য ঘুড়ি কিনে আনত গ্রাম্য মেলা ও আড়ং থেকে। তারপর লাটাইয়ের সুতায় মাজন দেওয়ার পালা। অনেকে আবার সুতায় কাচের গুঁড়া লাগাত আঠা দিয়ে, যাতে অন্যের ঘুড়িকে সহজেই কাটা যায়! কিন্তু গ্রামীণ ঘুড়ি ওড়ানো খেলা ও প্রতিযোগিতা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে এখন বলতে গেলে ভাটি অঞ্চলে হয়ে গেছে প্রায় অদৃশ্য! এর মুখ্য কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে বায়ুপ্রবাহের ঘাটতি, যা মূলত মৌসুমি জলবায়ুর তীব্রতা ও কার্যকারিতা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট।
গ্রামীণ খেলাধুলার অধিকাংশই আজকাল লুপ্ত কিংবা কিংবা বিলুপ্তির পথে। হাডুডুর পরিবর্তে আমাদের জাতীয় খেলা এখন কাবাড়ি। কিন্তু আমার শৈশব ও কৈশোর বয়সে আমি কোনো দিন দেখিনি কাবাডি খেলতে গ্রামে!
গ্রামেগঞ্জে এখন ক্রিকেট খেলাই তুঙ্গে অবস্থান করছে। খেলার সরঞ্জাম থাক বা না থাক, কিছুই যায় আসে না। এক টুকরো লম্বা তক্তার একদিকে কিছুটা সরু করে হাতলের মতো বানিয়ে ক্রিকেট ব্যাট আর একটি টেনিস বল জোগাড় করেই ক্রিকেট খেলার মহড়া চলতে থাকে!
একসময় ফুটবল খেলা জনপ্রিয় থাকলেও ক্রমশ এটি লোকপ্রিয়তা হারাচ্ছে। গ্রামের ছেলেদের ফুটবল কেনার মতো সামর্থ্য না থাকায় অনেকে বাতাবি লেবু গাছ থেকে চুরি করে বাতাবি লেবু পেড়ে ফুটবল হিসেবে খেলত। মাঝেমধ্যে আশপাশের গ্রামের ফুটবল দলের সাথে মোকাবিলাও অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু আজ ফুটবল কেনার মতো সক্ষমতা গ্রামীণ যুবসমাজের বর্তমান।
সেই মাঠও বর্তমান, যা তঝলু’র মাঠ নামে পরিচিত ছিল। তবে এখন এ মাঠে আর কেউই ফুটবল খেলে না! আশপাশের গৃহস্থ বাড়ির গরু-বাছুরগুলোকে মুক্ত অবস্থায়, আবার কখনো-বা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘাস কিংবা শুকনো খড় খেতে দেয়!
ডিজিটাল বিশ্বে এখন প্রায় সর্বত্রই এর আসর দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও এখন স্মার্টফোন, আইফোন ব্যবহার করে। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে সারা বিশ্ব প্রত্যেকের মুঠোবদ্ধ। প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ায় ব্যাপক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শিশুরাও যেন মায়ের পেটে থাকতেই মোবাইল ফোনের আইকনগুলো টেপাটেপি করে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে! এ অবস্থায় গ্রামীণ ঐতিহ্য, পরম্পরা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে ও বা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে শুধু ইতিহাস হয়ে রইবে, তা একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই বলে দেবে! (সমাপ্ত)
